রবীন্দ্রনাথ ও কল্পবিজ্ঞান
লেখক: অমিতাভ রক্ষিত
শিল্পী: টিম কল্পবিশ্ব
রবীন্দ্রনাথ কবি, রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক। তিনি একাধারে গল্পকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, অঙ্কনশিল্পী, পরিবেশ বান্ধব, পল্লী সংস্কারক, এবং সর্বোপরি বিশ্বমানবতার একনিষ্ঠ পূজারীও! নিঃসন্দেহে, গত একশো বছর বা তারও বেশি সময় নিয়ে, অগণনীও সহস্র প্রবন্ধে, রচনায় ও আলোচনায়, বহু দেশি ও বিদেশি গবেষক মিলে, তাঁর প্রতিভার গভীর থেকে গভীরতর বিশ্লেষণ করে এসেছেন। তাঁদের সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গি, মেধা ও পরিশ্রমের কারণেই, আজ আমরা রবীন্দ্রনাথের রচনা শুধুমাত্র ‘ভালো লাগার’ থেকেও বেশি মাত্রায় উপভোগ করতে শিখেছি। সে কারণে তাঁদের সকলের কাছে আমরা ঋণী। অথচ তা সত্ত্বেও, আজ রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের ১৬০ বছর পরেও, তাঁর লেখার অন্তর্নিহিত দূরদৃষ্টি, দর্শন ও মানবিকতার পরিমাপ এখনও আমাদের বিস্মিত করে।
তবে একটা প্রশ্ন— তাঁর সর্বজনবিদিত বহুমুখী প্রতিভার বিস্তৃতি যে কত ব্যাপক, সে সম্বন্ধে শেষ কথা কি ইতিমধ্যেই বলা হয়ে গিয়েছে? তাঁর মূল্যায়ন কি একেবারেই পরিপূর্ণ? নাকি তাঁর মানসে এখনও আরও কিছু সম্পদ বাকি আছে যা এতদিনেও কেউ আলোকিত করবার সুযোগ পাননি? এই সমস্ত বিষয় নিয়েই আমাদের অনুসন্ধান। তবে পরিসরের স্বল্পতার কথা চিন্তা করে, আমাদের আলোচনা, আপাতত রবীন্দ্রনাথের রচনায় কল্পবিজ্ঞানের সম্ভাব্য ছায়া নিয়েই সীমাবদ্ধ থাকবে।
আলোচনায় অগ্রসর হবার আগে, রবীন্দ্রনাথের ‘বিশ্বপরিচয়’ গ্রন্থটির উৎসর্গ বাণীতে, শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর উদ্দেশে তাঁর নিজেরই লেখা কথাকে সামান্য পরিবর্তিত করে, তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের প্রতিবেদন শুরু করছি:
“শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বকবি শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজনেষু, এই বইখানি প্রবন্ধটি তোমার নামের সঙ্গে যুক্ত করছি। বলা বাহুল্য এর মধ্যে এমন কোন বিজ্ঞান সম্পদ নেই যা বিনা সংকোচে তোমার হাতে দেবার যোগ্য। তা ছাড়া, অনধিকার প্রবেশে ভুলের আশঙ্কা করে লজ্জা বোধ করছি, হয়তো তোমার সম্মান রক্ষা করাই হল না। কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ সামনে রেখে সাধ্যমতো নিড়ানি চালিয়েছি। কিছু ওপড়ানো হল। যাই হোক আমার দুঃসাহসের দৃষ্টান্তে যদি কোনও মনীষী, যিনি একাধারে সাহিত্যরসিক ও বিজ্ঞানী, এই অত্যাবশ্যক কর্তব্যকর্মে নামেন তা হলে আমার এই চেষ্টা চরিতার্থ হবে [১]”।
রবীন্দ্রনাথ যে একজন অত্যন্ত বিজ্ঞান মনোভাবী ব্যক্তি ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ কোনও অবকাশ নেই। তাঁর নিজের জীবনব্যাপী রচনায়, শিক্ষার ভিত্তিতে, দর্শনে, ইচ্ছায়, আচরণে, আলোচনায়, এবং সহস্রাধিক গবেষক ও সাহিত্যপ্রেমীদের বিশ্লেষণে, এই বিজ্ঞান মনস্কতার যথার্থতা বারংবারই প্রমাণিত হয়েছে। এখানে তাঁর বিশাল রচনাসম্ভার থেকে উদ্ধৃত করে, সামান্য কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে এই প্রসঙ্গটি সমাপ্ত করা হবে।
‘বিশ্বপরিচয়’ বইটির উৎসর্গ বাণীতেই, রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন:
“…বালককাল থেকে বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না। আমার বয়স বোধকরি তখন নয়-দশ বছর, মাঝে মাঝে রবিবারে হঠাৎ আসতেন সীতানাথ দত্ত [ঘোষ] মহাশয়। আজ জানি তাঁর পুঁজি বেশী ছিল না, কিন্তু বিজ্ঞানের অতিসাধারণ দুই-একটি তত্ত্ব যখন দৃষ্টান্ত দিতেন আমার মন বিস্ফারিত হয়ে যেত…”
“…আমি বিজ্ঞানের সাধক নই সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু বালককাল থেকে বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না। … [পিতৃদেব] আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেওয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে ক’রে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি। স্বাদ পেয়েছিলুম বলেই লিখেছিলুম, জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে”
এই উদ্ধৃতিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের যে “প্রথম ধারাবাহিক রচনা”-র কথা উল্লেখ করেছেন, তা হল একটি প্রবন্ধ: “গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি” [২] । এই সময়ে তাঁর বয়স ছিল ১২ বছর। লেখাটিতে কিছু বালকসুলভ সরলতা থাকলেও, বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় আকর্ষণের পরিচয়, তখন থেকেই দেখতে পাওয়া যায়:
“কোনও মেঘ-বিনির্মুক্ত তারকাসমুজ্জ্বলা রজনীতে গৃহের বাহির হইয়া গগনমণ্ডলের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মনে কতকগুলি চিন্তার উদয় হইবেই হইবে। যে-সকল অগণ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডল দ্বারা নভস্তল বিভূষিত হইয়া রহিয়াছে, তাহারা কি শূন্য না আমাদের ন্যায় জ্ঞান-ধর্ম-প্রেম-বিশিষ্ট উন্নত জীবদ্বারা পূর্ণ? …”
“…তবে যদি আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে জানিতে পারি যে আমাদের এই পৃথিবীর ন্যায় প্রত্যেক গ্রহই, নিয়মিত-কাল-মধ্যে সূর্যের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে—পৃথিবীর ন্যায় আলোক, উত্তাপ, বায়ু এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী দ্বারা সুসম্পন্ন—একই নিয়মে তথায় আলোক-অন্ধকারের পর্যায় উপস্থিত হইতেছে—ঋতুর পরিবর্তন হইতেছে—শীতোত্তাপের বিভিন্নতা হইতেছে—জলভূমির সুচারু বিভাগ সম্পাদিত হইতেছে—তখন কি ওই-সকল গ্রহগণ সর্বপ্রকারে আমাদেরই মতো জীবপুঞ্জের যে আবাসভূমি এ বিষয়ে আর সংশয় হইতে পারে?”
এরপরে, ১৭ বছর বয়সে তিনি আবার একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রবন্ধ লেখেন: “সামুদ্রিক জীব” [৩] । এই রচনাটিতে তিনি সহজ সরল সামুদ্রিক জীবেদের দৈহিক গঠনের উল্লেখ করেছেন। ‘সরল উদ্ভিদ শৈবাল’-এর সঙ্গে ‘সরল প্রাণীর’ পার্থক্য দেখাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন:
“কোন খানে উদ্ভিদ শ্রেণী শেষ হইল ও জীব-শ্রেণী আরম্ভ হইল, তাহা ঠিক নিরূপণ করা অতিশয় কঠিন।”
এরপরেও তিনি বিজ্ঞান সম্পর্কিত এরকম আরও বেশ কিছু প্রবন্ধ লেখেন, কিন্তু সেগুলোর সামগ্রিক উল্লেখ এখানে বাহুল্য। শুধু এইটুকু মনে রাখলেই হবে যে এই অল্পবয়সেও, কবির বিজ্ঞান ভাবনা শুধু প্রবন্ধর মধ্যেই সীমিত ছিল না। ১৮৮৫ সালে, তাঁর ২৫ বছর বয়সে, তিনি একটি ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করলেন: “কী গাব আমি, কী শুনাব, আজি আনন্দধামে” [৪] –
“…তব নাম লয়ে চন্দ্র তারা অসীম শূন্যে ধাইছে
রবি হতে গ্রহে ঝরিছে প্রেম, গ্রহ হতে গ্রহে ছাইছে
তব নাম লয়ে চন্দ্র তারা অসীম শূন্যে ধাইছে
রবি হতে গ্রহে ঝরিছে প্রেম, গ্রহ হতে গ্রহে ছাইছে”
এখানে বিজ্ঞান আর তাঁর প্রকৃতিগত দর্শনের মধ্যে, দৃশ্যতই মেলবন্ধন ঘটেছে। আর এই মেলবন্ধন তিনি সারা জীবনই মান্য করে গিয়েছেন। বিজ্ঞানশিক্ষা ছিল তাঁর অন্তরের অদম্য আকাঙ্ক্ষা। এই সূত্রে, ১৮৯৩ সালে তিনি লিখেছেন [৫] –
“বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা জিজ্ঞাসা বৃত্তির উদ্রেক, পরীক্ষণশক্তির সূক্ষ্মতা এবং চিন্তনক্রিয়ার যাথাতথ্য জন্মে এবং সেই সঙ্গে সর্বপ্রকার ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ও অন্ধ সংস্কার সূর্যোদয়ে কুয়াশার মত দেখিতে দেখিতে দূর হইয়া যায়”
১৯০১ সালে প্রকাশিত তাঁর একটি রচনায় দেখি [৬] –
“যে-নিয়ম আমাদের ধূলিকণার মধ্যে, অনন্ত আকাশ ও অনন্ত কালের সর্বত্রই সেই একই নিয়ম প্রসারিত…যখন জানিতাম যে যে, ইন্দ্র আমাদিগকে বৃষ্টি দিতেছেন, মরুৎ আমাদিগকে বায়ু জোগাইতেছেন, অগ্নি আমাদিগকে দীপ্তি দান করিতেছেন, তখন সেই জ্ঞানের মধ্যে আমাদের একটা আন্তরিক তৃপ্তি ছিল; এখন জানি, রৌদ্রবৃষ্টিবায়ুর মধ্যে ইচ্ছা-অনিচ্ছা নাই, তাহারা যোগ্য-অযোগ্য, প্রিয়-অপ্রিয় বিচার না করিয়া নির্বিকারে যথানিয়মে কাজ করে…”
এ তো গেল শুধুমাত্র তাঁর জীবনের প্রথম পর্যায়ের বিজ্ঞানচর্চার কথা। বিজ্ঞান যে সারাজীবন তাঁর শিক্ষা ও ভাবনার অপরিহার্য অঙ্গ ছিল, তা বোঝা যায় ১৯৩৭ সালে, পরিণত বয়সে এসে শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে। লাইনটির ইংরাজি অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত ইংরেজ রবীন্দ্র-গবেষক, শ্রী উইলিয়াম র্যাডিচি, তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধের মধ্যে [৭] –
“I read scientific books more than books of literature. If this enthusiasm finds expression in my writing, the pleasure of it will not be lost on you”
‘বিশ্বপরিচয়’ প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের এই সময়কালেরই লেখা। এখানে তিনি বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর বিভিন্ন চিন্তা ও ধারণার কথা বলেছেন [৮]। লেখাটির সূচি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ‘পরমাণুলোক’, ‘নক্ষত্রলোক’, ‘সৌরজগৎ’, ‘গ্রহলোক’, ও ‘ভূলোক’ – ইত্যাদি সমস্ত বিষয়কেই, তিনি খুব সহজ বাংলায় বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছেন এই প্রবন্ধে।
তিনি নিজে যদিও কবি, তবু হয়তো জীবনব্যাপী বিজ্ঞানচর্চার অভ্যাসের জন্যই, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজস্ব দার্শনিক শিল্পী-দৃষ্টি দিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের “সত্য” অনুসন্ধান করবার সঙ্গে সঙ্গে, বিভিন্ন সমকালীন বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমন্বয় সবসময়ই খুব সফলভাবে করে যেতে পেরেছেন।
উদাহরণস্বরূপ, শ্রী অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে এই বিষয়ে তিনি লিখেছিলেন [৯] –
“বিজ্ঞান যেখানে পরমাণুর পরমতত্ত্বের সামনে আমাদের বিস্মিত মনকে দাঁড় করায়, সেখানে চরমকে দেখি – আমি সেই চরমের বন্দনা করছি”
এখানে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত এই “চরমের বন্দনা” শব্দ দুটি আরও গভীর আলোচনার দাবী রাখে। তবে সে আলোচনা পরে। এখানে শুধু লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথ যে কেবল বই পড়ে-পড়েই বিজ্ঞানের কিছু মামুলি সত্যকে আত্মস্থ করে ফেলেছিলেন, তা নয়। তাঁর বিজ্ঞান-বোধ সাধারণ মানুষের তুলনায়, এবং এমন কি অধিকাংশ সাধারণ বৈজ্ঞানিকদের তুলনাতেও, অনেক বেশি অগ্রসর ছিল। ‘বিশ্বপরিচয়’ থেকে নেওয়া আরও কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে এই কথাটা বুঝিয়ে দেওয়া যাক:
“সূর্য যেমন সৌরলোকের কেন্দ্রে থেকে টানের লাগামে ঘোরাচ্ছে পৃথিবীকে, পজিটিভ বৈদ্যুতকণা তেমনি পরমাণুর কেন্দ্রে থেকে টান দিচ্ছে নেগেটিভ বৈদ্যুত কণাগুলোকে, আর তারা সার্কাসের ঘোড়ার মতো লাগামধারী পজিটিভের চারদিকে ঘুরছে”
১৯৩৭ সালের মধ্যে মধ্যেই এইসব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বেশ ভাল ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। অতএব এখানে রবীন্দ্রনাথের কোনও স্বকীয়তা প্রমান হয়না। কিন্তু এই বিশ্বপরিচয়েরই উপসংহারে তিনি লিখেছেন:
“…বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে আপাতদৃষ্টিতে যে সকল স্থূল পদার্থ জ্যোতির্হীন, তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আকারে নিত্যই জ্যোতির ক্রিয়া চলছে। এই মহাজ্যোতিই সূক্ষ্ম আকারে প্রাণে এবং আরও সূক্ষ্মতর বিকাশ চৈতন্যে ও মনে। বিশ্বসৃষ্টির আদিতে মহাজ্যোতি ছাড়া আর কিছুই যখন পাওয়া যায় না, তখন বলা যেতে পারে চৈতন্যেই তার প্রকাশ। জড় থেকে জীবে একে একে পর্দা উঠে মানুষের মধ্যে এই মহাচৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা চলেছে। চৈতন্যের এই মুক্তির অভিব্যক্তিই বোধ করি সৃষ্টির শেষ পরিণাম…”
“…অসীমের মধ্যে কোথা থেকে আরম্ভ হল। অসীমের মধ্যে একান্ত আদি ও একান্ত অন্তের অবিশ্বাস্য তর্ক চুকে যায় যদি মেনে নিই আমাদের শাস্ত্রে যা বলে, অর্থাৎ কল্পে কল্পান্তরে সৃষ্টি হচ্ছে, আর বিলীন হচ্ছে, ঘুম আর ঘুম ভাঙার মতো”
এইসব বর্ণনাগুলোকে আমাদের সমকালে আমরা চিনতে পারি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মতবাদ বলে – যার নাম দেওয়া হয়েছে ‘বিগ ব্যাং’, বা মহা বিস্ফোরণের তত্ত্ব। এই তত্ত্বটা আজ ধীরে ধীরে বেশ দৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে বৈজ্ঞানিক জগতে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ এই নিয়ে আলোচনাটা করেছেন ১৯৩৭ সালে। যদিও এই বিস্ফোরণ তত্ত্বটা ১৯৩১ সালে প্রথম উপস্থাপিত হয়, ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝির আগে সামান্য দুই-একজন প্রথম সারির বৈজ্ঞানিক ছাড়া, আর কেউই এইসব নিয়ে বেশি আলোচনা করতেন না। অর্থাৎ, তত্ত্বটা কেবল রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের ২৫ বছর পর থেকেই জনপ্রিয় হতে থাকে। তার আগে সাধারণ বৈজ্ঞানিকেরাও এই নিয়ে বেশি আলোচনা করতেন না [১০] । সাধারণ মানুষ তো এই তত্ত্বের কথা জানতে পারেন কেবল মাত্র ১৯৯০-এর দশক থেকে শুরু করে!
রবীন্দ্রনাথের পক্ষে আধুনিকতম বিজ্ঞান সম্বন্ধে এত আগে থেকে, এত বিস্তৃত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল নিঃসন্দেহে তাঁর ব্যক্তিগত মেধা ও নিয়মিত বিজ্ঞানচর্চার গুণে। কিন্তু এ ছাড়াও, তিনি ভারতবর্ষ ও সারা পৃথিবীর বহু প্রথম সারির বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অনেক আলোচনাও করতেন নিয়মিতভাবে— বিশেষ করে মধ্যজীবনের পরে যখন তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি অনেক বেড়ে যায়।
রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্রী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে বেশ কয়েকবার আলোচনায় বসেছিলেন সে কথা সর্বজনবিদিত। বিশেষ করে সেই আলোচনাগুলোর প্রতিলিপি আমেরিকার প্রথম সারির খবরের কাগজে ছাপা হবার পরে [১১] । কিন্তু আইনস্টাইন-ই একমাত্র প্রথম সারির বৈজ্ঞানিক ছিলেন না, যাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৯ সালে, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্রী ওয়ের্ণার হাইজেনবার্গ কিছুদিন রবীন্দ্রনাথের অতিথি হিসেবে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। সে সময়ে তাঁদের মধ্যে ঠিক কী সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল তার কোনও প্রতিলিপি যদিও তৈরি বা সংরক্ষণ করা হয়নি, তবু প্রখ্যাত অস্ট্রীয়-আমেরিকান পদার্থ বিজ্ঞানী, শ্রী ফ্রিজ ক্যাপরা তাঁর একটি সাম্প্রতিক বইতে, রবীন্দ্রনাথ-হাইজেনবার্গ আলোচনার কিছু তথ্য সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন স্বয়ং হাইজেনবার্গের নিজের কাছ থেকে [১২]। এই বইটির ৪০ পাতায় ক্যাপরা লিখেছেন:
“In 1929 Heisenberg spent some time in India as the guest of the celebrated Indian poet Rabindranath Tagore, with whom he had long conversations about science and Indian philosophy. This introduction to Indian thought brought Heisenberg great comfort, he told me. He began to see that the recognition of relativity, interconnectedness, and impermanence as fundamental aspects of physical reality, which had been so difficult for himself and his fellow physicists, was the very basis of the Indian spiritual traditions. ‘After these conversations with Tagore,’ he said, ‘some of the ideas that had seemed so crazy suddenly made much more sense. That was a great help for me.”
ক্যাপরা, হাইজেনবার্গের সঙ্গে সরাসরি তাঁর নিজের কথোপকথন ছাড়াও, জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী এবং হাইজেনবার্গের প্রিয় ছাত্র, শ্রী হেলমাট রেচেনবার্গ-এর [১৩] এবং শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত ও অ্যানড্রু রবিনসন-এর [১৪] রচনাতেও, রবীন্দ্রনাথ-হাইজেনবার্গের কথোপকথন সম্বন্ধে প্রায় একই রকম চিত্র পেয়েছেন। ক্যাপরা আরও জানাচ্ছেন যে হিন্দু দর্শন ও আধুনিক কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর তত্ত্বের সাদৃশ্য নিয়ে তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ, “Dance of Shiva” পড়ে, হাইজেনবার্গ ১৯৭১ সালের ৯ জুলাইতে লেখা একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে তাঁকে জানিয়েছেন:
“The kinship between the ancient Eastern teachings and the philosophical consequences of the modern quantum theory have fascinated me again and again…”
এই সূত্রে এ-পর্যন্ত যে কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে একমাত্র রেচেনবার্গ ছাড়া আর বাকি সকলেই ছিলেন (আছেন) কোনও না কোনও বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারজয়ী। আরও একজন সাম্প্রতিক নোবেল পুরস্কারজয়ী বৈজ্ঞানিক, শ্রী ইলিয়া প্রাইগোজিন-ও, আধুনিক কোয়ান্টাম মেকানিক্স আর রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা করা ভারতীয় দর্শনের একাত্মতা দেখে একই রকম অভিমত পোষণ করেছেন [১৫] । তাঁর প্রবন্ধে প্রাইগোজিন বলেছেন [১৬] এইভাবে:
“Curiously enough, the present evolution of science is running in the direction stated by the great Indian poet.”
এখানে একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন উঠতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ কি তাহলে কেবল উপনিষদই ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন সারা জীবন? তাঁর লেখাগুলো কি তাঁর নিজস্ব অনুভূতির প্রকাশ নয়? এই বিষয় নিয়ে সামান্য একটু আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়। প্রথমত, বলা যেতে পারে যে এই প্রশ্ন এর আগে বহুবারই উঠেছে – তাঁর নোবেল পুরস্কার অর্জন করবার আগেও উঠেছে এবং পরেও উঠেছে। প্রখ্যাত জার্মান পণ্ডিত শ্রী ম্যাক্স মিউলার প্রমুখ শিক্ষাবিদদের অনুবাদের মাধ্যমে প্রগতিশীল ইউরোপ, উপনিষদ ও অন্যান্য প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে মধ্যেই বেশ পরিচিত হয়ে গিয়েছিল। তাই বিংশ শতাব্দী প্রথমদিকে (১৯১৩) যখন রবীন্দ্রনাথকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হবে কি না হবে বিবেচনা করে হচ্ছিল, তখন কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিলেন যে আমরা কি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় উপনিষদই দেখছি, নাকি এই কথাগুলোয় কবির কোনও মৌলিক অনুভূতি আছে? এমনও কথা উঠেছে যে আমরা কি এই নতুন কবির লেখা পড়ছি, নাকি তার মধ্যে তাঁর সহায়ক শ্রী W. B. Yeats-এর ভাবনারই প্রতিফলন দেখছি? এই সমস্ত বিষয় নিয়ে নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক, শ্রী অমর্ত্য সেন সম্প্রতি তাঁর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন [১৭] । এছাড়া, রবীন্দ্রনাথ সুফি মতবাদের প্রতিফলন করে গেছেন কিনা, সে নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই আলোচনা করা হয়েছে [১৮] ।
অমর্ত্য সেন বলেছেন:
“Even Anna Akhmatova, …. (Who translated his poems into Russian in the mid-1960s), talks of “that mighty flow of poetry which takes its strength from Hinduism as from the Ganges, and is called Rabindranath Tagore.”
এই প্রবন্ধে তিনি অন্যত্র বলেছেন:
“Tagore was sensitive to criticism, and was hurt by even the most far-fetched accusations, such as the charge that he was getting credit for the work of Yeats, who had “rewritten” Gitanjali. (This charge was made by a correspondent for The Times, Sir Valentine Chirol, whom E.M. Forster once described as “an old Anglo-Indian reactionary hack.”)
“From India’s diverse religious traditions, he [Tagore] drew many ideas, both from ancient texts and from popular poetry. But “the bright pebbly eyes of the Theosophists” do not stare out of his verses.”
রবীন্দ্রনাথ যে উপনিষদ ও সুফিবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা তো নিঃসন্দেহে সত্যি। তিনি পাশ্চাত্য চিন্তাধারা এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা দিয়েও যথেষ্ট প্রভাবিত। তিনি ভারত ভূখণ্ডের, মৃত্তিকার সন্তান। অতএব বহু সহস্র বছর ধরে ভারতীয় ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে যতরকম সাংস্কৃতিক, দার্শনিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও অন্যান্য চিন্তা-ভাবনার স্রোত বয়ে গিয়েছে, তার একটা সম্মিলিত প্রভাব যে তাঁর ওপরে পড়বেই তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তাতে করে তাঁর ভাবনার মৌলিকত্বের খর্ব হয় না। বাঘের গায়ের চিত্তাকর্ষক ডোরা কাটা দেখে কি বলা যায়, যে ‘এটা তার নিজস্ব সৌন্দর্য নয়, এটা সে সুন্দরবনের ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে বলেই তার পরিবেশ থেকে আপনা আপনি পেয়েছে?’ অতএব রবীন্দ্রনাথের মতবাদ যে কেবল ঔপনিষদীয় ভাবনাই, এমন কথা মনে করবার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ নেই।
এই প্রসঙ্গে ওপরে উল্লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য নিয়ে আরও একটু আলোচনা করা যাক। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন [৯] –
“বিজ্ঞান যেখানে পরমাণুর পরমতত্ত্বের সামনে আমাদের বিস্মিত মনকে দাঁড় করায়, সেখানে চরমকে দেখি – আমি সেই চরমের বন্দনা করছি”
রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনেরই চরমের বন্দনা করে গিয়েছেন। তাঁর ‘মানুষের ধর্ম’ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন:
“…সীমার মধ্যে মানুষের জিজ্ঞাসা অসমাপ্ত থেকে যায়। কোনো সীমাকেই মানুষ চরম বলে যদি মানত তা হলে তা হলে মানুষের ভৌতিক বিজ্ঞানও বহুকাল পূর্বেই ঘাটে নোঙর ফেলে যাত্রা বন্ধ করত। একদিন পণ্ডিতেরা বলেছিলেন, ভৌতিক বিশ্বের মূল উপাদানস্বরূপ আদিভূতগুলিকে তাঁরা একেবারে কোণঠাসা করে ধরেছেন, একটার পর একটা আবরণ খুলে এমন কিছুতে ঠেকেছেন যাকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না। বললে কী হবে। অন্তরে আছেন প্রবহণ রাজা, তিনি বহন করে নিয়ে চলেছেন মানুষের সব প্রশ্নকে সীমা থেকে দূরতর ক্ষেত্রে। তিনি বললেন,
অপ্রতিষ্ঠিতং বৈ কিল তে সাম, অন্তবদ্ বৈ কিল তে সাম।
আদিভূতের যে বস্তুসীমায় প্রশ্ন এসে থেমেছিল সে সীমাও পেরোল। …. একদিন আলোকের তত্ত্বকে মানুষ বোধগম্যতার পরপারেই স্থাপন করেছিল। অদ্ভুত কথা বলেছিল, ‘ঈথারের ঢেউ’ -জিনিসকেই আলোকরূপে অনুভব করি। অথচ ঈথার যে কী আমাদের বোধের ভাষায় তার কোনও কিনারা পাওয়া যায় না…”
রবীন্দ্রনাথ এই সীমার অপর পারের প্রশ্নগুলোর উত্তরের সন্ধানই সারাজীবন ধরে করে গিয়েছেন। করেছেন তাঁর বোধ দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে। তাঁর ঔপনিষদিক ভাবনায়, সেইখানেই অবস্থান করে এই চরম, বা “সত্য”। একদিক থেকে চিন্তা করলে কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত বিজ্ঞানীদের সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরা এবং রবীন্দ্রনাথ, সকলেই এই একই “সত্য”-কে খুঁজে বেড়িয়েছেন। বিজ্ঞানীরা চেনা পরিধির বাইরের সত্যটাকে সন্ধান করেছেন তাঁদের বিজ্ঞান দিয়ে, গণিত দিয়ে – সীমার সীমানাকে ক্রমাগতই পেছন দিকে ঠেলতে ঠেলতে। রবীন্দ্রনাথ সত্যকে উন্মোচন করবার চেষ্টা করেছেন সীমানার অপর পারের পরিপ্রেক্ষিত থেকে – তাঁর দর্শন দিয়ে, তাঁর কবিত্ব দিয়ে। তাই দুপক্ষের যখনই মিল হয়েছে, তখনই বোঝা গিয়েছে যে তাঁদের প্রচেষ্টাগুলো পরিপূরক। হাইজেনবার্গ যদিও উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর অনিশ্চয়তার সূত্রটা ‘সত্য’, কিন্তু তা তখনও তৎকালীন “সীমা”-র বাইরে অবস্থিত বলে, তাতে তিনি নিজে কোনও সন্তুষ্টি অনুভব করতে পারেননি। কিন্তু যখন রবীন্দ্রনাথ সীমানার ওপারের দৃষ্টি নিয়ে এসে বলতে পারলেন: “‘চরম’ তো কখনও দৃশ্য, কখনও বা অদৃশ্য; এতে আর অবাক হবার কী আছে”, তখনই সেই সূত্রটা কেন যে ‘সত্য’ তা আরও ভাল করে বুঝতে পেরে, হাইজেনবার্গের মনে শান্তি ফিরে এসেছিল।
কিন্তু ‘সত্য’ অনুভব করা বা না করার ওপরে কি কল্পবিজ্ঞান রচনা নির্ভরশীল? এর সোজামাটা উত্তর তো নিঃসন্দেহে, ‘না’। কিন্তু তাহলে এবারে বিবেচনা করে দেখা যাক কল্পবিজ্ঞানের সংজ্ঞা কী। শ্রী রামকৃষ্ণদেব-এর একটি সুপরিচিত কথা এখানে খুবই যথাযথ মনে হয়। ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি বলে গেছেন – ‘যত মত তত পথ’! কল্পবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও মনে হয় কথাটা একইভাবে খাটে। শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রী জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের বিবেচনায়, ‘বিজ্ঞান তো সম্পূর্ণ তথ্যনির্ভর। তার ওপরে কি কল্পনার রঙ চড়ানো যায়?’ [২০] । এই কথাটা যেমন সত্য, তেমনি গভীরও। বিজ্ঞানকে বিকৃত করে কখনও কল্পবিজ্ঞান সৃষ্টি করা যায় না। ‘নিউটনের মাথার ওপর থেকে আপেলটা আপনা আপনি গাছের ওপরে উঠে এল’ – এই বলে একটা গল্প শুরু করলে সেটা ‘ফ্যান্টাসি’ বা কল্পনাই শুধু হবে, কল্পবিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হবে না। বাংলা ভাষার একটি আধুনিক অন্তর্জালভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা, ‘কল্পবিশ্ব’ -র সম্পাদকমণ্ডলীর মতে [২১], শ্রী কিম স্ট্যানলি রবিনসনের দেওয়া সংজ্ঞাটা অনুধাবনযোগ্য:
“[SF is] an historical literature… in every sf narrative, there is an explicit or implicit fictional history that connects the period depicted to our present moment, or to some moment in our past”
এছাড়া, টেক্সাস স্টেট ইউনিভার্সিটি-র ইংরিজী সাহিত্যের অধ্যাপক, শ্রী সুপর্ণ ব্যানার্জী, এর অন্য একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন [২৩] –
“কল্পবিজ্ঞান এমন এক সাহিত্য শৈলি যা লেখকের প্রতীতি আর বিচ্ছিন্নতা বোধ, এই দুইয়ের অসঙ্গতিকে আশ্রয় করে গড়ে তোলে এক অনন্য জগৎ”
বিশ্বের ইতিহাসের কিছু কিছু প্রখ্যাত কল্পবিশ্ব সাহিত্যিক কাছ থেকে আরও কিছু ভিন্ন সংজ্ঞা পাওয়া যায়:
আইজ্যাক অ্যাসিমভ [২৪] – “Science fiction can be defined as that branch of literature which deals with the reaction of human beings to changes in science and technology”
মার্টিন গ্রিনবার্গ ও আইজ্যাক অ্যাসিমভ [২৫] – “‘[H]ard science fiction’ [is] stories that feature authentic scientific knowledge and depend upon it for plot development and plot resolution.”
হিউগো গার্ণসব্যাক [২৬] “…a charming romance intermingled with scientific fact and prophetic vision… Not only do these amazing tales make tremendously interesting reading—they are always instructive. They supply knowledge… in a very palatable form… New adventures pictured for us in the scientifiction of today are not at all impossible of realization tomorrow… Many great science stories destined to be of historical interest are still to be written… Posterity will point to them as having blazed a new trail, not only in literature and fiction, but progress as well.”
রে ব্র্যাডবেরী [২৭] “Science fiction is the one field that reached out and embraced every sector of the human imagination, every endeavor, every idea, every technological development, and every dream…. I called us a nation of Ardent Blasphemers. We ran about measuring not only how things were but how they ought to be.
তাহলে সব মিলিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখলে বলা যেতে পারে, যে কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যের এমনই একটি শাখা, যার মাধ্যমে বর্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ওপরে ভিত্তি করে কল্পিত ভবিষ্যৎ অথবা কল্পিত অতীতের চিত্র তৈরি করা যায়। সে চিত্র যেমনই হোক, ধ্বংসেরই হোক বা প্রগতির হোক, শিক্ষামূলক হোক বা নিছক বিনোদনপূর্ণ হোক, ব্যঙ্গাত্মক হোক বা স্তুতিময় হোক, ঐকতা বা বিচ্ছিন্নতাপূর্ণ, সুন্দর বা অসুন্দর – যতক্ষণ পর্যন্ত তা বিজ্ঞানের কোনও প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব বা নীতি লঙ্ঘন না করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কল্পবিজ্ঞানই বলা যাবে। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের ওপরে ভিত্তি করে যদি একটি ভবিষ্যৎ কল্পনা করা হয়, এবং তার কিছুদিন পরে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে সেই ভিত্তিটাই যদি ভুল বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে কী সেই আগের ভিত্তিতে সৃষ্ট ভবিষ্যতটা আর কল্পবিজ্ঞান বলে গণ্য হবে না? ভবিষ্যৎ ভুল বা ঠিক হওয়াটাই কি কল্পবিশ্বের মাপকাঠি? নাকি প্রতিষ্ঠিত ভিত্তিকে বিশ্বস্তভাবে মেনে চলা? তা ছাড়া, এই অনাগত ভবিষ্যতের চিত্র যদি আমরা পাই কোনও ক্যানভাসের ওপরে শিল্পীর তুলির আলেপ থেকে, অথবা ধ্যানমগ্ন কোনও দার্শনিকের সাধনার দৃষ্টির স্বচ্ছতা দিয়ে, তাহলে কি কিছু যায় আসে? কল্পনার পদ্ধতিটা প্রথাগত না হলে কি তাকে আর কল্পবিজ্ঞানের পর্যায়ে ফেলতে পারব না? এইসব প্রশ্নের হয়তো কোনও উত্তর নেই, এবং দিতে গেলে বিচারটা হয়তো বা একটু বেশি চুলচেরা হয়ে যাবে।
কিন্তু কল্পবিজ্ঞানকে আবার অন্যভাবেও দেখা যেতে পারে। কল্পবিজ্ঞানের ভবিষ্যতকে যে সবসময় নিষ্ক্রিয়ই হতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। এই ধরনের ভবিষ্যৎ, কোনও কোনও সময়ে বর্তমানের প্রযুক্তিকে সক্রিয়ভাবে সামনের দিকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে নতুন নিশানার ইঙ্গিত দিতে দিতে। অথবা সে এমন এক ভবিষ্যতের বর্ণনা দিতে পারে, যা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হলেও, আরও কিছু অগ্রগতির পরে একদিন তা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়ে যায়।
এবারে, রবীন্দ্রনাথের কোনও রচনা কল্পবিজ্ঞান হিসেবে ধার্য হতে পারে কিনা তাই নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। আমরা আগেই দেখেছি যে রবীন্দ্রনাথের লেখা নানাভাবে বিজ্ঞান চিন্তায় সম্পৃক্ত। ১৯৩৬ সালে তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর কাব্যগ্রন্থ ‘শ্যামলী’। তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল একটি কবিতা: ‘চেতনা’। এই কবিতাটির মূল প্রতিপাদ্য হল সত্যের আপেক্ষিকতা। মানবধর্মী রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্যটা আপেক্ষিক, তার কারণ তা মানব ভিত্তিক। মানুষ না থাকলে সত্যও নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ‘সত্যের আপেক্ষিকতা’ নিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর কিছু মতবিরোধও হয়েছিল। আইনস্টাইন নিজে আপেক্ষিকতা শাস্ত্রের জনক হলেও, সত্যের ক্ষেত্রে (reality) তিনি ছিলেন নির্দিষ্টতাবাদি। কোয়ান্টাম মেকানিক্স বা আজকের মাল্টিভার্স তত্ত্ব তাঁর কাছে বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। কিন্তু সে বিষয়ে কোনও আলোচনা এই প্রবন্ধের সীমানার বাইরে। শুধু উল্লেখ করি যে ‘চেতনা’ কবিতাটির প্রতিপাদ্য ছিল যে মানুষ না থাকলে সৃষ্টির আর কোনও প্রাসঙ্গিকতা থাকে না, কারণ তখন প্রকৃতির সৌন্দর্য অনুভব করবার মতো আর কেউ বাকি থাকবে না। তাই রবীন্দ্রনাথ প্রথমে মানুষের জগতটার (পৃথিবীর) ধ্বংসের কথা কল্পনা করে নিলেন। তারপরে তিনি তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়ে চলে গেলেন। সেই ধ্বংস-কল্পনার অংশটুকু নীচে উদ্ধৃত করা হল:
“…বুড়ো চন্দ্রটা, নিষ্ঠুর চতুর হাসি তার,
মৃত্যুদূতের মতো গুঁড়ি মেরে আসছে সে
পৃথিবীর পাঁজরের কাছে।
একদিন দেবে চরম টান তার সাগরে পর্বতে;
মর্তলোকে মহাকালের নূতন খাতায়
পাতা জুড়ে নামবে একটা শূন্য,
গিলে ফেলবে দিনরাতের জমাখরচ;
মানুষের কীর্তি হারাবে অমরতার ভান,
তার ইতিহাসে লেপে দেবে
অনন্ত রাত্রির কালি।
মানুষের যাবার দিনের চোখ
বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রঙ,
মানুষের যাবার দিনের মন
ছানিয়ে নেবে রস!
শক্তির কম্পন চলবে আকাশে আকাশে,
জ্বলবে না কোথাও আলো।
বীণাহীন সভায় যন্ত্রীর আঙুল নাচবে,
বাজবে না সুর।….”
লক্ষণীয় যে এই চিত্রটি আজকের ডিস্টোপিয়ার গল্পের মতনই – ভবিষ্যতের পৃথিবী ধ্বংস হবার সজীব বর্ণনা। এখন আলোচনা করে দেখা যাক যে এই চিত্রটির কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল কিনা। আজ আমরা বুঝি যে পৃথিবীর ধ্বংসের সর্বাধিক সম্ভাবনা হবে যখন আমাদের সূর্য Supernova হয়ে যাবে। অথবা, তার আগেই যদি সৌর জগতের বাইরে থেকে ধেয়ে আসা কোনও বিশাল উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে পৃথিবীর হঠাৎ সংঘর্ষ হয়। কিন্তু চাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষ হবার কোনও সম্ভাবনা আছে বলে এখন আর মনে করা হয় না। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথ যখন এই কবিতাটা লেখেন, তখন কিন্তু আমাদের ধারণা ছিল যে চাঁদের কক্ষপথ ক্ষয়িষ্ণু হতে হতে একদিন সে পৃথিবীর এত কাছে এসে যাবে যে মাধ্যাকর্ষণের টানে সে পৃথিবীর ওপরে এসে আছড়ে পড়বে আর তাকে ধ্বংস করে দেবে। অতএব রবীন্দ্রনাথ এই ধ্বংসের কল্পনাটা পুরোপুরি তদানীন্তন বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই লিখেছিলেন। আর তাই যদি হয়, তাহলে এই কবিতাটিকে কল্পবিজ্ঞানের আখ্যান বলে অভিহিত করতে বাধা কোথায়?
পরিশেষে, একটি অতি পরিচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা আলোচনা করে আমাদের এই প্রতিবেদন শেষ করব। অল্প কিছুদিন আগে পর্যন্তও বিজ্ঞান আমাদের জানাত যে মহাবিশ্বের খুব অল্প স্থান জুড়েই অবস্থিত আছে প্রকৃতির গ্রহ নক্ষত্রগুলো। সর্বাধিক জায়গা জুড়ে আছে শুধু মহাশূন্য, আর মহাঅন্ধকার। হয়তো বা একসময়ে শুধু মহাশূন্য আর মহাঅন্ধকারই ছিল প্রকৃতিতে। শেষে একসময়, পদার্থ সৃষ্টি হবার পরে কোনও একসময়ে, ‘Big Bang’ বা মহাবিস্ফোরণের ফলে পদার্থপিণ্ডটা নানা অংশে বিক্ষিপ্ত হয়ে, উৎপত্তি করে যত গ্রহ-নক্ষত্রের। তারপরে, বিস্ফোরণের সেই প্রবল ধাক্কায়, নক্ষত্রগুলো তাদের নিজের নিজের গ্রহমণ্ডলীগুলোকে সঙ্গে নিয়ে, কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে এসে, একে অপরের থেকে ক্রমাগতই দূরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সময়ে, বিস্ফোরণের ধাক্কার তেজটা কমতে কমতে, তাদের মধ্যে দূরত্ব বাড়বার গতিটাও কমে আসবে ক্রমেই। শেষে সেই ধাক্কা কমতে কমতে, মাধ্যাকর্ষক আকর্ষণের বলে, তারা একদিন আবার বিস্ফোরণের কেন্দ্রের দিকেই উলটো করে ফিরে আসতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত, গ্রহ-নক্ষত্রগুলো একে অপরের ঘাড়ের ওপরে গিয়ে পড়ে, জমে জমে আবার সেই আদি পদার্থপিণ্ডটায় পরিণত হবে। তারপরে সেই পুঞ্জিভূত পদার্থের ভারে, একসময় কেন্দ্রের মধ্যে আবার বিস্ফোরণ হবে এবং এই পুরো ঘটনাটার ক্রমানুসার, চক্রাকারে ঘটতে থাকবে অন্তহীনভাবে। এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে মহাশূন্যের এই মহাঅন্ধকারের মধ্যে থেকে, আপনা আপনি পদার্থের সৃষ্টি হল কীভাবে? পদার্থ না থাকলে তো আর মহাবিস্ফোরণের প্রশ্নই উঠত না।
উল্লিখিত গানটা রবীন্দ্রনাথ লেখেন ১৯১৪ সালে:
“অন্ধকারের উৎস-হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো!
সকল দ্বন্দ্ববিরোধ-মাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই তো তোমার ভালো ॥
পথের ধুলায় বক্ষ পেতে রয়েছে যেই গেহ
সেই তো তোমার গেহ।
সমরঘাতে অমর করে রুদ্রনিঠুর স্নেহ
সেই তো তোমার স্নেহ ॥
সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান
সেই তো তোমার দান।
মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি বহিছে যেই প্রাণ
সেই তো তোমার প্রাণ।
বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি”।
গানটির প্রথম দুটি ও শেষ দুটি লাইন খুবই উল্লেখযোগ্য; বিশেষ করে প্রথম দুটি লাইন। বিজ্ঞান বলে, আলো হল শক্তি, আর শক্তি থেকেই সৃষ্ট হয় পদার্থ। পদার্থের মূলে আছে অণু-পরমাণু। তাদের কেন্দ্রের মধ্যে আছে ইলেকট্রন আর প্রোটন। প্রোটনকে কেন্দ্র করে, ঠিক সৌরমণ্ডলের গ্রহেদের মতন করেই প্রোটনকে প্রদক্ষিণ করে চলে ইলেকট্রনেরা। কিন্তু আধুনিক কোয়ান্টাম মেকানিক্সের তত্ত্ব এখন বলে, যে ইলেকট্রনেরা সবসময় একটা নির্দিষ্ট কক্ষে স্থিতিশীল হয়ে থাকতে পারে না; তারা প্রায়শই কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে পরিব্রাজন করে বেড়ায়। একটি কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে যেতে কিন্তু হয় গেলে প্রয়োজন লাগে শক্তির উৎক্ষেপের, নয়তো বিকাশ হয় তার নিক্ষেপের। এই নিক্ষিপ্ত শক্তিই দৃশ্য হয়ে যায় আলোর কণা, বা ফোটন হিসেবে। এইভাবে চিন্তা করলে, ‘অন্ধকারের উৎস-হতে উৎসারিত আলো, সেই তো তোমার আলো’ লাইনদুটির মধ্যে যে একটা গভীর অনুভূতি অন্তর্নিহিত আছে তা স্পষ্ট হয় বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ এখানে ‘শক্তি’-কেই বর্ণনা করছিলেন। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে আলো? আলোর উপস্থিতি থাকলে তো আর সেখানে অন্ধকার থাকতেই পারে না, তাহলে? লাইনগুলো কি তবে ছিল শুধুই কাব্যিক বর্ণনা?
অতি সাম্প্রতিক কালে কিন্তু কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে, এই বর্ণনাটাকে এখন আবার ভেবে দেখবার সময় হয়েছে। গবেষণাটিতে প্রমাণিত হয়েছে যে আসলে অন্ধকার বা ‘শূন্য’-ই হল আলোর উৎস। অর্থাৎ ফোটন কণার জন্ম হয় (বা হতে পারে) অন্ধকারে। যদি একটি আয়নাকে, শূন্যস্থানে নিয়ে গিয়ে আলোর গতিতে ঘোরানো যায়, তাহলে সেখানে দেখা যাবে ফোটন কণা [২৮], [২৯]।
তাহলে রবীন্দ্রনাথের লাইন দুটো এবারে আবার পরীক্ষা করে দেখা যাক! ‘অন্ধকারের উৎস-হতে উৎসারিত আলো, সেই তো তোমার আলো!’ এই তো শক্তি, এই তো সেই সত্য, যার আরাধনা রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরে করে গিয়েছেন। কিন্তু যে কবি ১৯১৪ সালে বসে, ২০১৩ সালের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে অক্ষরে অক্ষরে বর্ণনা করে দিয়ে গিয়েছেন, তাঁকে যদি আমরা একজন পুরোদস্তুর কল্পবিজ্ঞান লেখক বলে আখ্যা দিই তাহলে কি তা খুব অত্যুক্তি হবে?
পরিশেষে বলি, রবীন্দ্রনাথকে কল্পবিজ্ঞানের লেখক বলা যায় কিনা তাই নিয়ে যত বিস্তৃত আলোচনাই হোক না কেন, তিনি নিজে চিরদিনই এসবের ঊর্ধ্বে থাকবেন, যেমন তিনি জীবিতকালে ছিলেন। তাঁর চিরন্তন সন্ধান ছিল সীমার মাঝে অসীমের – ‘সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর’। সেই অসীমের সন্ধানেই তাঁর চিত্ত হয়েছিল, আজীবন ধরে বিস্ময়বোধে লীন –
“নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান।
বিস্ময়ে তাই জাগে, জাগে আমার প্রাণ..
আকাশ ভরা……”
তথ্যসূত্র:
[১] ‘বিশ্বপরিচয়’ বইয়ের উৎসর্গ বাণী, শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বসু উদ্দিষ্ট; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ২৫, বিশ্বভারতী প্রেস
[২] ‘গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি’ – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; রবীন্দ্র রচনাবলী ১৭ তম খণ্ড (বিজ্ঞান); প্রথম প্রকাশ ১২৮০ বঙ্গাব্দের (১৮৭৩) পৌষ সংখ্যা ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকায়। কবির বয়স তখন ১২ বছর।
[৩] ‘সামুদ্রিক জীব’ – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী ১৭ তম খণ্ড (পরিশিষ্ট); প্রথম প্রকাশ বৈশাখ সংখ্যা ‘ভারতী’ পত্রিকা, ১২৮৫ বঙ্গাব্দে (১৮৭৮) । কবির বয়স তখন ১৭ বছর ।
[৪] “কী গাব আমি, কী শুনাব, আজি আনন্দধামে” ব্রহ্মসঙ্গীত, গান সংখ্যা ৮৫০, রচনাকাল ১২৯২ বঙ্গাব্দ (১৮৮৫)
[৫] “প্রসঙ্গ-কথা” – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ১২, (শিক্ষা); বিশ্বভারতী প্রেস। প্রথম পঠিত হয় ১২৯৯ বঙ্গাব্দে, রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশনে (১৮৯৩)
[৬] “বৈজ্ঞানিক কৌতূহল” – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ২, (পঞ্চভূত); বিশ্বভারতী প্রেস। ১৩০৪ বঙ্গাব্দে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এর আগে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ পায় (১৯০১)
[৭] “Particles and sparks Tagore, Einstein and the poetry of science” William Radice,
India International Centre Quarterly, SUMMER/MONSOON 1998, Vol. 25, No. 2/3 (SUMMER/MONSOON 1998), pp. 131-150
[৮] “বিশ্বপরিচয়” – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ২৫, বিশ্বভারতী প্রেস। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ (১৯৩৭)
[৯] “চিঠিপত্র”, একাদশ সংখ্যা – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা।
[১০] “Big Bang: the etymology of a name” – Helge Kragh, Astronomy & Geophysics, Volume 54, Issue 2, April 2013, Pages 2.28–2.30, https://doi.org/10.1093/astrogeo/att035
[১১] “Confluences of Minds: Tagore-Einstein Colloquy”, First Indo-US Workshop on Mathematical Chemistry, January 9-13,1998. The pamphlet also contains two letters to Tagore from Einstein, Tagore’s Memories of Einstein (which introduce the conversation in the Appendix to The Religion of Man) and Einstein’s brief contribution to the Golden Book of Tagore, 1931
[১২] “Uncommon Wisdom – Conversations with Remarkable People” – Fritjof Capra; Simon & Schuster, January 1988
[১৩] “Werner Heisenberg – Die Sprache der Atome: Leben und Wirken – Eine wissenschaftliche Biographie – Die “Fröhliche Wissenschaft” (Jugend bis Nobelpreis)” – Helmut Rechenberg; Springer, 2010
[১৪] “Rabindranath Tagore: The Myriad-Minded Man” – Krishna Dutta and Andrew Robinson (St. Martin’s Press, 1995; footnote, p. 283).
[১৫] “The Mathematician and the Mystic” Andrew Robinson and Dipankar Home
https://www.resurgence.org/magazine/article3380-the-mathematician-and-the-mystic.html
Also summarized in Times Higher Education Supplement (THES) in 1995
[১৬] “Order out of Chaos: Man’s new dialogue with nature” – Ilya Prigogine and Isabelle Stengers (1984), Flamingo
[১৭] “Tagore and his India” – Amratya Sen. Nobel Prize Outreach AB 2021.
https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1913/tagore/article/
[১৮] “Rabindrantah Tagore’s Syncretistic Philosophy and the Persian Sufi Tradition” – Leonard Lewisohn. Internatioonal Journal of Persian Literature, Volume 2, 2017.
https://www.jstor.org/stable/10.5325/intejperslite.2.1.0002
[১৯] “মানুষের ধর্ম” – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ২০, বিশ্বভারতী প্রেস। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ (১৯৩৭)
[২০] জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, ব্যক্তিগত আলোচনা, আগস্ট ২০২১
[২১] কল্পবিশ্ব পত্রিকা; https://kalpabiswa.com
[২২] দীপ ঘোষ ও সুপ্রিয় দাস – Indian Science Fiction Writer’s Association -এর কাছে একটি উপস্থাপনা, আগস্ট ৩০, ২০২১
[২৩] “Other tomorrows: postcoloniality, science fiction and India” Suparno Banerjee, Doctoral Dissertation, 2010; Louisiana State University, USA
[২৪] “How Easy to See the Future!” – Isaac Asimov; Natural History, 1975
[২৫] Greenberg, Martin; Asimov Isaac, eds (1990) Writer’s Digest Books. P. 6.
[২৬] Stableford, Brian; Clute, John; Nicholls Peter (eds.) Encyclopedia od Science Fiction. London: Orbit/Little, Brown and Company, pp 311-314
[২৭] Farrell, Edmund J.; Gage, Thomas E.; Pfordesher, John; et al., eds. 1974. Science Fact/Fiction. Introduction by Ray Bradbury
[২৮] “Something from Nothing: A Vacuum Can Yield Flashes of Light” Charles Q. Choi; February 12, 2013. Scientific American. https://www.scientificamerican.com/article/something-from-nothing-vacuum-can-yield-flashes-of-light/
[২৯] “Understanding vacuum fluctuations in space” University of Regensburg. https://phys.org/news/2020-08-vacuum-fluctuations-space.html
সহায়ক রচনা, ব্লগ ও গ্রন্থাবলী:
১. “জীবনস্মৃতি” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ১৭, বিশ্বভারতী প্রেস
২. “শিক্ষার বাহন” (পরিচয়), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ১৮, বিশ্বভারতী প্রেস
৩. “প্রসঙ্গ-কথা” (শিক্ষা), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ১২, বিশ্বভারতী প্রেস
৪. “শিক্ষার হেরফের” (শিক্ষা), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, খণ্ড ১২, বিশ্বভারতী প্রেস
৭. “রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা” – সুনীলচন্দ্র সরকার, কলকাতা মৈত্রী 1964
৮. “India Perspectives”, Vol 24 No. 2/2010, Editor: Navdeep Suri http://www.meaindia.nic.in
৮. “আমার রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের আমি” – গৌতমকুমার পাল, এখন আহবকাল, ১১ বর্ষ, পাতাঃ ৭৭-৮০, ২-৩ সংখ্যা, মে-ডিসেম্বর ২০১০
৮. “রবীন্দ্রনাথের চেতনা বিজ্ঞানের আলোয়” – https://sabychak.wordpress.com/author/sabychak/
৯. “রবীন্দ্রে বিজ্ঞান” – অভিজিৎ রায়, https://blog.mukto-mona.com/2011/05/07/16129/
১০. https://www.tagoreweb.in/
১১. “বিজ্ঞানে রবীন্দ্রনাথ” – মো. ইসরাফিল আলম, https://www.jagonews24.com/literature/article/499071
১২. http://rajatdevp.blogspot.com/2017/03/1.html
১৩. https://www.facebook.com/AmaraRabindranatha/posts/256547107804278/
১৪. “Reflections and Remembrance: A Selection of Tagore’s Writings”; Translated by Amitabha Rakshit. Papyrus, Kolkata, India. 2007
Tags: অমিতাভ রক্ষিত, বিশেষ আকর্ষণ, ষষ্ঠ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা
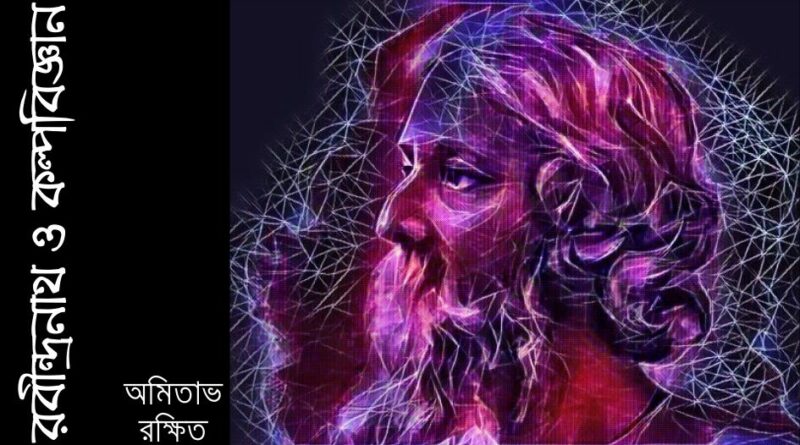

অনেক কিছু জানলাম অমিতাভদা। অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর একটি প্রবন্ধের জন্যে।
দীপ – আমি তোমার কাছে আর পুরো কল্পবিশ্ব টিমের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ – আমাকে “খেলায় নেবার জন্য”!!! তোমরা সবাই যে কত পরিশ্রম করছ এর জন্য তা আর কেউ জানুক আমি জানি – আমি যে তোমাদেরই মতন – ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়েছি সারা জীবন। তোমাদের কাছ থেকে অনেক অনুপ্রেরণা পেয়ে এত বছর পরে আবার এইসব লেখার উৎসাহ হচ্ছে। এই বছরে এখানে লেখার মান অতি উচ্চ – মনে হয় সবাই যেন তাঁদের জীবনের সবচেয়ে ভাল লেখাগুলো লিখে দিয়েছেন! চলুক এরকম!
এই লেখাটা কল্পবিশ্বের একটি মাইলস্টোন হয়ে থাকবে।
অনেক অনেক ধন্যবাদ, সুপ্রিয়, এত বড় কমপ্লিমেন্ট দেওয়ার জন্য। রবীন্দ্রনাথের কথা ভেবে কিছু লিখতে গেলেই তা আপনা থেকেই একটু অন্য রকম হয়ে যায় – এটা তাঁরই প্রসাদ!
এইবারের পূজাবার্ষিকীর অন্যতম সেরা লেখা। ঋদ্ধ হলাম
অনেক ধন্যবাদ সোহম। রবীন্দ্রনাথের কথা আলোচনা করতে গেলেই মনটা উর্দ্ধে উঠে যায়।