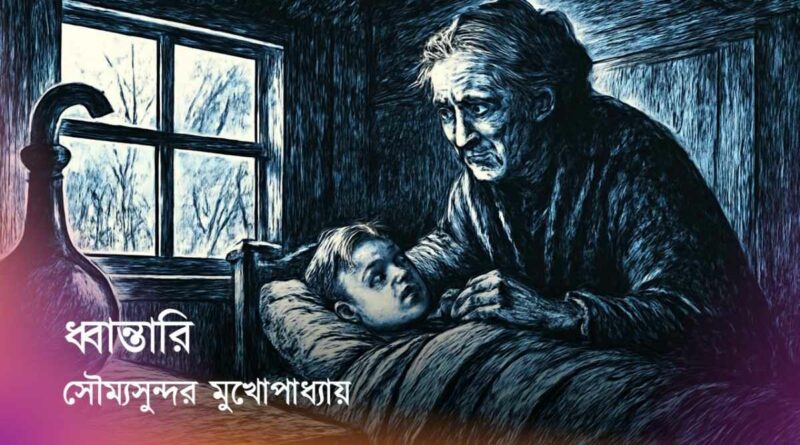ধ্বান্তারি
লেখক: সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়
শিল্পী: টিম কল্পবিশ্ব
জ্বরে বেহুঁশ ছেলের পাশে বসে তার দুর্বল শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনতে শুনতে অপেক্ষা করছি আমি। কোলের উপর রাখা আছে লম্বা গলার কাচের বোতলটা। এই বোতলটায় কুকি রাখতাম আগে, কিন্তু আজকের পর থেকে…
পাহাড়ের উপর থেকে সকালের রোদ এসে পড়ছে পুবদিকের জানালা দিয়ে, কিন্তু ঘরের তীব্র ঠান্ডা তাতে বিশেষ কমছে না। ভারী বোতলটার মসৃণ গায়ে আমার নিশ্বাস যেন জমে যাচ্ছে। ছেলের দেহটা শীতে কাঁপছে। আরেকটা কম্বল ওর গায়ে চাপিয়ে দিয়ে ওর তামাটে চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিলাম আমি; ফিশফিশ করে বললাম, “আর চিন্তা নেই, বিরজু। শেঠজি আসছে। আবার আগুন জ্বালাতে পারব আমরা। শেঠজি এলেই তুই আবার ভালো হয়ে যাবি।”
আমার কথা বিরজুর কানে গেছে বলে মনে হল না। অবশ্য গেলেও ও মোটেই বিশ্বাস করত না। এই গাঁয়ের লোক খুব ভালো করেই জানে, শেঠজি কী চিজ! মোটা টাকা আমদানির লোভ না থাকলে লোকটা কোনোদিন কারও ‘ভালো’ করতে চেয়েছে, এ অপবাদ তার অতি বড়ো শত্রুও দেবে না।
সমস্যাটা তো ওইখানেই। টাকা আমাদের কাছে একদম নেই, আর…
আর আগুনের দাম যে বড়ো বেশি! সত্যি সত্যিই অগ্নিমূল্য!
গত দু-বছর ধরে আমরা সাদা পাহাড়ের বাসিন্দারা দেখছি, আগুনের দাম কীভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। আমরা শুধুই দেখছি, কিন্তু কিচ্ছু করতে পারছি না। এখন এক বাক্সো দেশলাইয়ের দাম হয়েছে পাঁচশো টাকা! সারামাসেও আমি অত টাকা রোজগার করি না।
কিন্তু শিগগির যদি ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালাতে না পারি, বিরজু বাঁচবে না।
পুরুতঠাকুর এসেছিল গতকাল। তার কথাগুলো আমার পছন্দ হয়নি বটে, কিন্তু আমি জানি, লোকটা আপাদমস্তক সত্যি কথাই বলে গেছে।
সত্যি কথাগুলো এখন বড্ড বেশি তেতো লাগে।
পুরুতঠাকুর বলেছিল, “কতকাল আয়না দেখিসনি যমুনা? আরও কতকগুলো চুল পাহাড়চূড়ার বরফের মতো সাদা হয়ে গেছে, দেখেছিস কখনও? বয়স তো তোরও কম হল না। এই বুড়ো বয়স কি জোয়ান ছেলেকে বিদায় জানানোর উচিত সময়? ভগবান না করুন, যদি বিরজুর ভালোমন্দ কিছু একটা হয়ে যায়, তাহলে বাকি জীবনটা যে পুরো একা হয়ে যাবি তুই।”
একটা শুকনো হাসি হাসলাম আমি, “মা হয়ে ছেলেকে বিদায় দেওয়ার কি কোনো ‘উচিত সময়’ হয়, পুরুতঠাকুর?”
“না, হয় না। কিন্তু তুই অসুস্থ হয়ে পড়লে কি আর ছেলেটার কোনো উপকার হবে? আমি সূর্যদেবের কাছে প্রার্থনা করব, তিনি যেন ওকে জীবন দেন। এর মধ্যে তোকে কিন্তু যেভাবেই হোক, দেশলাই কিনতে হবে, যমুনা। ছেলেটাকে বাঁচাতে হলে এ ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালাতে হবে।”
আমি ভ্রূ কুঁচকে বললাম, “তোমার কি মনে হয়, আমার কাছে যদি পয়সা থাকত, তাহলে বিরজুর এই ঘোর অসুখে সে পয়সা আমি সিন্দুকে জমিয়ে রাখতাম? ছেলেটা কাল থেকে ক্রমাগত ভুল বকছে। রাতে কীরকম হাড়-কাঁপানে ঠান্ডা পড়েছিল, বলো? ওই ঠান্ডায় আমি সারারাত একফোঁটাও না ঘুমিয়ে ওকে গায়ে জড়িয়ে রেখেছি, যাতে ওর শরীরটা একটু হলেও গরম পায়। সারারাত ধরে ওর দাঁতকপাটি লাগার ঠকঠক আওয়াজ শুনেছি আমি। বিশ্বাস করো, যদি আমার টাকা থাকত…।”
আমাকে শেষ করতে না দিয়ে সে বলে উঠল, “শুনলাম, শেঠজি নাকি তোর সেই বোতলটা কিনতে চায়?”
আমার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, “হ্যাঁ। একবার ঘুরে গেছে এর মধ্যেই। মায়ের কুকি রাখার বোতলটা বিক্রি করব কি না জানতে এসেছিল।”
বিরক্তিতে ভরে উঠল পুরুতঠাকুরের মুখ, “কত দাম দেবে, বলেছে?”
“পাঁচটা দেশলাই। আর পনেরো টাকা। পুরোটাই আইন মেনে দেবে, বলছিল।”
পুরুতঠাকুর যেন তুষারচিতার মতো গরগরিয়ে উঠল, “হারামজাদা শকুনগুলো বড়ো বাড় বেড়েছে। দু-পয়সার মালিক হয়ে ধরাকে সরা ভাবতে শুরু করেছে এরা।… বোতলটা মির্জা সাবের হাতের তৈরি, না?”
“হ্যাঁ।”
“সারা ভারতের সর্বকালের সেরা কাচশিল্পীর ওই দুর্দান্ত কাজের মূল্য কিনা পাঁচটা দেশলাই আর পনেরো টাকা! এই গোটা সাদা পাহাড় এলাকায় তোর ওই বোতলটা ছাড়া মির্জা সাবের নিজের হাতে তৈরি কাজ কেউ চোখেও দেখেছে কখনও? ওটা তোর মা আনিয়ে দিয়েছিল না তোকে?”
“হ্যাঁ। আমার বিয়ের আগে মা উপহার দিয়েছিল। ওই দ্যাখো, ওখানে রাখা আছে।”
পলকা কাঠের তাকের উপর রাখা কাচের অসামান্য শিল্পকর্মটির দিকে মুগ্ধ চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখল সে। বোতলটার নকশা-করা ঘন নীল গলা বেঁকে আছে রাজহাঁসের ভঙ্গিমায়। লম্বাটে গলাটার নীচে স্বচ্ছ, মোটা কাচের তৈরি গোলক। দেখতে দেখতে পুরুতঠাকুরের চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠল; কয়েক মুহূর্তের জন্য নিশ্বাস ফেলতেও যেন ভুলে গেল সে।
এইরকম রাজহাঁসের মতো বাঁকানো গলার বোতল তৈরি করার জন্যই একসময় মির্জা সাবের ভারতজোড়া নাম ছিল।
তারপর আমার দিকে ফিরে সে বলল, “এই যে ভয়ংকর পাহাড়ি নিউমোনিয়া—যতক্ষণ না পোড়া অশ্বমূলের ধোঁয়া নাকে যাচ্ছে, ততক্ষণ সারবে না। কাছে আছে ও জিনিস?”
“এক ঠোঙা ভরতি আছে। কিন্তু থেকেই বা লাভ কী, পুরুতঠাকুর। আগুন তো নেই, আর আগুন জ্বালানোর উপায়ও নেই। যদি তোমার কাছ থেকে, বা অন্য কারও কাছ থেকে ধার করি, তাহলে দুজনকেই ধরে নিয়ে যাবে ওরা। কাঠে কাঠ ঘষে আগুন জ্বালালেও আইন ভাঙার দায়ে জেল হবে।”
পুরুতঠাকুর চুপ করে রইল। আমি বললাম, “সেইজন্যই ভাবছি, মা তো মরেই গেছে। মরা মানুষের স্মৃতি আঁকড়ে রেখে আর কী লাভ হবে? তার চেয়ে ওটা বিক্রি করে যদি ছেলেটার প্রাণ বাঁচানো যায়, সেটাই কি ভালো নয়? এত প্রিয়, এত দামি জিনিসটা দিয়ে দিতে হবে, ভাবলে খারাপ লাগছে, কিন্তু এ ছাড়া আর কী উপায় আছে, বলো?”
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, “সূর্যদেবের কাছে প্রার্থনা করব, তিনি যেন তোর ছেলেকে রক্ষা করেন।”
এ কথার কী-ই-বা উত্তর দেব? শেঠজির মতো অত্যন্ত পাজি লোকের পাষাণ হৃদয় সূর্যের আলোতেও গলবে কি?
পুরুতঠাকুর চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর বিরজু আবার গোঙাতে শুরু করল। অপূর্ব সুন্দর বোতলটাকে তাক থেকে নামিয়ে এনে ওর পাশে বসে রইলাম আমি। রোদ এসে পড়ছে বোতলটার সুন্দর গলায় আঁকা ফুলের নকশাগুলোর উপর।
এই জিনিস দিয়ে দিতে হবে আমায়!
বোতলের নীল গলাটায় অপরূপ নকশাগুলো দেখতে দারুণ লাগে বটে, কিন্তু এর আসল কাজের জায়গা হল নিখুঁত গোল মোটা পেটটা। স্বচ্ছ কাচের এই পেটের মধ্যেই কুকি-বিস্কুট-চকোলেট ভরে রাখা যায়। ওই ঠান্ডা, মসৃণ কাচের গায়ে আঙুল বুলিয়ে নিলাম একবার। মনের মধ্যে অনেকগুলো আনন্দের স্মৃতি জেগে উঠল।
মা যেদিন আমার হাতে মির্জা সাবের তৈরি এই অপূর্ব শিল্পবস্তুটি তুলে দিয়েছিল, তার সেই দিনের ঝকঝকে হাসিটা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। বহু দূরের ফিরোজাবাদ থেকে জিনিসটা অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়ে আনিয়েছিল মা। সেই তখনকার দিনে আমাদের মতো নিম্নবিত্ত পরিবারের পক্ষে সে ছিল অনেক টাকার ধাক্কা।
মা বলেছিল, “এর মধ্যে আমার নাতি-নাতনিদের কুকি-চকোলেট রাখবি তুই। আমি হয়তো ততদিন থাকব না, কিন্তু তুই ওদের বলে দিবি, দিদিমা ওদের জন্য এই সুন্দর উপহারটা রেখে গেছে।”
মা যখন মারা গেল, আমার বিরজুর বয়স তখন দুই। দিদিমার কথা ওর কিচ্ছু মনে নেই। তবে এই নীল হাঁসের গলাওয়ালা পেটমোটা বোতলটা ওর বরাবরই খুব প্রিয় ছিল। আমাদের পড়শিদের অনেকেই আমার বিয়ের পর এসে মির্জা সাবের শিল্পকলার প্রশংসা করে যেত। এ নিয়ে কারও কারও যে টুকটাক ঈর্ষাও হত, তাও আমি দিব্যি বুঝতে পারতাম। ওরা বোধহয় ভাবত, আমাদের মতো গরিবের বাড়িতে এত দামি একটা জিনিস মানায় না।
শেঠজি নিজেও অবশ্য এই দলেই পড়ে।
দুপুর পেরিয়ে বিকেল এসেছিল, তারপর তাও ফুরিয়ে আসছে। সূর্য সরে যাচ্ছে পশ্চিম পাহাড়ের দিকে। ক্যামেলিয়া ফুলের মতো লালচে গোলাপি আভা ছড়িয়ে পড়ছে বরফ-ঢাকা পাহাড়চূড়ার গায়ে। অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গেই আমার আবার ভয় করতে শুরু করেছে; বুড়ি শরীরটার হাড়ের মধ্যে যেন কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে কনকনে ঠান্ডাটা। অর্ধচেতন অবস্থায় পড়ে আছে বিরজু; মাঝেমধ্যে অদ্ভুত একটা ‘গোঁ গোঁ’ শব্দ করছে।
সামনে পড়ে আছে দীর্ঘ রাত্রি।
শক্ত করে হাত মুঠো করে বসে রইলাম আমি। আবার সূর্য ওঠার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আমাকে। করতেই হবে।
***
সকালবেলা দরজায় আওয়াজ পেয়ে এগিয়ে গেলাম সেদিকে। শেঠজি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে; তার পরনে লম্বা, কালো কোট আর মাথায় লাল পাগড়ি। দরজা খুলতেই একটা ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা এসে ঢুকল ঘরের মধ্যে। শেঠজির সরু ঝাঁটার মতো গোঁফ কেঁপে উঠল একবার।
আমি বললাম, “ভেতরে আসুন, শেঠজি; আমি দরজাটা লাগিয়ে দিই। ঘরটাকে যতটা সম্ভব গরম রাখার চেষ্টা করছি।”
ঘরের মধ্যে কয়েক পা ঢুকে এসে শেঠজি নাকের মধ্যে ‘ঘোঁত’ করে একটা আওয়াজ করল। “তাতে যে খুব একটা কাজ হচ্ছে বলে তো মনে হচ্ছে না।”
মনে মনে লোকটাকে একটা বাজে গালাগাল দিলাম আমি, কিন্তু মুখে কাষ্ঠহাসি হেসে বললাম, “সেইজন্যই তো আপনি আমাকে সাহায্য করতে এসেছেন, না?”
তার কালো চোখগুলো স্থির হয়ে রইল আমার মুখের উপর। “মানুষজনকে সাহায্য করার ব্যাপারে আমার খুব একটা সুনাম নেই, তুই জানিস, যমুনা। এখানে তোর সঙ্গে স্রেফ ব্যাবসা করতে এসেছি, ভুলে যাস না যেন। আমার যা চাই, তুই দিবি; তার বদলে আমি তোকে সেই জিনিসের উপযুক্ত দাম দেব। ব্যাস, ফুরিয়ে গেল।”
আমি ‘ফোঁস’ করে উঠলাম। “উপযুক্ত দাম? ভারতবিখ্যাত শিল্পীর অমূল্য শিল্পকর্মটি আপনি আমার কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছেন, আর তার বদলে দিয়ে যাচ্ছেন দু-চারটি কুত্তা-বিস্কুট। এই আপনার ব্যাবসার নমুনা?”
মনে হল, উত্তর দেওয়ার আগে গোঁফের তলায় কয়েকবার চিবিয়ে নিল সে কথাগুলো, “কুত্তার যা পাওনা, তা-ই তো সে পাবে। দুনিয়ার এই নিয়ম, বুঝলি? শোন যমুনা, তোর ছেলে বিরজু বরাবর গাঁয়ে ঝামেলা পাকিয়ে এসেছে। তোদের ভাগ্য ভালো, পুলিশ ডেকে ওকে ধরিয়ে দিইনি এখনও। এই তো গত মাসেই আমার দুই কর্মচারীকে ধরে বেদম মারধর করেছিল ও। কেন? তারা নাকি ওর মা-কে নিয়ে খারাপ কথা বলেছিল।”
আমি বললাম, “সত্যিই তো বলেছিল ওরা। কোন ছেলে তার মায়ের নামে নোংরা কথা চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনবে, শেঠজি? আমি সব কথাই শুনেছি। বিরজু যখন আপনার লোক দুটোকে ধোলাই দিচ্ছিল, তখন আপনি নিজে তো দূরে ভীতুর মতো দাঁড়িয়ে চুপটি করে দেখছিলেন। এত নাকি ক্ষমতা আপনার; কিন্তু যখন বিরজু খেপে গেল, তখন আপনারও সাহস হয়নি ওকে থামিয়ে নিজের কর্মচারীদের বাঁচানোর। গাঁয়ের লোকের আলোচনায় অনেক কথা আমার কানেও আসে। ঘটনাটা ঠিক বললাম তো, শেঠজি?”
তার মুখ তার পাগড়ির মতোই লাল হয়ে উঠল। “আজ যদি তোকে দেশলাইগুলো না দিয়েই আমি ফিরে যাই, তিন দিনের মধ্যে পাহাড়ি নিউমোনিয়ায় তোর ওই অপদার্থ ছেলেটার মরণ কেউ আটকাতে পারবে না। নিজের গাঁয়ের বাইরের কোনো আগুন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে দেশলাই কিনতে গেলেও তোকে পুলিশ ধরে জীবনের মতো চালান করে দেবে। কাঠ ঘষে আগুন জ্বাললেও তোর একই গতি হবে। তোর ভালোর জন্যই বলছি, মুখটা সামলে চল, বুড়ি। আজ দরকারটা আমার চেয়ে তোর অনেক বেশি।”
আমি থমকে গেলাম। ভুল বলছে না লোকটা। ও যত বড়ো লোভী শয়তানই হোক, কথাটা একদম ঠিক।
আজ দেশলাই না পেলে বিরজুকে বাঁচানো যাবে না।
আমার ভ্রূকুটি মিলিয়ে যেতে দেখে খিকখিক করে হাসল সে। “এবার নিয়ে আয় জিনিসটা। বিখ্যাত শিল্পীর শিল্পকর্মটি আগে ভালো করে দেখি।”
বোতলটা এনে তার বাড়ানো হাতে সাবধানে ধরিয়ে দিলাম আমি। ঠিক যেন একটা লম্পটের মতো লালসা-মাখানো আঙুল দিয়ে সে বোতলটার সুন্দর গলায় স্পর্শ করতে লাগল। লম্বা, সরু গোঁফের আগা আবার তিরতির করে কেঁপে উঠল তার। দৃশ্যটা আমার কাছে এতটাই অসহনীয় লাগল যে, আমি মুখ ফিরিয়ে জানালার বাইরে তুষার-ঢাকা পাহাড়চূড়ার দিকে তাকিয়ে রইলাম।
সাদা তুষারের উপর রোদ এমন উজ্জ্বলভাবে ঝলমল করছে যে, আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ফিরে তাকিয়ে দেখি, লোকটা হাঁ করে তখনও নিরীক্ষণ করছে হাতের বোতলটাকে। নীলচে ময়ূরকণ্ঠি কাচের ফুল-পাতার নকশা-করা গলায় সকালের আলো ঠিকরে পড়ছে। সেই আলোয় বিভ্রম হচ্ছে, ফুলগুলো যেন হালকা বাতাসে অল্প অল্প মাথা নাড়ছে। নীরব, অসহায় রাগ আর বিতৃষ্ণা চোখে নিয়ে আমি দেখতে লাগলাম, শেঠজির সরু সরু, লোভী মাকড়সার দাঁড়ার মতো আঙুলগুলো কিলবিল করছে বোতলের গলার নকশাগুলোর উপর। পেটের মধ্যে কী যেন একটা পাকিয়ে উঠল আমার। মনে হচ্ছিল, লোকটার হাত থেকে জিনিসটা কেড়ে নিয়ে ঘাড় ধরে ওকে এ ঘর থেকে দূর করে দিই।
শুধু আমার বিরজুটা যদি আজ সুস্থ থাকত…!
ডান হাতে বোতলটার গলা ধরে বাম হাতে কোটের পকেট থেকে একটা ছোট্ট, স্বচ্ছ পলিথিনের প্যাকেট বার করে আনল শেঠজি; আমার দিকে ওটা ছুড়ে দিয়ে বলল, “খাসা জিনিসটা, বুঝলি? এই নে দাম।”
একনজরে তাকিয়ে দেখলাম, প্যাকেটটার মধ্যে আছে মাত্র তিনটে দেশলাই বাক্সো, একটা দশ টাকার নোট আর একটা দু-টাকার কয়েন। অবাক হয়ে মুখ তুলে কী একটা বলতে গিয়ে দেখি, শেঠজি ততক্ষণে দরজার দিকে হাঁটা দিয়েছে।
খেপে গিয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম লোকটার উপর। তার কাঁধ খামচে ধরে বলে উঠলাম, “এ কী? এত কম দামে তো কথা হয়নি!”
শিয়ালের মতো ধূর্ত একটা হাসি ঠোঁটে নিয়ে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল সে। “ওইটুকুই পাবি, ওর বেশি নয়। দেখ, জিনিসটা বেশ সুন্দর ঠিকই, কিন্তু হাতে নিয়ে দেখছি, আমি যা ভেবেছিলাম, তার চেয়ে সাইজ়ে অনেক ছোটো। আর বেশ হালকাও বটে।”
‘তুইতোকারি’ করা হয়ে গেল আমার। চিৎকার করে বললাম, “তাতে আমি কী করব? হয় পুরো দাম দে, নয়তো আমার জিনিস আমাকে ফেরত দে বুড়ো শকুন। এইভাবে দিনে ডাকাতি করে পালাতে দেব না আমি তোকে।”
এইবার দাঁত বেরিয়ে এল তার, “কুত্তার যা পাওনা, তা-ই তো সে পাবে। আর ঝামেলা বাড়াস না যমুনা। নয়তো ফল খারাপ হবে।”
তার হাত থেকে আমি ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করছিলাম বোতলটা। এর মধ্যেই একবার চোখ গেল বিছানায় শুয়ে-থাকা বিরজুর দিকে। কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান ফিরেছে তার। জ্বরের ঘোরে টকটকে লাল চোখ নিয়ে সে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে, কিন্তু উঠে এসে মা-কে সাহায্য করার মতো শক্তি আর তার দেহে নেই।
শেঠজির হাতে নখ দিয়ে আঁচড়ে দিলাম আমি। “ছাড় আমাকে, হারামজাদি ডাইনি!” বলে আর্তনাদ করে উঠল সে।
আর সেই মুহূর্তেই গোটা আকাশ ভেঙে পড়ল ঘরের মধ্যে।
না, আকাশ নয়, পড়ল মির্জা সাবের তৈরি-করা বোতলটা। শেঠজির হাত থেকে ফসকে গেল জিনিসটা; আর আমি পৃথিবীর সব আতঙ্ক চোখে নিয়ে দেখতে লাগলাম, বোতলটা অনিবার্যভাবে নেমে আসছে শক্ত মেঝের দিকে; তার রাজহাঁসের মতো বাঁকানো গলাটা যেন প্রলম্বিত হয়ে আসছে মাটির টানে।
মেঝে থেকে যখন ‘ঝনঝন’ শব্দটা বিস্ফোরণের মতো উঠে এল, ততক্ষণে আমি চোখ বন্ধ করে ফেলেছি।
“কুত্তার বাচ্চা! মরণ হয় না তোর?”
নিজে বোঝার আগেই যেন গলা ছিঁড়ে চিৎকারটা বেরিয়ে এল আমার। পায়ের কাছে জড়ো-হওয়া ভাঙা কাচের স্তূপটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে শেঠজিও। অত সুন্দর নীল গলাটা পুরো গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেছে। একদিকে উলটে পড়ে আছে গলাকাটা বোতলের গোল পেটটা।
পাক্কা শয়তানের মতো একটা হাসি ফুটে উঠল শেঠজির ঠোঁটে। চট করে দেশলাইয়ের প্যাকেটটা কুড়িয়ে নিয়ে সে দৌড় দিল দরজার দিকে। “মাল পাইনি, তাই দাম দেওয়ার গল্প নেই আর।”
আমি ছুটলাম তার পিছনে। “মড়াখেকো শকুন! জিনিসটা ভাঙার আগেই তুই ওটা কিনেছিলি আমার কাছ থেকে, দামও দিয়ে দিয়েছিলি। তারপর তুই ওটা ভাঙলে আমার কী দায়? আমার দেশলাই আমাকে দে বলছি এখুনি!”
পাহাড়ি নেকড়ের মতো গরগরিয়ে উঠল লোকটা, “এতগুলো খারাপ কথা আমাকে বলার পর আর কোনো দয়া পাওয়ার আশা ছেড়ে দে যমুনা। আর তোর ওই হারামি ছেলেটাও তিন দিনের মধ্যে মরবে, কেউ বাঁচাতে পারবে না। সেই হবে তোদের উচিত শিক্ষা!”
অসহায় রাগে চিৎকার করে অভিশাপ দিলাম আমি, “বজ্রাঘাতে মরবি তুই!”
খ্যা খ্যা করে শয়তানি হাসি হাসল শেঠজি, “এত জলদি মরছি না রে আমি, ডাইনি। কিন্তু বিরজুর আর সময় বেশি বাকি নেই। আগুন চাই তোর? তোকে আগুনই দেব আমি। শোন, ঠিক তিন দিন পরে তোর এই দরজায় আবার আসব। এবার আসব তৈরি কফিন নিয়ে। সেদিন এসে তোকে বিনা পয়সায় একটা দেশলাই বাক্সো দিয়ে যাব, যাতে তোর মরা ছেলের জন্য ধূপ আর মোমবাতি জ্বালাতে পারিস। কথা দিয়ে গেলাম আজ।”
দরজা খুলে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সে।
পাল্লা দুটো লাগিয়ে এসে আমি হা-ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম ঘরের ঠান্ডা মেঝের উপর। পাশেই ছড়িয়ে আছে নীল কাচের অসংখ্য ভাঙা টুকরো—আমার মায়ের অপূর্ব সুন্দর কুকি বোতলের ধ্বংসাবশেষ।
মুখ তুলে দেখলাম, বিরজু চুপ করে পড়ে আছে। অনিয়মিত ছন্দে ওর বুক উঠছে-পড়ছে, আর ওর আধখোলা মুখের মধ্য থেকে একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে। ওর চোখ বন্ধ, দেহ স্থির। আবার বোধহয় অচেতন হয়ে গেছে ছেলেটা।
তাতেও যেন একটু স্বস্তি পেলাম।
অন্তত এই মুহূর্তে যে কী নরকযন্ত্রণার মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হচ্ছে, ও তার কিছুই বুঝতে পারবে না।
জানালা দিয়ে এসে পড়েছে রোদ। সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে সূর্যদেবের কাছে প্রার্থনা করলাম, “প্রভু, আমার ছেলের মঙ্গল করো। ওকে রক্ষা করো। তবু যদি ওকে যেতেই হয়, তাহলে যেন অন্তত শান্তিতে যেতে পারে।”
চোখ বন্ধ করলাম আমি। মায়ের হাসিমুখটা ভেসে উঠল মনশ্চক্ষে। দেখলাম, লাল ফ্রক-পরা ছোট্ট আমি মায়ের হাঁটু জড়িয়ে ধরে আছি; তার পিঠ বেয়ে কাঁধে ওঠার চেষ্টা করছি। ঝুঁকে পড়ে আমাকে তুলে নিল কোলে; গান গাইতে লাগল, “সুয্যিকণা, চাঁদের কণা,/ আমার সোনা, আমার ছানা।” তারপর আমার হাতে একটা কুকি ধরিয়ে দিয়ে মা আমাকে নিয়ে চলল বাইরের পাহাড়ের ধারে ঝকঝকে রোদ-মাখা সবুজ খেতের দিকে।
জানালা দিয়ে আসা জোরালো হাওয়ার ঝাপটা গালে লাগতেই আমার দিবাস্বপ্নটা ভেঙে গেল। চোখ খুলে দেখলাম, বিছানার উপর বিরজু একইভাবে পড়ে আছে। ওর শুকনো ঠোঁটগুলো একটু ফাঁক হয়ে রয়েছে, মুখটা লাল, খুব কষ্ট করে শ্বাস নিচ্ছে। আমার পাশে এখনও জমে আছে বোতলটার ভাঙা গলার টুকরোগুলো; তাদের উপর সকালের রোদ চিকমিক করছে।
মির্জা সাবের অমূল্য শিল্পকর্ম—সব শেষ!
ওদিকে দেখতে বড়ো কষ্ট হল। বোতলটার পেটমোটা গোলাকার নীচের অংশটা এখনও অক্ষত আছে। সেটাকেই তুলে নিলাম হাতে।
চোখে জল এল আমার। আজকের দিনটা বড়ো খারাপ। মায়ের স্মৃতিটুকুও গেল, আর তার সঙ্গে গেল বিরজুকে বাঁচানোর শেষ আশাটুকুও।
এমন অপদার্থ মা আমি, ছেলেটাকে রক্ষা করার জন্য কিছুই করতে পারলাম না।
চারপাশে যেন ঘোর অন্ধকার ঘিরে ধরছে আমাকে। কিন্তু কোথায় পাব এই অসহায় অন্ধকার দূর করার মতো একটুখানি আলো?
একফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। দেখতে পেলাম, জলের ফোঁটাটা নেমে এল মেঝের উপর রাখা গলা-ভাঙা বোতলের গোলাকার পেটের মধ্যে। দুপুরের রোদে মহামূল্য রত্নের মতো চিকমিক করতে লাগল জলবিন্দুটা। তার উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব এসে পড়ল মেঝের গায়ে, অশ্বমূলের ঠোঙাটার পাশে।
হঠাৎ একটা অদ্ভুত বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়।
জানি, পাগলামি করছি। জানি, এখন আমার মাথা ঠিকমতো কাজ করছে না। তবু… একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী?
জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখলাম। মনে হল, দূরের রোদ-ঝলমল তুষার-ঢাকা পাহাড়চূড়াগুলো যেন আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। উঠে দাঁড়িয়ে স্নানের ঘর থেকে এক মগ জল নিয়ে এলাম। মায়ের কুকি বোতলটার নীচের অক্ষত অংশটাকে যখন জানালার পাশে এনে বসিয়ে তার মধ্যে জল ঢালছি, বুঝতে পারলাম, আমার হাত কাঁপছে।
স্বচ্ছ জলে ভরে উঠল ভাঙা বোতলের মোটা কাচের গোল পেট। তার তীব্র উজ্জ্বল ছায়াটা বেরিয়ে এসে পড়ল মেঝের উপর। না, একে ‘ছায়া’ বলা বোধহয় ঠিক হবে না; আসলে জলভরা গোল কাচের পাত্রটার গা থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে একটা ছোট্ট গোল বিন্দুতে এসে পড়ল কেন্দ্রীভূত আলোকরশ্মি।
খোলা মাঠে ছুটে-বেড়ানো টাট্টু ঘোড়ার মতো লাফাচ্ছে আমার হৃৎপিণ্ড। ঠোঙা থেকে একমুঠো কালো অশ্বমূলচূর্ণ এনে রাখলাম মেঝেতে। জলভরা কাচের গোল পাত্রটা নেড়েচেড়ে ঠিক করে বসালাম, যাতে ওই অত্যুজ্জ্বল আলোকবিন্দুটা ঠিক অশ্বমূলের স্তূপটার উপর গিয়ে পড়ে। মনে হল, কানের পাশে যেন মায়ের উৎসাহভরা কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি।
না, মাথাটা শান্ত রাখতে হবে। হাত কাঁপলে চলবে না। প্রথম যে গানটা মনে এল, সেটাই গুনগুন করে গাইতে লাগলাম আমি: “সুয্যিকণা, চাঁদের কণা,/ আমার সোনা, আমার ছানা।”
গলা কেঁপে যাচ্ছে। বুড়ি-হয়ে-যাওয়া পাঁজরের ভেতরে জোরে জোরে ধাক্কা মারছে হৃৎপিণ্ডটা। যদি এতে কাজ না হয়, তাহলে আর…!
“মা আছে তো, সোনা! মা কাছে থাকলে কোনো ভয় নেই!”
মনে হল, আমার মা যেন খুব মিষ্টি করে কথা বলছে আমার পাশে বসে, ভরসা দিচ্ছে। আমিও কী একটা ঘোরের মধ্যে আমার বিরজুর দিকে তাকিয়ে এই কথাগুলোই তাকে ফের শোনাতে লাগলাম।
তারপর তাকিয়ে দেখলাম, কালো অশ্বমূলের গুঁড়োর মধ্য থেকে পাকিয়ে উঠছে সরু ধোঁয়ার ধূসর রেখা। ঘরের বাতাসে তার পোড়া গন্ধ ভেসে আসছে নাকে।
সেই মুহূর্তে মনে হল, সূর্যদেব, যিনি আমাদের সব অন্ধকার দূর করে আলো দিচ্ছেন, শীত দূর করে তাপ দিচ্ছেন, অসহায় দুঃখে বেঁচে থাকার রসদ দিচ্ছেন—তিনি অবশেষে আমার প্রার্থনা শুনেছেন।
চোখের জল মুছে চিমটেয় করে ধোঁয়া-ওঠা কালো অশ্বমূল কিছুটা তুলে নিলাম মেঝে থেকে। এসে বসলাম আমার ছেলের পাশে। বললাম, “বিরজু, একবার বুক ভরে শ্বাস নে তো বাবা।”
***
শেঠজি এককথার মানুষ। ঠিক তিন দিনের মাথায় আমার ঘরের দরজায় কফিন নিয়ে এসে হাজির হল সে।
আমার বাড়ির বাইরে ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চাপিয়ে কফিনটা নিয়ে এসেছে সে। সকাল ঠিক আটটায় আমার দরজায় কড়া নাড়ল হতচ্ছাড়া।
আমার দিকে তাকিয়ে একবার মাথা নাড়ল বিরজু, তারপর এগিয়ে গেল দরজা খুলতে। আমি পিছন থেকে দেখতে লাগলাম দৃশ্যটা।
শেঠজির হাঁ-মুখের প্রস্থ আর গোঁফের চিড়বিড়ানি দেখে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, যে ব্যক্তি দরজা খুলেছে, তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য সে আদৌ প্রস্তুত ছিল না।
অবিশ্বাসভরা দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সুস্থ বিরজুর শক্তপোক্ত দেহটার দিকে শেঠজি তাকিয়ে নিল একবার। তারপর তার চোখ গেল ওর ভ্রূকুটিভরা মুখের দিকে।
বিরজুর হাতে ধরা আছে রামদা।
লাল পাগড়ি কেঁপে উঠল মাথার সঙ্গে সঙ্গে। ঢোঁক গিলে সে একবার শুধু বলল, “তুই… তুই…!”
বিরজু মাথা গরম করল না; ঠান্ডা গলায় বলল, “একটা কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি, শেঠজি। আমার মায়ের সঙ্গে যদি আর কোনোদিন ওইভাবে কথা বলতে শুনি, কফিনটা কিন্তু একদিন তোমারই কাজে লেগে যাবে। আর, ওইসব পুলিশ-ফুলিশের ভয় আমাকে দেখিয়ে যে কোনো লাভ নেই, এ কথাটা তোমার চেয়ে ভালো আর কে-ই-বা জানে?”
শেষবারের মতো একটু বীরত্ব দেখিয়ে মুখরক্ষা করতে চাইল শেঠজি, “এই গ্রামের সব চেয়ে বড়ো ব্যবসায়ী আমি। কত কোটি টাকার ব্যাপার আছে আমার, খবর রাখিস? তোদের মতো হাভাতেদের সাহস হয় কী করে এইভাবে আমার সঙ্গে কথা বলার?”
বিরজু তার চোখে চোখ রেখে বলল, “কুত্তার যা পাওনা, তা-ই তো সে পাবে।”
হাতের দা-টা পেন্ডুলামের মতো দুলতে লাগল তার। আমি এগিয়ে এসে দাঁড়ালাম আমার ছেলের পাশে। দু-চোখে ঘৃণা নিয়ে শেঠজি আমার দিকে তাকিয়ে রইল।
আমি বললাম, “ও, আরেকটা কথা। আইন মেনে আগুন তৈরি করার এই বিদ্যাটা আমি এর মধ্যেই গাঁয়ের সকলকে শিখিয়ে দিয়েছি। কোটি টাকার ব্যাবসার কথা বলছিলে না এখুনি? ক-দিন অপেক্ষা করে দ্যাখো, দেশলাইয়ের দাম খুব শিগগির পড়ল বলে।”
খুশি মনে আমরা দেখলাম, বিড়বিড় করে কী সব গালাগালি দিতে দিতে লোকটা তার গাড়িতে চেপে চলে যাচ্ছে।
সকালের রোদের তাপটা বড়ো আরামের। আমরা মা-ব্যাটা আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম ওখানে। বিরজুর মাথার তামাটে চুলগুলো ঘেঁটে দিলাম আদর করে। তারপর বললাম, “ভেতরে চল বাবা। একটু চা করব; আগুন জ্বালাতে হবে।”
Tags: দশম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়