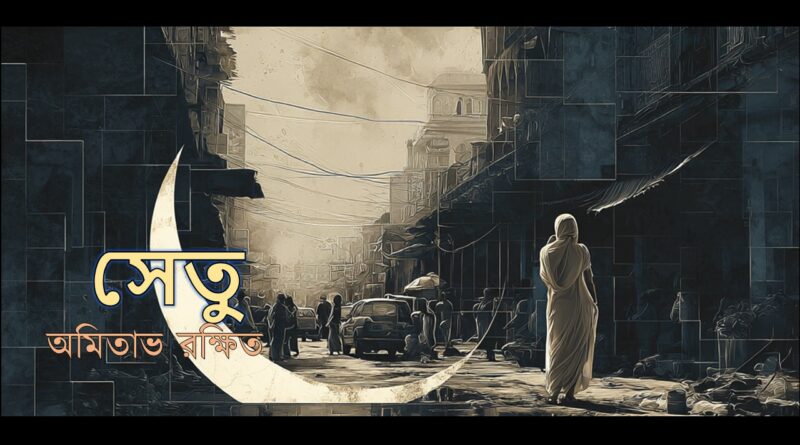সেতু
লেখক: অমিতাভ রক্ষিত
শিল্পী: টিম কল্পবিশ্ব
পূর্বকথা
A mind not to be changed by place or time
The mind is its own place, and in itself
Can make a heav’n of hell, a hell of heav’n.
— (‘Paradise Lost’—John Milton)
স্থান বা কালভেদে নেই চেতনার অবক্ষয়—
তার স্থিরতা আপনাতেই।
সেই চেতনার আত্মসমন্বয়ে, স্বর্গও হতে পারে নরক
আর নরক স্বর্গ। (অনু: অমিতাভ রক্ষিত)
সেদিন পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের ওপরে উঠেছিল একটি বাঁকা চাঁদ। ইদের চাঁদের মতো শীর্ণ। বাইরে থেকে দেখলে, অর্থাৎ, যে-কোনো একটি ভ্রাম্যমাণ স্পেস স্টেশন থেকে, অথবা কোনো মহাকাশযান থেকে পর্যবেক্ষণ করলে অবশ্য তা বোঝা যাবে না। কারণ আমাদের প্রিয় নীল মার্বেলটি, তার বায়ুমণ্ডলটিকে একটি পেঁজা তুলোর কাটাছেঁড়া কম্বল করে, সদাই তাকে গায়ে জড়িয়ে ধরে থাকে। ফলে বাইরে থেকে তার ভেতরের অবস্থানটা ঠিক বোঝা যায় না।
আমাদের সূর্যের নৈর্ঋত কোণে, যে অঞ্চলে প্রতি এগারো বছর অন্তর তার মেরুবদল হয়, আর যেখানে প্রচণ্ড চৌম্বক শক্তির বিকিরণের কারণে পৃথিবীর আশপাশ থেকে কোনো পার্থিব যন্ত্র দিয়ে সেই অঞ্চল ভালো করে পর্যবেক্ষণ করা যায় না (অন্তত আজ পর্যন্ত), সেইখানে অনাদিকাল থেকে লুকিয়ে আছে মহাজাগতিক একটি প্রতিরক্ষা সমিতির একটি স্পেশ স্টেশন, কয়েকটি মহাকাশযান ও প্রয়োজনীয় কিছু স্থাপত্য। এদের কর্তব্য, মহাকাশের বিভিন্ন আগ্রাসী সমাজের আক্রমণের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করা—অন্তত যতদিন না পৃথিবীর নিজস্ব প্রযুক্তি তার প্রতিবেশীদের সমকক্ষ হচ্ছে। পৃথিবী একটি অতি বিশিষ্ট জায়গা, যার পরিপূর্ণ বিকাশ সারা মহাজগতের কাছেই খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার সৃষ্টি হয়েছে অপেক্ষাকৃত নবীন কালে বলে শক্তির মাপে সে এখনও বেশ দুর্বল। তাই সেই প্রতিরক্ষা সমিতির কাছে আগে পরীক্ষিত না হয়ে, কোনো ‘অপ্রাকৃত’ বস্তুই পৃথিবীর বলয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না।
সেই ইদের চাঁদের দিনে প্রতিরক্ষা সমিতির থানায় টেনে আনা হল অপেশাদার একটি একক মহাকাশযানকে—একজনই মাত্র আরোহী তার। তার গন্তব্য পৃথিবী, উদ্দেশ্য সেখানে গিয়ে মৃত্যুর আস্বাদ পাওয়া।
“তুমি পৃথিবীতে যেতে চাও—মরতে? সে আবার কী!”
“আজ্ঞে হ্যাঁ, ম্যাডাম। আমাকে এমন করে তৈরি করা হয়েছিল যে না প্রকৃতি, না প্রাণী—কেউই আমাকে পর্যুদস্ত করতে পারে না।আমার মৃত্যু নেই—আমি অমর।”
“ও, তুমি রোমানব! বুঝতে পারিনি। তোমাদের প্রযুক্তির প্রশংসা করি! কিন্তু মরতে এতদূর এসেছ কেন? তোমার ব্যাটারি প্যাক ফুরিয়ে গেলেই তো তুমি আর ‘নেই’! বাড়িতে বসেই তো মরতে পারতে।”
“না ম্যাডাম, আমাকে সৃষ্টিই করা হয়েছিল এমন একটি বিশেষরকমভাবে, যে আমি কোনোভাবেই মরতে পারি না। কিন্তু আমার সৃষ্টির বহু যুগ পরে, যখন আমাদের সূর্যটি সুপারনোভা হবার অবস্থায় পৌঁছে গেল, তখন আমাদের গ্রহের মানুষেরা বাধ্য হয়ে অন্য আর-একটা গ্রহে চলে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল সমস্ত প্রাণীকেই, কেবল শেষ মুহূর্তে একটি বিশেষ কারণে, আমারই কেবল শেষ জাহাজটি ধরবার সুযোগ হল না। তারপর থেকে বোধহয় কোটি কোটি বছর কেটে গিয়েছে, আমাদের গ্রহ-সূর্যও ধ্বংস হয়ে গিয়েছে কতদিন! কিন্তু আমার যে ধ্বংস নেই! আমি আমার একাকিত্বের অভিশাপ নিয়ে বছরের পর বছর কাটিয়ে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি। শেষে, এই সম্প্রতি খবর পেয়েছি যে, পৃথিবীতে সব প্রাণীরই মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়, মৃত্যু এসে তাদের যথার্থ শান্তি এনে দেয়। তাই মৃত্যুর আশায় আমি চলেছি পৃথিবীর পথে!”
ম্যাডাম এবারে একটু নড়েচড়ে বসলেন। তারপরে একটু ভেবে বললেন, “দ্যাখো, তুমি যতটা ভাবছ, ব্যাপারটা কিন্তু ততটা সহজ নয়। পৃথিবীতে শুধু প্রাণীদেরই মৃত্যু হয়, সব কিছুর মৃত্যু হয় না। পাথর, ধাতু—এসবের জন্মও হয় না, মৃত্যুও হয় না। তুমি তো বোধহয় বেশিটাই ধাতু দিয়ে তৈরি। পৃথিবীতে গেলেই তোমার মৃত্যু হবে কি না বলা শক্ত। তুমি সচেতন বটে, কিন্তু ঠিক তো প্রাণী নও—কাজেই সেই ‘নাটের গুরু’ তোমাকে প্রাণী হিসেবে দেখবেন কি না বলা মুশকিল। তবে তুমি যদি স্বেচ্ছায় রাজি হও, তবে তো আমরা তোমাকে এখানেই শল্য দিয়ে বিচ্ছেদ করে তোমার চেতনার অবসান ঘটিয়ে দিতে পারি খুব সহজে…”
“না না, সেরকমভাবে মৃত্যু খুঁজছি না আমি। তাহলে তো আমি কবেই নিজের মাথাটা কেটে-ছিঁড়ে সব কিছুর শেষ করে ফেলতাম… কিন্তু, ম্যাডাম, ‘নাটের গুরু’ মানে?”
“ওঃ, ওই, মানে আমরা তো আর প্রকৃতির সব রহস্যের সমাধান করতে পারিনি এখনও—বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিতে যতই অগ্রসর হই-না কেন! জন্মমৃত্যু তেমনই একটি অমীমাংসিত রহস্য। কাজেই যা বুঝি না, তাকে অন্যান্য সকলের মতো আমিও ‘বিধাতা’র নামেই চালিয়ে দিই। নাটের গুরু বলতে তাঁকেই বোঝাচ্ছিলাম। তবে তার মধ্যে যদি একটু ব্যঙ্গ মিশে আছে, ভেবে থাকো, তবে জানবে যে ভক্তি আমার সাবজেক্ট নয়!”
“না না, আমিও আপনার মতন করেই ভাবি, কাজেই সে ব্যাপারে মতভেদ কিছু নেই আমার। তবে আমি দূর থেকে হলেও, পৃথিবীর ওপরে অনেক রিসার্চ করে তবেই এসেছি, কিন্তু এই সম্ভাবনাটাতো কখনও ভেবে দেখিনি। এখন আপনার সাবধান বাণী শুনে একটু চিন্তা হচ্ছে—যদি মৃত্যু আমাকে না নেয়, তাহলে?”
“দ্যাখো, আমি তোমাকে নিরুৎসাহ করতে চাইনি, কারণ আমি নিজেই জানি না আমি ঠিক বললাম কি না। কিন্তু জানো তো, পৃথিবীতে সব কিছুরই একটা চক্র আছে, পরম্পরা আছে। জীবন একটা চক্র, অস্তিত্বও একটা চক্র। জন্ম-মৃত্যু-জন্ম একটা চক্র… তেমনি…”
“জন্মমৃত্যু, আবার জন্ম! মানে? মৃত্যুর পরে আবার মৃত্যু হলে বুঝি জন্ম হয়? কিছু রোমান্টিক কবিতা ছাড়া তো আর কোথাও পড়িনি যে মৃত্যুর পরে আবার মৃত্যু হয়…”
“হা হা, তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ? না, আসলে ব্যাপারটা খুবই গভীর। সব পৃথিবীতেই এই নিয়ে কোটি বছর ধরে অনেক চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। কিন্তু কিছু সমাধান হয়েছে বলে তো শুনিনি। তবে শুনেছি যে মৃত্যুর পরে আত্মা, মানে শরীরের ভেতরের অবিনেশ্বর সত্তাটির, আবার পুনর্জন্ম হয়। এটা একটি মতবাদ…”
“হ্যাঁ, হিন্দু দর্শনের মতবাদ… আমি জানি…”
“তাহলে? তাহলে সেটা বর্তুল হল না? মানে চক্র! সময়ও তো আসলে চক্র—অন্তত এই পৃথিবীতে। বৈজ্ঞানিক বলে গেছেন, সময় আপেক্ষিক! তবে সময়চক্রের ব্যাসার্ধ, জীবনচক্রের ব্যাসার্ধের থেকে অনেক অনেকগুণে বড়ো। তাই জীবনের জানলা দিয়ে মেপে দেখলে সময়কে সরলরেখা বলেই মনে হবে। আমার মনে হয় যে, তুমি যদি মানুষের মতন করে মরতে চাও, তাহলে তোমাকে আগে জন্মাতে হবে কোনোভাবে। একবার জন্মে গেলে, বিশেষ করে যদি মানুষ হয়ে জন্মাতে পারো, তাহলে মনে হয়, তোমার মৃত্যু আপনি আসবে জীবনের নিয়মে। তবে তার আগে তোমাকে পুরো একটি জন্ম কাটাতে হবে মানুষ হয়ে, মানুষের সুখে-দুঃখে, তবেই মৃত্যু তোমাকে গ্রাহ্য করবে। তুমি যদি তা-ই করতে রাজি থাক, তাহলে আমি সকলের সঙ্গে কথা বলে দেখি, আমরা কীভাবে তোমাকে সাহায্য করতে পারি।”
ম্যাডামের কথাগুলো শুনে অমর নীরব হয়ে গেল। ম্যাডাম দেখলেন অমর গভীর চিন্তায় মগ্ন। তখন একটুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বললেন, “তুমি এক কাজ করো, অমর। তুমি আমাদের অতিথিশালায় গিয়ে একটু বিশ্রাম করো, আর ব্যাপারটা ভেবে দ্যাখো ভালো করে। এটা কোনো সহজ সিদ্ধান্ত নয়—কত লোকে আজীবন প্রার্থনা করে চলে মানবজীবনের জন্ম-দুঃখ-কষ্ট-মৃত্যু—এই চক্র থেকে রেহাই পেতে। আর আমি কিনা তোমাকে সেই কষ্টই গ্রহণ করতে বলছি স্বেচ্ছায়! সময় তো লাগবেই ভাবতে…”
চমকে উঠে অমর তাড়াতাড়ি বলল, “না না, এতে চিন্তা করার কী আছে! আমি তো আর আমার গ্রহে ফিরে যাচ্ছি না কোনোভাবেই! কাজেই আপনি এখন শুধু বলুন, আমি কী করে মানুষ হয়ে জন্মাতে পারি।”
“আচ্ছা বেশ। তবুও তুমি কিছুদিন এখানে কিছুদিন বিশ্রাম করো। আমি আমাদের ডাক্তার-বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে কথা বলে দেখি, তাঁরা কী বলেন।”
***
কিছুদিন অপেক্ষার পরে অমরের আবার ডাক পড়ল ম্যাডামের ঘরে। তিনি বললেন, “একটা প্ল্যান হয়েছে। কিন্তু তাতে ঠিক কাজ হবে কি না আমরা জানি না। প্ল্যানটির মধ্যে কিছু অনিশ্চয়তা আছে নিঃসন্দেহে, কারণ আমরা এর আগে কোনো কৃত্রিম জীবনকে কখনও জৈব করে তোলবার চেষ্টা করিনি। কেবল তার উলটোটাই কয়েকবার মাত্র হয়েছে। তাই কতদূর…”
“কতদূর সফল হবে, তা-ই ভাবছেন? তা ফল যা-ই হোক, আমি কিন্তু একেবারে তৈরি। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে আপনারা যতটা সম্ভব চেষ্টা করবেন আমাকে ‘মানুষ’ করে দিতে। কিন্তু তা যদি সফল না হয়, তাহলেই-বা কী? আমার যা পরিণতি হবার, তা-ই হবে। এখন যা আছি, তার থেকে তো আর খারাপ কিছু হতে পারে না! আর অনিশ্চয়তা? সে তো থাকবেই। মানবজীবনের অনিশ্চয়তা বিধাতার বিধান! সরি… নাটের গুরুর বিধান…”
ম্যাডাম একটু মুচকি হেসে বললেন, “তাহলে তোমাকে কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে সবার আগে। আমাদের তাত্ত্বিকেরা অনেক বিবেচনা করে বলেছেন যে, জীবনের একেবারে প্রথম হৃৎস্পন্দন থেকে তোমাকে যাত্রা শুরু করতে হবে। তাই আমাদের ডাক্তারেরা তোমার মধ্যে যত কিছু কৃত্রিম—তোমার নাড়িভুঁড়ি, হাড়-মাংস সব কিছু বার করে, মানবশরীরের যা যা জৈবিক উপাদান প্রয়োজন, তা এই গ্রহ থেকেই সংগ্রহ করে তোমাকে একটি নবজাতক মানবকন্যারূপে পুনর্গঠন করবেন।”
“আচ্ছা, বেশ! তাহলে বলুন, আমাকে কী সিদ্ধান্ত নিতে হবে?”
“বলছি। তবে ব্যাপারটা আগে বোঝো ভালো করে। আমরা তোমার যা চেতনা, জ্ঞানবুদ্ধি, স্মৃতি, অভিজ্ঞতা—সব কিছুই সংরক্ষণ করে রাখব কয়েকটি অতি ক্ষুদ্র কোশের আধারের মধ্যে—ডাক্তারি পরীক্ষাতেও তা কোনোদিনই ধরা পড়বে না, মস্তিষ্কের অন্যান্য সাধারণ কোশ বলে মনে হবে। কিন্তু তোমার পূর্ব-অস্তিত্বের স্মৃতি বা চেতনার নাগাল তুমি একদিনে ফিরে পাবে না। প্রথম হৃৎস্পন্দন থেকে শুরু করে পূর্ণযুবতি হওয়া পর্যন্ত অতি ধীরে ধীরে, তোমার পূর্বচেতনা, তোমার নতুন অস্তিত্ব আর চেতনার সঙ্গে আস্তে আস্তে মিশে যাবে। তোমার শরীরে বিভিন্ন হরমোনের নিষ্ক্রমণ সেইভাবেই নিয়ন্ত্রণ করবার ব্যবস্থা করা হবে।”
“বাঃ, বেশ তো। আর?”
“আরও আছে। আমাদের তাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে, তোমাকে শুধুমাত্র একটা জৈব কোশের পুতুল করে বানিয়ে পৃথিবীতে ছেড়ে দিলেই তুমি হঠাৎ ‘মানুষ’ হয়ে যেতে পারবে না। এই ব্যাপারে আমাদের প্রযুক্তির যথেষ্ট ঘাটতি আছে। তাত্ত্বিকদের মতে, তোমার মধ্যে আরও কিছু উপাদানের প্রয়োজন হবে…”
“যেমন?”
“যেমন সময় বা কালের অনুকূলতা আর মানবচরিত্রের উপাদান। চরিত্রের উপাদান স্পর্শনাতীত। তাই আমরা সেগুলো তৈরি করতে পারি না। সেগুলো জন্ম থেকে, ক্রমান্বয়ে পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতা থেকে মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে ধীরে ধীরে নিবিষ্ট হয়। কিন্তু সেখানে অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যটাই সব চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, পবিত্রতা নয়। শুধুমাত্র মানবচরিত্রের প্রশংসনীয় দিকগুলি অনুভব করলে মানবচরিত্র গঠন কখনও সম্পূর্ণতা পায় না।”
“তাহলে উপায়?”
“উপায় একটা হতে পারে, যদিও তাত্ত্বিকেরা নিশ্চিত নন। তবুও অনেক ভেবেচিন্তে একটা পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা; আর বলেছেন, সেখানেই তোমার সিদ্ধান্তের প্রয়োজন।”
“বলুন।”
“সময়!” তোমাকে আমরা পৃথিবীর ইতিহাসের এমন একটা সময়ে এবং এমন একটা সমাজে প্রতিস্থাপন করতে চাই, যখন সেখানে আবেগের আতিশয্য অতি প্রকট—ভালো-খারাপ, সবরকম আবেগেরই! সেই অনুকূল-প্রতিকূল আবেগের মধ্যে বড়ো হবার সুযোগ পেলে তোমার চরিত্রগঠনের অনেক সুবিধে হবে। তুমি কোথায় এবং কোন সময় যেতে চাও—পৃথিবীর ইতিহাস ভরতি এই ধরনের সময় অনেক আছে—এই সময়কাল বহুবার, বহু দেশে এসেছে… কোন সমাজে তুমি…”
ম্যাডামকে বাধা দিয়ে অমর বলে উঠল, “যে-কোনো ‘সময়ে’? আপনারা কি সময়েরও অধিপতি? আমি জানি আপনারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে খুবই উন্নত, কিন্তু আপনারা সময়কেও বশ করেছেন বুঝি?”
ম্যাডাম হেসে বললেন, “না, তা ঠিক নয়। আমরাও পৃথিবীর মানুষের মতনই সময়ের শৃঙ্খলে বাঁধা। তবে আমাদের সময়বৃত্তের ব্যাসার্ধটা পৃথিবীর চেয়ে অনেকগুণে বড়ো। তাই আমরা পৃথিবীর সময়বৃত্তের বাইরে বাস করি, এবং অবাধে, যে সময়ে খুশি, পৃথিবীর সেই সময়ে পৌঁছে যেতে পারি।”
“বেশ। তাহলে আমাকে ভারতবর্ষে নিয়ে যান, ভারত বিভাগের সময়।”
“আচ্ছা? ভারতবর্ষে কেন? ট্রয়ের যুদ্ধের সময়, গ্রিস-পারস্যের যুদ্ধের সময়, কিংবা মঙ্গোলরা যখন সারা এশিয়া-ইউরোপ তছনছ করে দিচ্ছিল, তখন নয় কেন? তখনও তো চারদিকে আবেগের উথালপাতাল!”
“হ্যাঁ, বুঝলাম। কিন্তু আমার পছন্দের প্রধান কারণ, ভারতীয় সমাজের জ্ঞান অর্জন ও বিতরণের আদি পদ্ধতি।”
“আচ্ছা! শুধু জ্ঞান অর্জন-বিতরনের পদ্ধতি?”
“না, আরও আছে। আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদার আহ্বান শুনেছি—’এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান!’ আর তাঁর কাছ থেকেই আমি প্রথম শিখেছি মৃত্যুকে প্রেমিক হিসেবে গ্রহণ করতে—’মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যামসমান’!”
“হ্যাঁ, টেগোরের কথা আমরাও জানি। তিনি যথার্থই বিশ্বকবি। ঠিক আছে, ভারত বিভাগের প্রাক্কালে, যে প্রচণ্ড দাঙ্গাটি বিভাজনের পাল্লাটাকে এক দমকাতেই একপাশে হেলিয়ে দিয়েছিল, সেই দাঙ্গা শুরুর সময়েই তোমাকে ওই সমাজে নিয়ে গিয়ে প্রতিস্থাপন করা হবে। যখনই, যে-কোনো প্রাণী তোমাকে স্পর্শ করবে, তখনই তোমার হৃৎস্পন্দন শুরু হয়ে যাবে। তোমার নাটের গুরুর কাছে প্রার্থনা করো যেন সেই প্রাণীটা মানুষ হয়। কুকুর যদি হয়, তাহলে কিন্তু কুকুরের জীবন যাপন করবে তুমি। মানুষ হলে প্রার্থনা করো যে, সে মানুষটি যেন একটি সৎ ও দয়ালু মানুষ হন, কারণ সেই মানুষের ব্যক্তিত্বও তোমার ওপরে বর্তাবে। আরও প্রার্থনা করো যে, তুমি যেন যথার্থ একজন পালকের আশ্রয় পাও। মানবশিশুরা জন্মায় বড়ো অসহায় হয়ে। তখন তাদের মাতা-পিতা স্থানীয় কারও আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়। আশা করা যায় যে, কেউ না কেউ তোমার জীবনে সেই ভূমিকাটি পালন করতে এগিয়ে আসবেন। তা না হলে আমাদের পুরো প্রয়াসটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। তখন তোমার যে কী পরিণতি হতে পারে, তা আমরা বলতে পারব না। অতএব দেখতেই পাচ্ছ, ব্যাপারটিতে অনেক ঝুঁকি আর অনিশ্চয়তা আছে। তুমি কি তাও রাজি?”
“রাজি।”
নবজাতক
নবীন আগন্তুক,
নব যুগ তব যাত্রার পথে
চেয়ে আছে উৎসুক।
কী বার্তা নিয়ে মর্ত্যে এসেছ তুমি;
জীবনরঙ্গভূমি
তোমার লাগিয়া পাতিয়াছে কী আসন।
তরুণ বীরের তূণে
কোন মহাস্ত্র বেঁধেছ কটির ‘পরে
অমঙ্গলের সাথে সংগ্রাম-তরে।
রক্তপ্লাবনে পঙ্কিল পথে
বিদ্বেষে বিচ্ছেদে
হয়তো রচিবে মিলনতীর্থ
শান্তির বাঁধ বেঁধে। (‘নবজাতক’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
অবিভক্ত বাংলার হিন্দু-সংখালঘু নোয়াখালি জেলার লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে, দালালবাজারের প্রান্তে, কিশোরপুর বলে ছোট্ট একটি গ্রাম। এলাকার আদি রাজা শ্রীগৌরকিশোর রায়ের নামেই গ্রামটির নামকরণ। কিশোরপুর ছেড়ে একটি বাঁশঝাড়ের মধ্যে দিয়ে কয়েক পা এগোলেই চোখে পড়বে রায়েদের বিশাল বড়ো জমিদারবাড়ি। সেই প্রাসাদের পাশেই রায় পরিবারের কাটানো ২২ একরের একটি বিশাল পুকুর, ‘সাগরদিঘি’। পারিবারিক হলেও, তৎকালীন জমিদার নলিনীকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় বহুদিনই সেটি এলাকার প্রজাদের ব্যবহারের জন্য, বেড়া তুলে উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন।
সেদিন অক্টোবর মাসের ১৭ তারিখ, খ্রিস্টাব্দ ১৯৪৬। কাকভোরে উঠে সাগরদিঘির দিকেই এগোচ্ছিলেন শাকিব মিয়াঁ। সেই ভয়াবহ কোজাগরি লক্ষ্মীপূর্ণিমার পরে পুরো সাত দিন কেটে গেলেও, ভোর আকাশে চন্দ্রদেব তখনও বলিষ্ঠ। গত ক-দিনের দাঙ্গা, খুন, ধর্ষণ আর রক্তের প্লাবন দেখে দেখে শাকিব খুবই ক্লান্ত। ভেবেছিলেন, আজকে ভোরের দিঘির জলে ভালো করে গোসল করতে পারলে হয়তো-বা সেই দুঃস্বপ্নের স্মৃতিগুলো কিছুটা ফিকে হবে। মানুষ কী করে এতটা নৃশংস হতে পারে!
কিন্তু দিঘি পর্যন্ত আর পৌঁছোনো হল না। পুরো পথটা ধরেই মানুষের লাশ চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ছিল। তারই মধ্যে দিয়ে সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগোচ্ছিলেন শাকিব। কিন্তু বাঁশঝাড়টা শুরু হবার ঠিক আগেই, বট গাছটার তলাটায়, হঠাৎ তাঁর পা গিয়ে ঠেকল কী যেন একটা পুঁটলিতে—রক্তাক্ত এক পুঁটলি! ভোরের আধা-অন্ধকারে ঠিকমতন ঠাহর করা না গেলেও, শাকিবের মনে হল, পুঁটলিটি যেন নড়ছে। তিনি তাড়াতাড়ি মাথা নীচু করে দেখতে গিয়ে শুনতে পেলেন একটি ক্ষীণ আর্তনাদ—একটি নবজাতকের কান্না।
***
অনেকবার ধাক্কা দিয়ে আর কড়া নেড়েও, দরজাটা কেউ খুলল না ভেতর থেকে। শাকিব বুঝলেন যে, কোনো হিন্দু-বাড়িই এখন আর যে-কেউ কড়া নাড়লে দরজা খুলবে না। কিন্তু শাকিব তো… যা-ই হোক, তিনি গলা উঁচু করে ডাক দিলেন, “ঠাকুরমশাই, ঠাকুরমশাই, ভয়ের কিসু নাই। আমি শাকিব। দরজা খুলেন!”
কিছুক্ষণ পরে ঘুম-চোখে উঠে দরজাটা খুলতে খুলতে হরিহর ভটচায বলে উঠলেন, “ক্যাডা, শাকিব? আয় ব্যাডা। এত ভোররাতে কী মনে কইর্যা? তোর হাতে ইতা কী—খাবার তো কাল যেগুলা মুখুজ্জে গিন্নি রাইখ্যা গেসলো, সেগুলা… ওইহানে দেখ… কেউ তো হাতটাও দে নাই। ভিতরে ঢুইক্যা আয়, দরজাটা আবার লাগাইয়্যা দে… আরে! তর হাতে কি কার ছাওল? কানতাসে তো! কী হইসে?”
খুব সাবধানে বাচ্চাটিকে দালানের ওপর শোয়াতে শোয়াতে শাকিব জিজ্ঞেস করলেন, “মা ঠাকরুন অ্যাহন কেমন? একটু সামলায়ে উঠছেন তো?”
“না, কোথায় আর। সে তো গিয়া সেই যে মাটির অপরে হুইয়া রইল সেদিন, আর তো অঠে নাই। নাওয়া নাই, খাওয়া নাই, কত কইসি, ‘কী আর করবা! আমাগো ভাগ্যে যা ছিল, তা-ই হইসে। যারা গ্যাসে, তারা তো গ্যাসেই, আর তো হিরর্যা আইবে না! কিন্তু আরা দুজনা তো এনও বাঁইচ্চা আচি, তুমি উইঠ্যা একটু না সামলাইলে আমাগো কী হইব?’”
১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসের ১০ তারিখ ছিল কোজাগরি লক্ষ্মীপূর্ণিমা। সেদিন গভীর রাতে যে শুধু হরিহরের বাড়িতেই হামলা হয়েছিল, তা নয়। পুরো নোয়াখালি অঞ্চলে জুড়েই, সেই রাত থেকে শুরু করে ১৪ তারিখ অবধি, পুরো চার দিন ধরে নির্বিরোধে সমস্ত হিন্দু-পরিবারের ওপরে চলেছিল এক পাশবিক তাণ্ডবলীলা। হয়তো-বা তার কয়েক মাস আগে, সম্ভবত কলকাতাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করবার পরিকল্পনায়, অনুমিতভাবে ভারত-বিভাজনপন্থী নেতা শ্রীসুরাবর্দির নির্দেশে সেখানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে দাঙ্গাটি বাধানো হয়, এবং যে দাঙ্গায় ব্যাপকভাবে অনেক নির্দোষ মুসলমানকে হত্যা করা হয়, তার প্রতিশোধ নেওয়াটাই ছিল নোয়াখালির এই হামলার প্রধান কারণ। কিন্তু সেই ঘৃণা-পরম্পরার শুরু যে কোথায়, তা কি কেউ বলতে পারে? কিন্তু শুরু যেভাবেই হোক, জাতীয় স্তরের পত্রিকা ‘যুগান্তর’-এর ১৮ অক্টোবর, ১৯৪৬-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্থানীয় নেতাযুগল, গোলাম সারোয়ার ও তাঁর ব্যক্তিগত গুন্ডার দল ‘মিয়াঁর ফৌজ’ এবং কাসেম মোল্লা ও তাঁর ‘কাসেমের ফৌজ’—সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা করে, নির্বিরোধে হত্যা করে ফেলেছিল ওই অঞ্চলের প্রায় পাঁচ হাজার হিন্দুকে এবং পঞ্চাশ হাজার হিন্দু জাঁতাকলে আটকে পড়ে গিয়েছিলেন কোনোদিকে পালাবার রাস্তা না পেয়ে। ফলত, এই চার দিন ধরে কুড়ুলের সামনে বসিয়ে, জোর করে গোমাংস খাইয়ে ধর্মান্তরকরণ, হত্যা, এবং শিশু, যুবতি বা প্রৌঢ়া নির্বিশেষে গণধর্ষণ, এবং হিন্দু-পাড়ায় বাড়িতে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে, পরিবারের পর পরিবারকে চরমভাবে হত্যা ও গৃহচ্যুত করে দেওয়া—এসবই সইতে হয়েছে নোয়াখালির মানুষদের।
ভারত বিভাজনের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে, নোয়াখালির দাঙ্গাটি একটি দিক্নির্ণায়ক ঘটনা। নোয়াখালির ঘটনার আগে পর্যন্ত, হিন্দু-মুসলমান দু-পক্ষেরই যাঁরা মধ্যপন্থী ছিলেন, তাঁরা আশা করেছিলেন যে, গত বারোশ-তেরোশো বছর একসঙ্গে মোটামুটি সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করবার পরে, সাম্প্রতিক রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সম্প্রদায় দুটি আবার আগের মতনই শান্তিপূর্ণভাবে একসঙ্গে বাস করতে পারবে, এবং ভারত বিভাজনকে রুদ্ধ করা যাবে। কিন্তু নোয়াখালির দাঙ্গার ঘৃণ্য নৃশংসতার পরে দু-পক্ষই স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয় যে সহাবস্থান, অন্তত আপাতত, একেবারে অসম্ভব।
দাঙ্গাটির সূত্রপাত হয় সম্ভবত এলাকার জমিদার নলিনীকিশোর রায়চৌধুরীর বাসভবনে, ১০ তারিখেই। ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে, প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে সব কিছু ছেড়েছুড়ে একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হন জমিদারবাবু। পরের দিন, অক্টোবর মাসের ১১ তারিখে, ‘মিয়াঁর ফৌজ’ আক্রমণ করে স্থানীয় হিন্দু-নেতা রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরীর বাড়িটি। তিনি ছিলেন নোয়াখালি আইনজীবী সংস্থার এবং সেখানকার হিন্দু মহাসভার অধ্যক্ষ। তিনি একা হাতে রাইফেল নিয়ে সারাদিন ছাদ থেকে তাঁর বাড়িটিকে রক্ষা করেন এবং রাতের বেলায় তাঁর পরিবারের সকলকে নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হন। কিন্তু পরের দিন, ১২ তারিখে, মিয়াঁর ফৌজ আরও বেশি সংখ্যায় দুর্বৃত্ত আনিয়ে, আবার আক্রমণ চালায়। সেদিন আর রাজেন্দ্রলালবাবু পেরে ওঠেননি। শোনা যায় যে, তাঁর কাটা মাথাটা একেবারে মোগল সংস্কৃতির ধাঁচে, একটি থালায় করে গোলাম সারোয়ারকে উপহার দেওয়া হয়।
১০ তারিখে হরিহরবাবুর বাড়ি থেকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর একমাত্র পুত্র বৈকুণ্ঠকে। তাঁর অপরাধ? তিনি তাঁর স্ত্রী মালতী আর ১২ বছরের কনিষ্ঠা বোন রাধাকে গণধর্ষণের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়েছিলেন। বৈকুণ্ঠ আর হরিহরের হাত-পা বাঁধা হয়ে গেলে, তাঁদের সামনেই, একের পর এক বারংবার ধর্ষণ করা হয় মালতী, রাধা আর প্রীতিবালাকে। এমনকি বন্দুকের ডগা ব্যবহার করতেও দ্বিধা করেনি পশুগুলো। হরিহরের তিন বছর বয়সের একমাত্র নাতি নগেন্দ্রর গলা কেটে, তাকে উঠোনেই ছুড়ে ফেলে দেয় তারা। শেষ পর্যন্ত বাড়ির যাবতীয় টাকাপয়সা লুঠ করে, বৈকুণ্ঠসহ মালতী আর রাধাকে চুল ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলে যায় দুষ্কৃতীরা। এরপরে ১৪ তারিখ সন্ধেবেলা, বাড়ির পাশের বট গাছে ঝুলতে দেখা যায় ওই তিনজনের ছিন্নভিন্ন তিনটি মৃতদেহ। গ্রামে তখন সৎকার করবার জন্যও আর বেশি সমর্থ হিন্দু বাকি ছিল না। তাই শাকিবই গ্রামের কিছু সজ্জন মুসলমান প্রতিবেশীকে ডেকে ব্যবস্থা করেছিলেন সৎকারের। সেই থেকেই শোকে মৃতপ্রায় ভটচায-বাড়ির নিজের লোক হয়ে যান শাকিব মিয়াঁ।
“এই মাইয়াটারে দ্যাহেন—কী হুডহুডে দ্যাখতাসেন? দিঘিতে গোসল করতে যাইতাসিলাম, আপনাগো বট গাছের ধারে দেখি, বেটি পুঁটলি থিক্যা হাত-পা বাইর কইর্যা ছুইড়্যা ছুইড়্যা কানত্যাসে। দেইখ্যা মনে অইল, হিন্দুর মেয়েই হইব—দ্যাখেন, কেমন সুন্দর টিপ আর কাজল পরাইসে… মনে হয়, সদ্যই জন্মাইসে!”
“হিন্দুর মাইয়া হইতে পারে, কিন্তু আমার কাছে আনলি ক্যান? আই কী করমু?”
“অত তো ভাবি নাই, ঠাকুরমশাই, হিন্দু দেইখ্যাই আপনার বাড়ি লইয়া আইসি, যদি আশ্রয় দেন!”
“আশ্রয় দিব? ওটারে দেখবে ক্যাডা? তর মা ঠাকরুন তো মরার লগে… সেই যে বিছানায় পড়সে পরশু দিন, তারপর থিক্যা কত ডাকছি—সাড়াই দেয় না সে। আর সাড়া দিবেই-বা কীসের লগে—বাড়ি তো শূন্য! এইবার দুইজনে মরলেই হয়!”
“আহা-হা, সাতসকালে এইসব কথা কন ক্যানে?”
“হঃ, কইব না তো করুম কী? হয় দুইজনে মিল্যা গলায় দড়ি দিয়া মরি, নয়তো জমিদারবাবুদের মতন কলকাতাতেই চইল্যা যাই ভিটা ছাইড়্যা। আমরা গেলে তুই আমাদের জমিটা দখল কইর্যা নিবি কিন্তু, কইয়্যা যাইত্যাসি…”
“বাপ-দাদার ভিটা ছাইড়্যা কোথায় যাইবেন ঠাকুরমশায়? কলকাতার বাবুরা তো সব কেমন কেমন! সেইখানে গিয়া কী হইব?”
“আচ্ছা, কী হইতাসেটা কী, শুনি? বলি আক্কেল নাই? কচি বাচ্চাটা কাইন্দা কাইন্দাই মইর্যা যাবে, তবু মরদদের হুঁশ হইব না।” হঠাৎ পিছন থেকে প্রীতিবালার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙল দুজনের: “গাইয়ের থিক্যা একটু দুধ দুইয়্যা আনসি। শাকিব মিয়াঁ, একটু কাঠখড় খুঁইজ্যা আইন্যা দাও তো বাপু, দুধটারে একটু জ্বাল দেই।”
“আইজ্ঞা, মা ঠাকরুন, এখনই আনতাসি।”
স্বপ্নের দেশে
মরমের যত তৃষ্ণা আছে—
তারি খোঁজে ছায়া আর স্বপনের কাছে
তোমরা চলিয়া এসো—
তোমরা চলিয়া এসো সব!
ভুলে যাও পৃথিবীর ওই ব্যথা—ব্যাঘাত—বাস্তব!
সকল সময়
স্বপ্ন—শুধু স্বপ্ন জন্ম লয় (‘স্বপ্নের হাতে’, জীবনানন্দ দাশ)
শুক্রবার, ১৫ নভেম্বর, ১৯৪৬ সাল। সাদা-কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে, ঝিকঝিক করে ধুঁকতে ধুঁকতে এসে কলকাতার শিয়ালদহ, ওরফে ‘শেয়ালদা’ স্টেশনের পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে থামল ‘ঢাকা মেল’। এই দিনের মতো তার কাজ শেষ। কামরা ভরতি করে করে দুঃস্বপ্নের নরক থেকে তুলে, অনেকগুলি নতুন জীবনের প্রত্যাশাকে সে বয়ে এনেছে এই ‘স্বপ্নের শহর’ কলকাতায়।
সেই ট্রেনে, শত শত নিপীড়িত মানুষের মধ্যে সপরিবারে রয়েছেন হরিহর ভট্টাচার্য। পরিবার বলতে তিনি ও তাঁর স্ত্রী প্রীতিবালা। আর একটি নবজাতক, যাকে প্রীতিবালা সচরাচর কোলছাড়া করেন না। সঙ্গে কয়েকটি পুঁটলি। তাদের মধ্যে কিছু হাঁড়িকুড়ি, কয়েকটি পিতলের থালা, ডজনখানেক বাটি ও গেলাস। একটি পুঁটলির মধ্যে কিছু যাত্রার রসদ—একটু চিঁড়ে, একটু মুড়ি; কিছু সেদ্ধ চাল আর খানিকটা মশুর ডাল; একটু শুকনো নারকেল, আর এক শিশি সরষের তেল। বাকি পুঁটলিগুলোতে কয়েকটা ধুতি, ফতুয়া, চাদর হরিহরের; কিছু শেমিজ ব্লাউজ় আর আটপৌরে শাড়ি প্রীতিবালার। দু-চারটে কাঁথা, কম্বল, বালিশ ও চাদর দিয়ে একটা হোল্ডঅল মতন তৈরি করা হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে সযত্নে মুড়িয়ে রাখা আছে মা লক্ষ্মীর একটি বাঁধানো ছবি, কিছু পারিবারিক পুথি, কুলদেবতা কশ্যপ মুনির প্রায় পাঁচশো বছরের পুরোনো একটি ছোটো পোড়ামাটির মূর্তি; পুজোর আসন দুটি; আর সামান্য কিছু পুজোর সামগ্রী। তুলে তুলে পরবার মতন প্রীতিবালার দু-তিনটে ভালো লাল-পাড় শাড়ি, শেমিজ আর ব্লাউজ়ও হোল্ডঅলের মধ্যে ভাঁজ করা আছে। নবজাতকের জন্য আলাদা একটা পুঁটলি। তাতে তার কাঁথা-বালিশ-চাদর ও ঝিনুক-বাটি—যা কিছুদিন আগেই শেষবার ব্যবহার করেছিল হরিহরের ছোট্ট নাতি নগেন্দ্র। আর নগেন্দ্রর কিছু পুরোনো জামা। হরিহরের ধুতির খুঁটে কষে বাঁধা আছে তাঁর বাপ-দাদার ভিটের একমুঠো মাটি।
না। হরিহরের কোনোদিনই কোনো স্বপ্ন ছিল না কলকাতা চলে যাবার। রাজা বল্লাল সেনের সময় থেকে তাঁদের বংশানুক্রমিক বাস নোয়াখালির ওই লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে। যজমানদের ঘরে পুজোআচ্ছা করেই প্রধানত জীবিকা নির্বাহ করতেন তাঁদের বংশের পুরুষেরা। সেই সঙ্গে সামান্য কিছু আয়ও ছিল দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে। হরিহর কখনও ভুলেও কল্পনা করতে পারেননি যে, তাঁদের কোনোদিন ওই ভিটে ছেড়ে নিঃস্ব হয়ে, হঠাৎ একবস্ত্রে অজানা দূর দেশে চলে যেতে হবে চিরদিনের জন্য। কিন্তু দাঙ্গার হিংস্রতা ও আকস্মিকতার জন্য কে-ই-বা প্রস্তুত থাকতে পারে কখনও!
ওই দুর্দিনে, শাকিব মিয়াঁ এবং আরও দু-একজন প্রতিবেশী, যেমন এনামুল খান বা মেহেদি হোসেন ও তাঁদের পরিবারেরাই ছিলেন হরিহরদের ভরসা। নৃশংস হত্যাকাণ্ডটির মতন একটি দুঃসময়ে যদি তাঁরা পাশে এসে না দাঁড়াতেন, তাহলে হরিহরবাবুরা যে কোথায় ভেসে যেতেন, তা কল্পনাতীত। প্রীতিবালা তো বেঁচে থাকতেই চাইছিলেন না আর। তবু কুড়ানিকে কোলে পেয়ে শেষ পর্যন্ত একটুখানি চিকিৎসা করাতে রাজি হয়েছিলেন তিনি। শাকিব মিয়াঁর স্ত্রী রোকেয়া তাঁকে সঙ্গে করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন তাঁর ক্ষতের চিকিৎসা করাতে। সে সময়ে স্থানীয় হিন্দু মহাসভার প্রখ্যাত ডাক্তার ও সমাজসেবক, মেজর প্রভাতকুমার বর্ধন, লক্ষ্মীপুরে ত্রাণকার্যের সুবিধার জন্য দাঙ্গা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একটি রিলিফ ক্যাম্প ও ২৫টি শয্যার একটি হাসপাতাল নির্মান করে ফেলেছিলেন। প্রীতিবালার চিকিৎসা করানো হয়েছিল সেইখানেই। কিন্তু দয়ালু প্রতিবেশী ও পরিচিত লোকেদের কথা বাদ দিলে, তখনকার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা কোনো হিন্দুর জন্যই আর ভালো ছিল না নোয়াখালিতে। ক্রমেই বোঝা যাচ্ছিল যে বাংলার এই অঞ্চল আর হিন্দুদের জন্য নিরাপদ নয়।
প্রস্তাবটা শেষ পর্যন্ত শাকিব মিয়াঁই দিলেন। তাঁর সাধ্যমতো কিছু নগদ টাকা হরিহরের হাতে তুলে দিয়ে তিনি বললেন, “দূর দেশে যাইতাসেন তো। হাতে কিছু নগদ টাকা থাকলে ভালোই অইব। আপনাগো ঘর তো রইলই, কলকাতা গিয়া ব্যাপারস্যাপার একটু দেইখ্যা আসেন। ততদিনে তো দ্যাশে শান্তি আইস্যা যাইব। তহন আবার ফিইর্যা আসেন, আপনাগো ভিটাজমি ততদিন আমার জিম্মায় রইল গিয়া।” বেশি নগদ টাকা অবশ্য যাত্রাপথে নিরাপদ নয়। তাই লক্ষ্মীপুর থেকে ঢাকা যাবার গোরুর গাড়ির, আর ঢাকা থেকে কলকাতা যাবার ট্রেনগাড়ির ভাড়া গুনে, বাকি টাকার বেশিটা দিয়েই প্রীতিবালার জন্য হাতের কয়েক গোছা নতুন সোনার চুড়ি গড়ানো হল, আর কুড়ানির হাত দুটির জন্য দুটি বালা। গ্রামটা ছাড়বার আগে জমিবাড়িগুলো শাকিবের নামে লিখে দিলেন হরিহর।
শেকলে তালা পড়বার আগে প্রীতিবালা গেলেন উবু হয়ে বসে শেষবারের মতন সদর দরজার চৌকাঠে একটু মাথাটা ঠেকিয়ে আসতে। কিন্তু তিনি এত সময় নিচ্ছিলেন যে, গাড়োয়ান পর্যন্ত অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, “বেলা থাকতে থাকতে গাড়ি ছাড়ুম, আসেন, আসেন, মা ঠাকরুন!” হরিহরও একবার ডাক দিলেন। শেষ পর্যন্ত অশ্রু সংবরণ করতে করতে এসে, প্রীতিবালা কুড়ানিকে কোলে তুলে, লম্বা একটা ঘোমটা টেনে গাড়িতে উঠে বসলেন। বসলেন একেবারে ভিটের উলটোদিকে মুখ করে। আর একবারের জন্যও ফিরে তাকালেন না ভিটাটার দিকে। হরিহর এগিয়ে গেলেন তালা লাগানোর কাজটা সম্পন্ন করে ফেলতে। কিন্তু তিনিও বেশ কিছুক্ষণ দরজাটার ওপরে হাত বোলাতে বোলাতে কিছু যেন কথা বললেন কাউকে। তাঁর চলাফেরা দেখে বেশ শান্তই লাগছিল তাঁকে, পরিস্থিতি অনুপাতে। কিন্তু সবশেষে যখন দরজায় তালাটা লাগিয়ে চাবির তোড়াটা শাকিব মিয়াঁর হাতে ফেরত দিতে গেলেন, তখন তাঁর হাতটা এতই কাঁপছিল যে, সেখান থেকে রীতিমতো ঝনঝন করে শব্দ হচ্ছিল।
গ্রামের সীমানা শেষ হবার আগেই প্রীতিবালা তাঁর অশ্রুজল সংবরণ করে ফেলেছিলেন, যদিও তখনও তাঁর গলাটা বেশ ভারী ছিল। তার মধ্যে দিয়েই জিজ্ঞেস করলেন, “দরজার পারে কার লগে কথা কইতাসিলা গো? কানে আইতাসিল!” হরিহর বললেন, “ও কেউ নয়! নগেন! আমি নগেনরে কইতাসিলাম যে, স্কটল্যান্ডের সায়েবদের একটি প্রথা আসে। তাহাদের কবরস্থানে যে লাশ সব চেয়ে নূতন আসে, তারই কত্তব্ব হয় কবরস্থানের দেখভাল করবার। তখন আগের লাশের ছুটি হইয়্যা যায়। কিন্তু আমাগো তো আর কবর হয় না। তাই তার আত্মার উদ্দেশেই কইলাম, ‘তুইই তো প্রেতলোকে এখন আমাগো বংশের সব চেয়ে তরুণ। মুক্তি পাইয়া আনন্দে ঘুইর্যা বেড়াইতেসস। তুমি নজর রাখবা আমাগো বাপ-দাদার ভিটার অপর।’”
***
‘স্বপ্নের না-শহর’ কলকাতার শেয়ালদা স্টেশনের পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেনটা এসে থামতেই কিন্তু, হরিহরের হাত-পা যেন তাঁর পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। অথচ যাত্রার এই ক-দিন ধরে তো তিনিই সাহস দিচ্ছিলেন প্রীতিবালাকে, “কিস্সু চিন্তা কইর্যো না প্রীতি। কলকাতায় পৌঁছাইয়াই সব ঠিক হইয়া যাইব, দেখবা। ওইহানে তো নিরাপত্তা পাইবা সবচে’ আগে। তারপরে দেখবা, আমাগো লগে থাকন-খাওনের ব্যবস্থা থাকবে ভালো, যতদিন না নোয়াখালিতে আবার শান্তি ফিইর্যা আসে। তোমাগো ডাক্তারই তো কইল তা-ই—ওই যে মেজর বর্ধন! উনি তো গিসলেন গান্ধিজির সঙ্গে দেখা করতে। গান্ধি তো কইসেন উনারে, এই ঝড়ঝাপটা ঠিক সামলাইয়া যাইব। অ্যাহন কিছুদিন গা-ঢাক্কা দিয়া কলকাতা ঘুইর্যা আইলেই দেখবা পরিস্থিতিটা বদলাইয়ে গ্যাসে।
“ও, হ্যাঁ, আর যদি কলকাতাটারে ভালো লাইগ্যাই যায়, তবে তো উইহানেই একটা জমি কিইন্যা থাইক্যা যাইব। ভিটার মাটি আনসি, দ্যাখো নাই? ওইটারে ছড়াইয়া দিমু নূতন বাড়ির উঠানে।”
প্রীতিবালা অবশ্য হরিহরের সব কথা বিশ্বাস করতে পারেননি। প্রথম কথা, নোয়াখালি ফেরবার রাস্তা যে খোলা, তা তিনি বিশ্বাস করেননি। ওই নির্মম হত্যা, ধর্ষণ আর লুঠপাটের পরে সেই রাস্তা চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলেই তিনি বিবেচনা করেছিলেন। আর হরিহরও যদি নিজের মন থেকে সে কথা না জানতেন, তাহলে তিনি কখনোই তাঁর দশ-পনেরো পুরুষের ভিটাটা শাকিব মিয়াঁকে বিক্রি করে আসতেন না। কাজেই প্রীতিবালা জানতেন যে, হরিহর তাঁকে শুধু উৎসাহই দিতে চাইছেন।
শেয়ালদা স্টেশনের কাছাকাছি এসে ঢাকা মেলটা আস্তে হওয়া শুরু করতেই, পুরো ট্রেনের মধ্যে থেকে একটা চাপা গুঞ্জন উঠল। অচেনা শহর, অজানা মানুষ, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ—সব শরণার্থীর মনেই এক চিন্তা। ট্রেনটা থেমে যেতেই শুরু হয়ে গেল হুড়োহুড়ি। সবাই যে যার বাক্সো-প্যাঁটরা-পুঁটলি নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দু-চারটে লালা জামা-পরা বিহারি কুলি এসে হেঁকে গেল, ‘কুলিইই, চাই কুলি?’ হরিহরেদের কামরায় অবশ্য বেশির ভাগই গরিব লোক। তাই কুলিদের তেমন কেউ আমল দিল না। তারা নিজেরাই নিজেদের মালপত্র সামলে প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল।
প্রায় সবাই নেমে গেলেও যখন হরিহর প্ল্যাটফর্মে নামবার কোনো তোড়জোড় করলেন না, তখন প্রীতিবালা তাঁর স্বামীর কালো-হয়ে-যাওয়া মুখটার দিকে তাকিয়েই এক মুহূর্তে তাঁর মনের অবস্থাটা বুঝতে পেরে গেলেন। মানুষটা জীবনে কোনোদিন তাঁর গ্রামের চত্বর ছেড়ে কোথাও বেরোননি। বংশপরম্পরায় পেয়েছিলেন সাবেক দিনের বাড়ি-ঘর-জমি। জীবনটা বেশ সহজ ছন্দেই চলছিল তাঁর। কিন্তু কুড়ুলের এক কোপে মাটি থেকে উৎখাত-হয়ে-যাওয়া লতার মতন, তিনিও হঠাৎ সমূলে উচ্ছেদিত হয়ে গেলেন কেবলমাত্র একরাত্রের—একটিমাত্র রাত্রের—কয়েকটি মুষ্টিমেয় দুর্বৃত্তের অবর্ণনীয় পাশবিক অত্যাচারে। নৃশংসভাবে হারালেন তাঁর চোখে-হারানো পুত্র, কন্যা, নাতি আর পুত্রবধূদের! তার ওপরে আবার তাদের জন্য ভালো করে শোক করবারও অবকাশ পেলেন না একটুও। বাধ্য হলেন ভিটেমাটি ছেড়ে প্রায় নিঃস্ব হয়ে, একেবারে অজানা একটি দেশের উদ্দেশে পাড়ি দিতে। তবুও তো যাত্রার এই ক-দিন তিনি মুখে বেশ সাহসই দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু ট্রেনটা আজ যাত্রার শেষ স্টেশনে এসে থামতেই, কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন হরিহর।
প্রীতিবালা বুঝলেন যে ট্রেনটা থেমে যাওয়া মানেই তাঁদের পুরোনো জীবনটা ফুরিয়ে যাওয়া। ট্রেনটা যতক্ষণ সামনের দিকে চলছিল, ততক্ষণ যেন তাঁরা ‘আজ’ বেয়ে বেয়ে ‘আগামীকাল’-এর দিকে এগোচ্ছিলেন। কিন্তু জীবনে ‘আজ’টাকে যতই টেনে টেনে রবার ব্যান্ডের মতন লম্বা করবার চেষ্টা করা হোক-না কেন, প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে সেটা একসময় নিঃশেষ হয়ে যায়, আর ‘আগামীকাল’টা হুড়মুড়িয়ে ঘাড়ের ওপরে এসে পড়ে। হরিহরের মনের কষ্টটা বুঝতে পেরে, প্রীতিবালার মনটা মমতায় ভরে গেল। তিনি হরিহরের পিঠে সস্নেহে একটু হাত বুলিয়ে বললেন, “চলো। এইবারে নাইম্যা যাই। তুমি কুড়ানিটাকে ধইর্যা একটু প্ল্যাটফর্মে গিয়া দাঁড়াও, আমি পোঁটলাপুঁটলিগুলিরে নামাই।”
প্রীতিবালা মালপত্র সব নামিয়ে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ালেন। একটু পরেই খালি-হয়ে-যাওয়া ঢাকা মেলটা, হঠাৎ ঘটাং ঘটাং শব্দ করে পেছু হটে, সেদিন রাত্রের মতো তার নির্দিষ্ট গুদামঘরের দিকে যেতে যেতে, একসময়ে পুরোপুরি দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রীতিবালার চোখটা হঠাৎ জলে ভরে গেল। সাত পুরুষের ভিটেমাটির সঙ্গে তাঁর শেষ সূত্রটাও তবে এবারে ছিন্ন! যতক্ষণ ট্রেনটা শারিরীকভাবে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল, ততক্ষণ যেন তাঁর মনের কোনো এক অবুঝ কোণে, কেমন একটা অযৌক্তিক ভরসাও ছিল—যেন সেরকম কোনো প্রয়োজন পড়লে, ওই ট্রেনটাতে চাপলেই বুঝি তিনি আবার তাঁর নিজের দেশে, অর্থাৎ তাঁর পুরোনো শান্তিপূর্ণ জীবনে, হুস করে ফিরে যেতে পারবেন। কিন্তু এখন সেই অলীক ভরসাটুকুও পুরোপুরি চলে গেল। মনের মধ্যে একরাশ আবেগি অভিমান-অভিযোগের একটা অনুভূতি উথলে উঠল তাঁর, ওই অপস্রিয়মাণ ট্রেনটির দিকে তাকাতে তাকাতে। জুলিয়াস সিজ়ারের মতনই যেন আর্তনাদ করে ট্রেনটাকে বলে উঠতে চাইলেন তিনি, “দাও টুউউ, ব্রুটাস!” কিন্তু আবেগের সময় আর নেই। বাস্তবিক, তিনি এখন দাঁড়িয়ে আছেন অজানা একটি শহরের অচেনা একটি প্ল্যাটফর্মের ওপরে; সঙ্গে একটি অসহায় শিশু, একটি ভগ্নোদ্যম পুরুষ, আর কয়েকটি পুঁটলি ভরতি শুধু কিছু স্মৃতি। পিছনে সদ্য খালি-হয়ে-যাওয়া প্ল্যাটফর্মের খাদ। সেই খাদের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়েছে দুটি অন্তহীন ট্রেন লাইন—কত স্বপ্নের, কত জগতের দিকেই-না নিয়ে যেতে পারে তারা! কিন্তু তাদের কর দেবার মতন জীবন-শুল্ক এখন আর বাকি কই? এখন তিনি পুরোপুরিই পূর্ববাংলা থেকে আসা একজন ‘ছিন্নমূল হিন্দু-শরণার্থী’—অসহায়ভাবে কলকাতার করুণাপ্রার্থী।
নিজেকে সামলে নিতে বেশি সময় লাগল না প্রীতিবালার। এবারে শরণার্থীর চোখ নিয়ে চারদিকে ভালো করে চেয়ে দেখলেন। লক্ষ্মীপুর-কিশোরপুরের মতন সেই সজল-সরস-সবুজ কোথাও দৃষ্টিতে ধরা পড়ল না। আশপাশে নেই কোনো বট গাছ, বাঁশ গাছ, বা বাইশ একর দিঘির ধারের নারকেল গাছগুলো। চারদিক সিমেন্টে বাঁধানো। মেঝে অপরিষ্কার। শুধু ধুলোই নয়, এদিকে-ওদিকে কলা আর চিনেবাদামের খোসা ছড়ানো। তার সঙ্গে পুরোনো ঠোঙা, শালপাতা, আর আরও কত কিছু জঞ্জালই-না পড়ে আছে চারদিকে! লাল ইটের দেওয়ালগুলো নিষ্প্রাণভাবে স্টেশনের পরিধিগুলোকে পাহারা দিচ্ছে। তার বাইরে, দূরে রাস্তা থেকে শোনা যাচ্ছে হাজার লোকের ব্যস্তসমস্ত হট্টগোল, ট্রাম-বাসের ঘণ্টা, ট্যাক্সি-গাড়ির কানফাটানো হর্নের আওয়াজ, আর কিছু ঘোড়ার গাড়ি থেকে কংক্রিটের ওপরে ঘোড়ার খুর ঠোকবার শব্দ। দৃষ্টি ফিরিয়ে ভেতরদিকে আবার দেখলে চোখে পড়বে মাথার ওপরে একটা বিরাট বড়ো টিনের আচ্ছাদন, একটা বিশাল ছাতার মতন করে পুরো স্টেশনটাকে ঢেকে রেখেছে। আচ্ছাদনের ঠিক নীচেই, মাটির ওপর থেকে অনেকটা উঁচুতে, সারি সারি কাচের জানলা। হয়তো-বা জানলার কাচগুলোকে কেউ পরিষ্কার করেনি বলেই আকাশটা কেমন ঘোলাটে। তবে প্ল্যাটফর্মের খোলা দিকটা দিয়ে তাকালে বোঝা যাচ্ছিল যে, অপরাহ্ণ হয়ে গিয়েছে, যদিও সূর্যটা কোনদিকে হেলেছে, তা ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারলেন না প্রীতিবালা। কিন্তু এই ইট-কাঠ-কংক্রিট আর কলার খোসার মধ্যেই জীবনটাকে আবার চালু করতে হবে কোনোভাবে। তাই চট করে মুখে একটু হাসি মেখে নিয়ে, নতুন জীবনটার প্রথম দুটো পদক্ষেপ নিয়ে হরিহরের কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। গাঢ় স্নেহে বললেন, “তুমি ঠিক এইহানেই কুড়ানিকে লইয়া খাড়া হইয়া থাকো। আমি একটু আগাইয়া ব্যাপারস্যাপার দেইখ্যা আসি। মাইয়াটার লগে একটু দুধ জোগাড় লাগব।”
হরিহর ও প্রীতিবালা কিন্তু একলা নন। তাঁদেরই মতন ছোটোবড়ো অসংখ্য পরিবার, যারা সবেমাত্র সেদিনের ঢাকা মেলে করে শেয়ালদা স্টেশনে এসে নেমেছে, তাদের সকলের চোখেই এক জিজ্ঞাসা। এরপরে কী? প্রীতিবালা তাঁর আশপাশের সহযাত্রীদের উদ্দেশ করে বললেন, “আপনারাও দাঁড়ায়ে থাকেন, যদি চান। আমি চাইরদিক দেইখ্যা ব্যাপারটা একটু বুইঝ্যা আসি।”
মিনিট পনেরো-কুড়ি পরে প্রীতিবালা ফিরলেন। হাতে এক বাটি গরম দুধ আর সঙ্গে একজন স্বেচ্ছাসেবী। স্বেচ্ছাসেবীর শাড়ির ওপরে বেশ বড়ো করে লটকানো আছে কংগ্রেস পার্টির চরকা-কাটা-ছবি-দেওয়া একটা তকমা। তাঁর পিছনে পিছনে এলেন কংগ্রেস পার্টির আরও কয়েকজন সদস্য। সকলের একই রকম চরকা-কাটা তকমা। তাঁদের দেখে শরণার্থীরা ভিড় করে সেদিকে এগিয়ে এলেন। স্বেচ্ছাসেবীদের একজনের হাতে বুঝি একটি ছোটো টুল ছিল। তিনি সেটা মেঝেতে পেতে দিলে, তার ওপরে উঠে সকলকে নমস্কার জানিয়ে শাড়ি-পরা স্বেচ্ছাসেবীটি গলা চড়িয়ে বললেন, “আমার নাম মহাশ্বেতা বসু। আপনারা সবাই অনেক দূর থেকে এসেছেন, অনেক অত্যাচার সহ্য করেছেন, অনেকেই নিজেদের বাস্তুভিটা ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন! আপনাদের কলকাতায় স্বাগত জানাই। আপানারা এখানে এসেছেন অনেক আশা নিয়ে। আপনাদের ওপরে যেরকম মানবেতর অত্যাচার চলেছে, ইতিহাসে তার জুড়ি নেই। আমরা আপনাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাই। আমরা জানি যে সব চেয়ে প্রথম, আপনারা শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ জীবন কামনা করেন। আমাদের কংগ্রেস পার্টিরও একই লক্ষ্য আপনাদের জন্য। এই ব্যাপারে, আমরা আমাদের যতদূর সাধ্য, সাহায্য করব আপনাদের। কলকাতায় আপনারা নিরাপদ। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, পূর্ববঙ্গের এই ন্যক্কারজনক ঘটনাগুলি ঘটছে এত দ্রুত, এবং আমরা এখানে যে পরিমাণে শরণার্থী পাচ্ছি প্রতিদিন, সেই পরিমাণে নাগরিক পরিকাঠামো আমাদের শহরে নেই। আমরা চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, পরিকাঠামোর উন্নতি করাতে, আপনাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে। এ ব্যাপারে কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের নেতাদের সঙ্গে আমাদের পার্টির নেতাদের প্রায় প্রতিদিনই আলোচনা চলছে। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির প্রধানমন্ত্রী, শ্রীসুরাবর্দির সঙ্গেও আমরা যোগাযোগে আছি।
“আপাতত, আপনাদের বিশ্রামের জন্য কিছু জরুরি ব্যবস্থা করা আছে, যদিও তা স্থায়ী কিছু নয়—আমাদের সাধ্যমতন, তাড়াতাড়ির মধ্যে যা করা গেছে। কিন্তু তার আগে একটা প্রশ্ন করি। আমরা জানি যে, আপনাদের মধ্যে কারও কারও চেনাশোনা লোকজন বা আত্মীয়স্বজন রয়েছেন কলকাতায়। তাঁদের আমি অনুরোধ করব, একটুখানি আমার ডান পাশে সরে এসে দাঁড়াতে।”
মহাশ্বেতার কথায় কয়েকটি পরিবার একটু বাঁদিকে গিয়ে গোল হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁদের উদ্দেশ করে মহাশ্বেতা বললেন, “আপনাদের যখন বন্ধু বা পরিবার কেউ কেউ আছেন এখানে, তখন আপনারা ইচ্ছেমতো তাঁদের কাছে চলে যেতে পারেন, এখানে অপেক্ষা করবার কোনো প্রয়োজন নেই। যদি কারও কোনো সাহায্য লাগে ঠিকানাপত্র বার করতে, বা সেখানে কীভাবে যাবেন তা জানতে, তাহলে আমি দীপংকর মুখার্জি ও প্রণব সেনকে অনুরোধ করব একটু সাহায্য করতে। দীপংকর, প্রণব, তোমরা কোথায়?”
দীপংকরবাবুরা হাত তুলে এগিয়ে এলেন। শরণার্থীদের এই দলটি অবশ্য সংখ্যায় বেশ কম, কারণ যাঁদের আত্মীয়স্বজন আছেন এই অঞ্চলে, তাঁদের আত্মীয়রা ইতিমধ্যেই হয় তাঁদের স্টেশন থেকে নিয়ে যেতে এসেছিলেন, নয়তো-বা অন্য কোনো ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তাই বেশির ভাগই ততক্ষণে স্টেশন ছেড়ে চলে গিয়েছেন।
কিন্তু যাঁদের কেউ জানাশোনা নেই বা আর কোথাও যাবার জায়গা নেই, তাঁদের সংখ্যা অনেক বেশি। মহাশ্বেতা এবারে তাঁদের উদ্দেশ করে বললেন, “এবারে একটু সমস্যার কথা আপনাদের জানাই। আমাদের এখানে প্রায় গত এক মাস ধরে প্রতিদিন এত করে শরণার্থী আসছেন নোয়াখালি অঞ্চল থেকে, যে আমাদের এখন আর আশ্রয় দেবার মতন পরিকাঠামো বাকি নেই। রোজ প্রায় আড়াইশোজন করে মানুষ নিঃস্ব হয়ে ঢাকা মেলে চেপে কলকাতায় চলে আসছেন… বেশির ভাগের তো আত্মীয়স্বজনও নেই এখানে! তাঁরা কোথায় যাবেন, তাঁরা নিজেরাই জানেন না! আমরা তাঁদের কোথায় পাঠাব? আবারও একটু ভালো করে ভেবে দেখুন, যদি কাউকেও চেনেন, দীপংকরবাবুরা তাঁদের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ করিয়ে দিতে সাহায্য করবেন।”
প্রীতিবালা চট করে আশপাশ তাকিয়ে, মনে মনে একটু হিসেব করে দেখলেন যে, হ্যাঁ, ঠিকই তো। আজকেও প্রায় দুশো লোক অন্তত এই ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন গন্তব্যহীন হয়ে। প্রতিদিন দুশো-আড়াইশোজন করে শরণার্থী আসছেন? কোথায় যাবে সকলে? তিনি মহাশ্বেতাকে উদ্দেশ করে একটু হতাশ হয়েই বললেন, “কিন্তু আমাগো তো কেউ জানা নাই কলকাতায়, আমরা কুথায় গিয়া দাঁড়াই?” প্রীতিবালার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রায় পঞ্চাশজন স্ত্রী-পুরুষ মিলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন, “আমরা কী করুম? প্রাণের ভয়ে তো পালাইয়া আইসি। অ্যাহন কোথায় গিয়া দাঁড়াই? আপনারা সরকার থিক্যা কিছু ব্যবস্থা করেন আমাদের লগে…”
মহাশ্বেতা একটু করুণভাবে বলে উঠলেন, “আমরা তো যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছি স্যার, কিন্তু দেখুন, আমরা তো আর সরকার নই। আমাদের প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দি সাহেব নিশ্চয়ই এই সমস্যাটার সমাধান করবার চেষ্টা করে চলেছেন জরুরিভাবে, তবে সরকারের কাজ তো! সময় লাগে অনেক, আপনারা তো জানেনই!”
মহাশ্বেতার শেষের দিকের কথাগুলোর মধ্যে কৌতুক, নাকি একটু প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপ ছিল, তা ঠিক বোঝা গেল না। তবে তিনি আরও বলে চললেন, “আমরা তো শুধু স্বেচ্ছাসেবী—কংগ্রেস পার্টি আমাদের সকলকে আপনাদের এই বিপদে পাশে এসে দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছে। অবশ্য সত্যি বলতে কী, শুধু কংগ্রেসই নয়, বামপন্থী দলেরা, সমাজবাদী দলেরা, কলকাতার ব্রাহ্মসমাজেরা, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতি, বিলাস রায় কাতরা সেবা দল, এবং এইরকম আরও অনেক প্রতিস্থানই এগিয়ে এসেছে এই স্বেচ্ছাসেবায় কাঁধ মেলাতে।”
একজন শরণার্থী একটু ঝাঁজ দেখিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, “আরে, তাতে আমাগো লাভ কী হইল, শুনি? আপনি তো কইতাসেন যে আমাগো কোথাও স্থান নাই!” আর-একজন বলে উঠলেন, “তাহইল্যে তো আমি এইহানেই শুইয়া পড়তাসি, দেখি, আপনারা কী করেন! আমারে মাইর্যা ফালাইবেন?” বলতে বলতে তিনি তাঁর কম্বলের বান্ডিলটা প্ল্যাটফর্মের ওপরেই খুলে পাততে শুরু করলেন। তাঁর দেখাদেখি বেশ আরও কয়েকটি পরিবারও তাঁদের কম্বলগুলো খুলতে শুরু করলেন।
“আরে করছেন কী, করছেন কী!” সব ক-টি স্বেচ্ছাসেবী মিলে একসঙ্গে হাঁ হাঁ করে উঠলেন, “না, না, এখানে নয়, এখানে নয়…”
প্রীতিবালা একটু উষ্ণ হয়েই বললেন, “তাহলে কোন লগে যামু, আপনারাই কইয়্যা দেন, নাকি আজ গলায় দড়ি দিয়া এইহানেই মইর্যা যাই, ল্যাঠা চুইক্যা যাইব!”
মহাশ্বেতা দৌড়ে এসে প্রীতিবালার দু-হাত ধরে অনুনয় করে বললেন, “মাসিমা, বিশ্বাস হারাবেন না। আমরা তো চেষ্টা করে চলেছি যথাসাধ্য! সমস্যাগুলোর কথা আপনাদের বললাম, কারণ বাস্তব অবস্থাটা জানা তো সকলের প্রয়োজন! কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা কোনো সাহায্য করব না। আপনারা আমাদের সঙ্গে আসুন সকলে। এই ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে অনেক ট্রেন আসে রোজ, আর কোনো শৌচাগারও নেই কাছাকাছি। তাই এই প্ল্যাটফর্মটা থাকবার জন্য মোটেও উপযুক্ত নয়। অবস্থাগতিকে স্টেশনমাস্টার সামান্য একটা বিকল্প ব্যবস্থা করবার অনুমতি দিয়েছেন স্বেচ্ছাসেবীদের। স্টেশনের দক্ষিণদিকের কয়েকটা প্ল্যাটফর্মে কিছুদিন থাকা সম্ভব হবে। কাছেই শৌচাগার ও পানীয় জলের ব্যবস্থা রয়েছে ওখানে। আর-একটা অস্থায়ী রান্নাঘরও তৈরি করা হয়েছে এই ক-দিন আগে—একটু ডাল-ভাত তৈরি করে নেবার জন্য। সেখানেই আপনাদের নিয়ে যাবার নির্দেশ আছে আমাদের। কিন্তু এটা শুধুমাত্র কয়েক দিনের মতন অস্থায়ী ব্যবস্থামাত্র, তার বেশি নয়, মনে রাখবেন। আমরা আশা করছি যে, কিছুদিনের মধ্যেই আপনারা নিজস্ব কোনো ব্যবস্থা করে নিতে পারবেন। কোথাও না কোথাও ভাড়াবাড়ি বা কোনো চাকরি নিশ্চয়ই খুঁজে পেয়ে যাবেন। এখন আমাদের সঙ্গে আসুন।”
স্বেচ্ছাসেবকেরা শরণার্থীদের পথ দেখিয়ে দক্ষিণদিকের প্ল্যাটফর্মের দিকে নিয়ে গেলেন। সেখানে ১৫ আর ১৬ নম্বর প্ল্যাটফর্ম দুটোকে, মোটা দড়ি বেঁধে আলাদা করে শরণার্থীদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু গত এক মাস ধরে ‘ক্রমাগত-আসতে-থাকা’ শরণার্থীদের মধ্যে, অনেকেই সারি বেঁধে কম্বল পেতে বেশ কিছু জায়গা দখল করে রেখেছেন ইতিমধ্যেই।
দড়ি-বাঁধা অঞ্চলে ঢোকবার মুখে, দুটো টেবিল পেতে স্বেচ্ছাসেবক ডিউটি দিচ্ছেন নিকটবর্তী নীলরতন হাসপাতালের কজন ডাক্তার ও কম্পাউন্ডার। ডাক্তারবাবুরা সকলেকে ওপর ওপর হলেও, একটু পরীক্ষা করে দেখছেন। তারপরে কম্পাউন্ডারবাবুরা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে দিচ্ছেন কলেরার ইনজেকশন। দুজন পুরুষ ও একজন নারীকে হাসপাতালে পাঠানো হল টিবি সন্দেহ করে।
কলেরা ইনজেকশন নিয়ে আবার একটা টেবিল পেরোতে হল। সেখানে দুজন সরকারি কর্মচারী বসে বসে, দুটো মোটা খাতায় সকলের নাম নথিভুক্ত করছেন। প্রীতিবালা তাঁদের তিনজনের নাম লিখিয়ে নিলেন। হরিহর কুড়ানিকে কোলে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রীতিবালা এসে তাঁকে বললেন, “আমাদের নাম-পরিচয় লিইখ্যা দিসি। কুড়ানিকে কইসি আমাগো বাপ-মা-মরা নাতনি। নাম দিসি ‘সুজাতা’। ওকে আর তুমি ‘কুড়ানি’ কইবা না। আজ থিক্যা ওর নাম ‘সুজাতা’।”
সব কিছুর পরে, শরণার্থীরা দড়ি পেরিয়ে ১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢোকবার অনুমতি পেলেন। তখন আবার ভালো জায়গা দখল করবার জন্য একটা বিশ্রী রকমের হইচই লেগে গেল। যতীনবালা বলে একজন বিধবার সঙ্গে একটি পরিবারের তো তুমুল ঝগড়া বেধে গেল। যতীনবালা আগে থেকেই টিনের ঢাকার তলায় একটা জায়গা নিয়েছিলেন, যাতে করে ঝড়বৃষ্টির ঝাপটাটা গায়ে না পড়ে। কিন্তু অন্য পরিবারটিরও ওই জায়গাটাই চাই, কারণ তাদের একটি ছোটো বাচ্চা আছে! অনেক বাগ্বিতণ্ডার পর, শেষ পর্যন্ত প্রীতিবালার মধ্যস্থতাতেই, অন্য পরিবারটির জন্য আর-একটি ভালো জায়গা পাওয়া গেল। প্রীতিবালারা জায়গা পেলেন প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝিতে। ধারের দিকে হলে হয়তো একটু ভালো হাওয়া পাওয়া যেত, মধ্যেখানে ভ্যাপসা গরম। কিন্তু ক-দিনের জন্য তো মাত্র, তাই প্রীতিবালা আর বেশি বিতর্কে জড়ালেন না।
একসময় অন্ধকার নেমে এল শেয়ালদা স্টেশনের ওপর। সারাদিনের কোলাহল স্তব্ধ। প্ল্যাটফর্ম নম্বর ১৫ আর ১৬-র মেঝের ওপরে, নতুন আর পুরোনো শরণার্থী মিলিয়ে প্রায় চারশোটি পরিবার, শ্রান্ত হয়ে ঘুমের মধ্যে একটুখানি শান্তি নামার অপেক্ষা করছেন। হরিহর আস্তে করে বললেন, “কলকাতায় প্রথম রাত! ভিটের মাটিটা কি তবে প্ল্যাটফর্মটাতেই ছড়ায়ে দিমু এইবারে?” প্রীতিবালা বিষম রেগে বললেন, “আ মরণ! রসিকতা করবার সময় আর পাও নাই তুমি! চুপ কইর্যা ঘুমায়ে পড়ো দেখি। কাল থিইক্যা তো বাঁচার লগে অ্যাক্কেরে আসল সংগ্রাম শুরু হইব।”
হরিহর খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসতে হাসতে পাশ ফিরে চোখ বন্ধ করলেন।
বিজয়গড়
আমরা জানাব আমাদের দাবি অভাবিত ঘোষণায়,
কঠোর কণ্ঠে জানাব মোদের অধিকার দুনিয়ায়।
আমরা বাঁচিতে চাই,
কে বাঁচিবে বলো, স্বাধীন-মাটিতে মোরা যদি ম’রে যাই? (‘আমাদের দাবি’, সুনির্মল বসু)
১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। খুব ধুমধাম করে ফোর্ট উইলিয়ামস-এ তোপ দেগে ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। শেয়ালদা স্টেশনে মাথার ওপরে ঝোলানো মাইকগুলো থেকে সারাদিন দেশাত্মবোধক গানের মিছিল চলেছিল। কেবল মাঝে মাঝে কোন প্ল্যাটফর্মে কোন ট্রেন আসবে-যাবে, এইসব মামুলি ঘোষণার জন্য যা একটু বিরাম ছিল। হ্যাঁ, প্রীতিবালারা এখনও শেয়ালদা স্টেশনেই আটকে আছেন। কেবল একটাই তফাত। আজ থেকে তাঁরা ‘ভারতীয় নাগরিক’, শুধু শরণার্থী নন। অবশ্য যেহেতু তাঁরা স্বাধীনতার আগে সীমান্ত পেরিয়েছিলেন, সেহেতু চাইলে তাঁরা পাকিস্তানের নাগরিকও হয়ে যেতে পারতেন। তবে প্রীতিবালা যে আর কখনও পাকিস্তানে ফিরে যাবেন না, তাতে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। তখনও পূর্ববাংলার শরণার্থীরা রোজই অবিরামভাবে আসছেন ঢাকা মেল-এ করে। গত এক বছরে, প্রীতিবালার নিজের চোখের সামনে দিয়ে, অন্তত এক লক্ষ শরণার্থী এসেছেন পূর্ববাংলা থেকে। আজও এসেছেন, কালও আসবেন। কিন্তু কাল থেকে যেসব শরণার্থী আসবেন, তাঁরা হবেন পাকিস্তানের নাগরিক, উদ্বাস্তু হিসেবে ভারতে আশ্রয়প্রার্থী। সময়ের কাঁটাটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে এই জনস্রোত, এখনও অবাধে চলবে আরও প্রায় উনত্রিশ বছর ধরে। সব মিলিয়ে ১৯৪৬ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭৬-এর মধ্যে চল্লিশ লক্ষেরও বেশি শরণার্থী নিঃস্ব হয়ে এসে কলকাতার পথে-প্রান্তরে নতুন জীবনের সন্ধান করবেন।
কিন্তু ১৯৪৭ সালের সেই দিন, স্বাধীন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে, মুখ্যমন্ত্রীর পদে শপথ নিলেন ডা. বিধানচন্দ্র রায়—রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের বংশধর। ঠিক তেমনই তেজস্বী, তেমনই কর্মঠ। গত এক বছরের অস্থায়ী সরকারের পর একটি স্থায়ী সরকার আসায় অনেকেই আশাপ্রদ হলেন যে, এইবারে বুঝি ‘রিফিউজি’ সমস্যার যথার্থ সমাধান শুরু হবে। পুনর্বাসনের কাজও হবে পুরো।
ঠিক এক বছর আগে, ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসের ১৫ তারিখে, এক মাসের শিশু সুজাতাকে কোলে নিয়ে প্রথম শেয়ালদা স্টেশনে নেমেছিলেন হরিহর আর প্রীতিবালা। সেদিন থেকে প্রায় প্রতিদিনই তাঁরা আশা করে এসেছেন, আজকালের মধ্যেই তাঁদের পুনর্বাসন হয়ে যাবে। তাঁদের আগে, পরে, বা একসঙ্গে আসা অনেক শরণার্থীই, কলকাতার এদিকে-ওদিকে খুঁজে, কেউ চাকরি, কেউ মাস্টারি, কেউ মিস্ত্রি হয়ে, কেউ-বা গানের টিচারি পেয়ে, ১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মের আস্তানা ছেড়ে ধীরে ধীরে নতুন জীবনের ভাঁজে মিলিয়ে গিয়েছেন। অনেকে আবার চলে গিয়েছেন আশপাশের জেলায় বা অন্য প্রদেশের পুনর্বাসন ক্যাম্পে। কিন্তু স্টেশন খালি থাকেনি মোটেও। প্রতিদিনই নতুন নতুন শরণার্থী এসে পূরণ করেছেন সেইসব শূন্যস্থান। নতুন আশার স্বপ্ন বুনেছেন ওই প্ল্যাটফর্মেরই সিমেন্টের ওপরে, পুরোনো স্মৃতিতে, রাতের নিবিড়ে, আগুন-চোখের জল মুছতে মুছতে। কিন্তু সে আশা সফল হয়নি সকলের। দুঃখ, দারিদ্র্য, অর্থাভাব; পুষ্টির অভাব; অপরিচ্ছন্নতা—বিশেষ করে শৌচাগারের, আর ছোঁয়াচে রোগের আক্রমণ—এইসব মৃত্যুদূত পাঠিয়ে কত মানুষের প্রাণ অকালে কেড়ে নিয়েছে নিয়তি! নেকড়ের মতো হাতছানি দিয়ে, কত তরুণী মেয়ের প্রলোভনের টোপ ফেলে, অন্ধকারের জগতে টেনে নিয়ে গিয়েছে কত সুযোগসন্ধানী পিশাচেরা।
প্রীতিবালাদের স্থিত হবার উপযুক্ত কোনো সুযোগ গত এক বছরেও হাতে আসেনি তেমন। স্থানীয় মহিলা সমিতির উদ্যোগে একটা সেলাইয়ের ক্লাসে যোগ দেবার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শেয়ালদা থেকে রোজ গড়িয়াহাটা যাবার সামর্থ্য বা উপায়, কোনোটাই ছিল না তাঁর। তা ছাড়া কীভাবেই-বা সুজাতাকে অতক্ষণ ফেলে রেখে যাবেন? সে তো কোনো না কোনো কাণ্ড ঘটিয়ে বসে থাকবে নিঃসন্দেহে। হরিহর বয়সের কারণে কোথাও চাকরি পেলেন না। তা ছাড়া তাঁর হাবভাব দেখেই আজকাল বোঝা যায় যে তিনি এখন হতোদ্যম, বিষণ্ণ একটি মানুষ। আজকালকার কারখানায় নানান রকমের মেশিনপত্র থাকে। প্রায় ষাট বছর বয়সের একজন বৃদ্ধ, আর কিছু না হোক, বিষণ্ণতার কারণেই হয়তো একদিন কোনো মেশিন চালাতে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনা বাধিয়ে ফেলবেন। তাই কারখানায় কেউ চাকরি দিতে চায়নি তাঁকে। এদিকে পড়াশোনাও এমন কিছু শেখেননি কোনোদিন, যে কোথাও গিয়ে টিউশনি বা মাস্টারি করবেন তিনি। উপার্জন বলতে কেবল স্টেশনের মধ্যেই মাঝে মাঝে কিছু পুজোআচ্ছা করেছেন। অনেক দুর্ভাগা মানুষের পরলোকযাত্রার আচার পালন করিয়ে দিয়েছেন। কিছু অন্নপ্রাশন, কিছু সত্যনারায়ণপুজো, এমনকি একটা বিবাহও! কিন্তু এতে করে খুব সামান্যই দু-চার পয়সা ক্বচিৎ কখনও ঘরে এসেছে—তাঁর যজমানদের কাছেই-বা পয়সা কোথায়! কাজেই সরকার থেকে যা সামান্য শরণার্থী ভাতা পেয়েছেন পরিবার হিসেবে, তা-ই দিয়েই কোনোরকমে দিন চালাতে হয়েছে তাঁদের। বেশিটাই নির্ভর করেছেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর ওপরে। তারাই রোজ সকালে কলা-চিঁড়ে বা দুধ-চিঁড়ে দিয়ে জলপানি খাইয়েছে। দুপুরে সাধারণত একটু খিচুড়ি আর বাঁধাকপির ডালনা। রাতের খাবার আলাদা করে সব সময় জোটেনি। জুটলেও একটু মোটা লাল চালের সেদ্ধ ভাত আর নামমাত্র ডাল। তাই দুপুরের খাবার থেকে সব সময়ই কিছুটা করে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন প্রীতিবালা, রাত্রে খাবেন বলে। তেমন খাবার না জুটলে ‘খিদে নেই’ বলে সেদিন সবটাই সুজাতা আর হরিহরকে খাইয়ে দিয়েছেন। কেবল ন-মাসে/ছ-মাসে এক-আধবার স্টেশন থেকে বেরিয়ে, রাস্তার উলটোদিকের শেয়ালদা মার্কেট থেকে চুনোমাছের শুঁটকি কিনে এনেছেন হরিহর। সেসব দিনে প্রতিবেশীদের ডেকে শুঁটকি মাছের চচ্চড়ি খাইয়েছেন প্রীতিবালা। একটু একটু করে হলেও সবাই আনন্দের সঙ্গে ভাগ করে খেয়েছেন।
এইভাবেই জীবন কেটেছে প্রীতিবালাদের এবং তাঁদের মতন আরও কতশত পরিবারের—মাটির ধুলোয় লুটিয়ে, অজানা, আসন্ন, অনাগত কোনো সমাধানের জন্য অপেক্ষা করে করে। তবু, জীবনে যে কোনো পুরস্কার নেই, তাও নয়। প্রীতিবালার ব্যক্তিত্বের জন্য সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করেন, ভালোওবাসেন। ১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম সমাজের মধ্যে তিনিই বয়োজ্যেষ্ঠা এবং সম্ভবত প্রাচীনতম বাসিন্দা এখন। তাই কোনো খবরের কাগজ, পত্রিকা বা রেডিয়োর সাংবাদিকেরা এসে শিয়ালদা স্টেশনের ‘রিফিউজি সমস্যা’ নিয়ে কারও সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে চাইলে, সবাই তাঁদের পাঠিয়ে দেন প্রীতিবালার কাছেই। প্রীতিবালাও কোনোরকম কুণ্ঠা না করে, সাংবাদিকদের বেশ স্নিগ্ধভাবেই বুঝিয়ে দিতে পারেন, যে এইভাবে কলকাতার স্টেশনটি আটকে রেখে, তাঁরা কিছু গর্হিত অপরাধ করছেন না। সমস্যাটা তাঁরা নন! তাঁরা হিন্দু বাঙালি। অভাবনীয় ক্রূরতার মুখে কোনোরকমভাবে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে, ‘হিন্দু-বাঙালিদের প্রধান শহর’ কলকাতায় এসেছেন আশ্রয় খুঁজতে। হিন্দু হিসেবে, বাঙালি হিসেবে, তাঁদেরও একটা বৈধ দাবি, একটা জন্মগত অধিকার আছে পুনর্বাসন পাবার। যতদিন না পর্যন্ত কোনো গ্রহণযোগ্য পুনর্বাসন তাঁরা পাচ্ছেন, ততদিন এই শেয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে থেকে যাওয়া ছাড়া আর কি তাঁদের কোনো উপায় আছে? তাঁরা কি প্ল্যাটফর্মে শুয়ে খুব বিলাসিতার মধ্যে আছেন? অবশ্য সেই সঙ্গে তিনি এই কৃতজ্ঞতাটাও কখনও জানিয়ে দিতে ভুলে যান না, যে যতই হোক, তাঁরা যত কষ্টের মধ্যেই থাকুন না কেন, আর কলকাতা শহর তথা পশ্চিমবঙ্গ যত শীর্ণকায় বা যত দরিদ্রই হয়ে পড়ুক না কেন, তবু কলকাতা তাঁদের তাড়িয়ে দেয়নি, স্থান দিয়েছে। কারুর নতুন জীবন তৈরী করবার প্রচেষ্টায় সে কোনও অন্তরায় সৃষ্টি করেনি।
১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম সমাজের প্রধান মুখপাত্র হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়াবার ফলে সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং শরণার্থীদের অধিকার রক্ষা করবার জন্য উৎসাহী, এমন সমস্ত আইনজীবীর মধ্যে তাঁর কিছুটা জায়গা হয়ে গেল। এঁদেরই সঙ্গে মিলে একবার তিনি গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে বৈঠক করে এলেন। ডা. রায় অত্যন্ত সমবেদনশীল হওয়া সত্ত্বেও প্রতিনিধিদের জানিয়ে দিলেন, যে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য, এই দুই সরকার মিলে সমন্বয় করে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ফাঁকা ও উর্বর জায়গা বেছে ‘পুনর্বাসনকেন্দ্র’ তৈরি করছে বাঙালি উদ্বাস্তুদের জন্য। তবে সেগুলো তৈরি হতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে। যখন প্রীতিবালা উল্লেখ করলেন যে, বাঙালিরা কিন্তু বাংলাতেই পুনর্বাসিত হবার অধিকার চায়, তখন ডা. রায় বললেন, “দেখুন প্রীতিদেবী, দেশভাগের পরে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন আগের আয়তনের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ হয়ে গিয়েছে। অনেক উৎপাদনকেন্দ্র, যেমন পাট উৎপাদনকেন্দ্রগুলো, আমরা সব হারিয়েছি। এ ছাড়া তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ আর ছেচল্লিশের ভয়াবহ দাঙ্গা—এই সব কিছুর মোকাবিলা করতে বাধ্য হয়ে আমাদের আর্থিক ভাণ্ডার এখন একেবারে শূন্য। আমাদের পক্ষে কি সব কিছু ইচ্ছেমতো করা সম্ভব?” ডা. রায় প্রতিনিধিদের সমস্ত দাবি মেনে না নিলেও কিন্তু, প্রীতিবালা ডা. রায়কে শ্রদ্ধা ও তাঁর অবস্থানকে যথেষ্ট প্রশংসা না করে পারেননি।
এর কয়েকদিন পরের একটি রবিবারে শম্ভু গুহঠাকুরতা, কালু সেন, আশিস দেব রায় এবং শান্তিরঞ্জন সেন—এই চারজন যুবক মিলে ১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে হাজির হলেন প্রীতিবালার সঙ্গে কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে। এঁরা চারজন পস্পরের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। এঁদের পরিবারেরা, প্রীতিবালাদের আসবার কিছুদিন আগেই, পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় পালিয়ে এসেছিলেন নিজেদের প্রাণ রক্ষা করতে। এই শেয়ালদা স্টেশনেই ঠাঁই হয়েছিল তাঁদেরও। তারপরে প্রীতিবালারা এসে পৌঁছোলে সব ক-টি পরিবারের মধ্যে খুবই সৌহার্দ্যের সৃষ্টি হয়। চারজন তরুণ বন্ধু প্রীতিমাসির খুব ভক্তও হয়ে পড়েন।
এই চার বন্ধুর ধমনিতে বয়ে চলে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মতো বুকের পাটা, বাঘাযতীনের মতো সাহস, বিনয়-বাদল-দীনেশের মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আত্মত্যাগ করবার মতো আগুন। তাঁরা অগ্নিযুগের স্ফুলিঙ্গ! প্ল্যাটফর্মের মানবেতর অস্তিত্ব যখন তাঁদের ওপরে অকস্মাৎ আরোপিত হল, তখন তাঁরা সেটাকে ‘অতি সাময়িক’ বলেই মেনে নিয়েছিলেন কেবল। তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন যে শেষ পর্যন্ত একটি স্বাভাবিক জীবন শুধু তাঁদের প্রাপ্যই নয়, বাংলার বাঙালি হিসেবে সেটা তাঁদের মৌলিক অধিকার। কিন্তু অধিকার তো সব সময় নিজে থেকে হেঁটে এসে, মানুষের কোলে উঠে তার গলার মালা হয়ে ওঠে না! তার জন্য অনেক সময় করতে হয় সংগ্রাম। আর সংগ্রাম করতে হয় ধাপে ধাপে। প্রথম ধাপ, নিজেদের পায়ে দাঁড়ানো, উপার্জনক্ষম হয়ে ওঠা।
তাই প্রতিদিন সকালবেলায় স্বেচ্ছাসেবীদের হাতের চিঁড়ে-কলা খেয়েই বেরিয়ে পড়তেন চারজনে। বাসের ভাড়া না থাকলেও, যেতেন পদব্রজে, সারা শহরের আনাচকানাচে। তাঁদের প্রীতিমাসি, স্বেচ্ছাসেবীদের বলে-কয়ে চারজনের জন্য দুপুরের খাবার কিছু সংরক্ষণ করে রাখতেন, দিনশেষে অন্তত কিছু মুখে দেবার জন্য। সৌভাগ্যবশত, কিছুদিনের মধ্যেই দক্ষিণ কলকাতার উষা সেলাই মেশিনের কারখানায় বেশ ভালো চাকরি পেয়ে গেলেন চার বন্ধু। সেখানেই কোনোরকমে একটি ভাড়াবাড়ি জোগাড় করে, পরিবারদের শেয়ালদা স্টেশন থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁরা।
কিন্তু সেটা তো হল মাত্র প্রথম ধাপ। তা ছাড়া, তাঁদের নিজেদের কাজ হয়ে গেলেই তো আর লক্ষ্যে পৌঁছোনো হল না সকলের। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়, শেয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে প্ল্যাটফর্মে যেসব মানুষ এখনও তাঁদের জীবনের সামান্য মৌলিক অধিকারগুলোই পূর্ণ হবার আশায় বসে আছেন, তাঁদেরকেও তো এই অর্ধমানবের মতন অস্তিত্ব থেকে উত্তোলন করে নিতে হবে! তাই এই চার বন্ধু মিলে ক্রমাগতই সন্ধান করে গিয়েছেন ‘রিফিউজিদের নির্ভয়ে বাসা বাঁধবার মতো জায়গা’র। আজ তাঁরা সেই কারণেই দৌড়ে এসেছেন প্রীতিমাসির কাছে, একটা সম্ভাব্য ‘জায়গা’ খুঁজে পেয়েছেন বলে জানাতে।
১৯৪৭ সালের কলকাতা শহর আজকের মতো এত বিস্তৃত ছিল না। দক্ষিণদিকে কালীঘাট পেরোলেই অনেক অঞ্চল তখনও জলাজঙ্গলে ভরতি ছিল। দক্ষিণ-পূর্বে, যাদবপুরও তা-ই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই অঞ্চলে মিত্রবাহিনীর কিছু সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল। অতএব তাদের তো একটা বাসস্থান চাই! সেই কারণে ব্রিটিশরাজ, একটি সৈন্য আবাসন বা ‘ব্যারাক’ তৈরি করেছিলেন যাদবপুরে। যুদ্ধের পর থেকে সেটি এখন পরিত্যক্ত।
“আমরা ভালো কইর্যা ঘুইর্যা দেখসি, মাসি। ওই জায়গাটা পরিষ্কার করাইলে, আমাগো গুটা দশ পরিবার লইয়া, দিব্যি একটা কলোনি শুরু করা যাইব।”
“কী কইতাসস তোরা! কইলেই অইল নাকি? ওই ব্যারাক কার? জমি কার? তাদের জিগাইসস?”
“জিগাইব ক্যানে? জিগাইলে থাকতে দিব ভাবতাসো, মাসি? না, দিব না। তাই আমরাও জিগাইব না। গিয়া জবরদখল কইর্যা নিব!”
“জবরদখল কইর্যা নিবি? জবরদখল? তদের মাথা খারাপ হইয়া গ্যাসে একেবারে!”
শম্ভু-কালু-আশিস আর শান্তিরঞ্জন জানতেন যে, প্রীতিবালাকে এই ব্যাপারে খুব সহজে রাজি করানো যাবে না। এদিকে প্রীতিবালাকে তাঁদের চাইই চাই! আর কে আছেন, যিনি প্রীতিমাসির মতন এমন সহজাত নেতৃত্বের অধিকারী? আর কে আছেন, যিনি মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে শুরু করে সব সাংবাদিকের কাছেই সুপরিচিত? একবার জবরদখলের পথে গেলে অনেকই বাধা আসবে পথে। তখন প্রীতিবালার মতন শান্ত ও কার্যকর নেতৃত্বের খুবই প্রয়োজন হবে। তাই মাসিকে দলে টানতে তাঁরা নানারকমভাবে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন। বিশেষ করে জবরদখল কলোনির আইনি ভিত্তি নিয়ে তাঁরা বেশ গবেষণা করেছিলেন। শরণার্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল বেশ কিছু আইনজীবীর সঙ্গেও আলোচনা করে এসেছিলেন।
শান্তিরঞ্জন বোঝালেন যে শুধু আজ নয়, হাজার বছরেরও আগে থেকে, রোমান, গ্রিক আর ইজিপশিয়ান রাজারা, নতুন রাজ্য জয় করেই, জোর করে জমি কেড়ে নিয়ে নিজেদের কাজে লাগাত। আরও সাম্প্রতিককালে, ইউরোপের বহু রাজ্যই ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের জন্য আকছার জমি জবরদখল করত। এমনকি আমাদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও বহু খালি জমি জোর করে দখল করে নিজেদের নীলচাষে কাজে লাগাত! এ ছাড়া, মাত্র তিপ্পান্ন বছর আগে ব্রিটিশেরা ‘কলোনিয়াল ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যাক্ট অব ১৮৯৪’ বলে একটি আইন পাস করেছিলেন। সেই আইনটি এখনও ভারতবর্ষে বলবৎ। এই আইনে সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া আছে যে, প্রয়োজন হলে তাঁরা সাধারণ মানুষের কল্যাণার্থে, সমাজসেবী প্রকল্পের জন্য যে-কোনো জমি অধিগ্রহণ করতে পারেন, যদিও তার জন্য জমিটির ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করে তা মালিকদের চুকিয়ে দিতে হবে আগে। এই আইনের বলেই সরকার জমি নিয়ে পোস্ট অফিস বা রেল স্টেশন বানাতে পারে। তা রেল স্টেশনই যখন বানাতে পারে, তখন আর আবাসিক প্রকল্পের জন্য জমি নিতে পারবে না কেন?
এই কথাটা প্রীতিবালার খুব পছন্দ হল। বললেন, “হ, এই শ্যাষের যে কথাটা কইলি, কী অ্যাক্টোর কথা কইলি যেন, ওইটাতে কাম হইতে পারে। আমরা জমিতে বইস্যা গিয়া, সরকারকে কইমু জমিটা আমাদের লগে লইয়্যা লইতে। আমি আবার বিধান রায়ের কাছে যামু। তোরা কইত্যাসস অইহানে অনেক জমি ফ্যালো হইয়া পইড়্যা আসে?”
***
এর কিছুদিন পরে, নভেম্বর মাসের ১৫ তারিখে, প্রীতিবালার শেয়ালদা স্টেশনে নামবার ঠিক এক বছর পূর্তির দিনে, শম্ভু-কালু-আশিস আর শান্তিরঞ্জনের নেতৃত্বে, প্রীতিবালা-হরিহরসহ ১২টি পরিবার, শেয়ালদা স্টেশন ছেড়ে, ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে উঠে যাদবপুরের দিকে রওনা দিলেন। একজন ঠিকাদার, ঠ্যালাগাড়িতে অন্তত আশি-পঁচাশিটা পোঁটলা তুলে তাঁদের পিছনে পিছনে রওনা হলেন যাদবপুরের দিকে।
খুব শিগগিরই, যাদবপুরের পরিত্যক্ত আর্মি ব্যারাকে এই বারোটি পরিবারের সফল পদার্পণের খবরটি দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল সারা কলকাতার শরণার্থী মহলে। বন্যায় বাঁধ ভেঙ্গে তোড়ে জল বেরিয়ে যাবার মতন করে কলকাতা ও প্রত্যাঞ্চলের যত শরণার্থী, বিশেষ করে যাঁরা তখনও কোনও স্থায়ী বাসস্থান খুঁজে পাননি, তাঁরা শুধু যাদবপুরের আর্মি ব্যারাক অঞ্চলেই নয়, তাদের গঠন পদ্ধতি অনুসরণ করে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের পরিত্যক্ত ও অনাবাদি জমি খুঁজে বার করে, ‘জবর দখল’ কলোনীর সৃষ্টি করলেন সারা শহর জুড়ে।
যাদবপুরের আর্মি ব্যারাক অঞ্চলের প্রতিষ্ঠাটারা অনেক আঁটঘাট বেঁধে তবেই পথে নেমেছিলেন। প্রথমেই তাঁরা তাঁদের অধিকৃত বাসস্থানকে বৈধ করবার ধাপ নিলেন। তাঁরা ‘যাদবপুর বাস্তুহারা সমিতি’ বলে একটি সংস্থার পত্তন করলেন, যাদের কাজ ছিল দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিধরদের সঙ্গে ফলপ্রসু সম্পর্ক তৈরী করবার যোগ্য একটা সাংগঠনিক পরিকাঠামো তৈরী করা। সেই সূত্রে, প্রীতিবালা দেবীর সাহায্যে তাঁরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বিধবা স্ত্রী, শ্রীমতি বাসন্তী দেবীকে রাজী করালেন সেই সংস্থার নের্তৃত্ব দিতে। প্রখ্যাত বিপ্লবী সন্তোষ দত্তও এসে কাঁধ লাগালেন। সন্তোষ দত্ত ও বাসন্তী দেবীর যুগ্ম প্রভাবে, যাদবপুর বাস্তুহারা সমিতির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ শুরু হল। এই যোগাযোগ ভবিষ্যত সময়ে খুবই কার্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
সমিতি সেইসময়ে আরও একটা বড় দায়িত্ব পালন করেছিল। তা হল, পরিকল্পিতভাবে কলোনীর জমি বন্টন। পুরোনো ব্যারাকটা ভরে যাবার পরে, চারিপাশের অনাবাদী জমিগুলোতেও এসে নতুন বাস্তুহারারা যত্রতত্র বাস করতে শুরু করছিলেন। তখন শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্য সমিতি একটি কঠোর নিয়ম জারি করল। ঠিক হল যে প্রতিটি আগন্তুক পরিবারকে চার কাঠা করে জমি, শুধুমাত্র দু-টাকা মূল্যে বিক্রী করা হবে এবং জমির পরিধি সঠিক ভাবে চিহ্নিত করা হবে। সমিতির এই ধরনের নেতৃত্বের কারনে, ভবিষ্যতে এই কলোনীটি বেশ পরিকল্পিত ভাবে সম্প্রসারিত হতে পেরেছিল। ইতিমধ্যে কলোনীর জমির সাবেক দাবীদার, প্রথমে গুণ্ডা লাগিয়ে, তারপরে আইনি প্রথায়, বাস্তুহারাদের উচ্ছেদ করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু, ১৯৪৯ সালে, বাস্তুহারাদেরই জিত হল। এই বিজয়টাকে উদযাপন করবার জন্য তখন কলনীটির নতুন নামকরন করা হল ‘বিজয়গড়’।
এরপরে শুরু হল লড়াই। সম্মানের সাথে বেঁচে থাকবার লড়াই। প্রায় সমস্ত বাস্তুহারাদেরই এক ইতিহাস – প্রবল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই। শেয়ালদা স্টেশন, রিফিউজি ক্যাম্প, আত্মীয়ের বাড়ি, ভাড়া বাড়ি – এইসমস্ত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে নিজস্ব ঠিকানায় স্থান পাবার লড়াই। কারুর দয়ায় নয়, কারুর দাক্ষিণ্যে নয়, নিজেদের হিম্মতেই বাস্তুহারারা স্থান করে নিলেন এই নতুন, অবাঞ্ছিত-ভাবে-সঙ্কুচিত বাঙলার বুকে! এতদিন পূর্বপুরুষদের বাস্তু থেকে বলপূর্বক উচ্ছেদিত হয়ে, কলকাতায় পৌঁছে, ‘নিজ-ভূমে-পরবাসী’ হয়ে, অনেক দারিদ্র্য, অনেক অসম্মান আর অনেক লাঞ্ছনাকে অগ্রাহ্য করে, শেষ পর্যন্ত জিতে গেলেন তাঁরা। তাঁদের সেই ফাটা দড়মার বেড়ায় খবরের কাগজের তাপ্পি মেরে অস্তিত্বের লড়াই চালিয়ে যাওয়াকে কে হয়ত যথার্থ মর্যাদা দেওয়া আজ আর সম্ভব নয়। অথবা টিনের চালের ওপর প্লাস্টিকের জোড়াতাপ্পি মারা সেই সহজিয়া জীবনবোধকেও নয়। সামান্য জামাকাপড়ে সসম্মানে বেঁচে থাকার সেই মন্ত্রগুপ্তিও পাঠ করবার সুযোগ হয়নি আজকের দিনের বেশির ভাগ লোকের।
এই লড়াইতে প্রীতিবালা বা তাঁরই মতন শত শত বাস্তুহারা গৃহবধুদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। বিশেষ করে প্রীতিবালার। বিজয়গড়ের একজন প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে অনেক প্রতিনিধিত্বে, অনেক সমাবেশে, অনেক সালিশিতে যোগদান করতে হত তাঁকে। তবুও সময় বাঁচিয়ে, লুকিয়ে রাখা বাকি-থাকা দুটো চুড়ির বিনিময়ে একটা ছোট চায়ের দোকান খুলে ফেললেন তিনি। নাম দিলেন ‘বৈকুন্ঠর চায়ের দোকান’ – তাঁদের হারিয়ে ফেলা পুত্র সন্তানের নামে। ব্যাবস্থা করলেন চায়ের কেটলীটিকে সারাদিন উনুনে বসিয়ে রাখতে। উনুনটাকে ঘিরে বসালেন কয়েকটি বেঞ্চি। হরিহর বাবুকে সংসারে একটা কার্যকরী ভূমিকায় যুক্ত করাটা এই ব্যাবসাটি শুরু করবার একটা প্রধান কারন ছিল। তা না হলে হরিহর বড্ড বেশী অবসাদের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিলেন। দোকানে উনুনের সামনে বসে চা বানাতেন হরিহর। আর অন্য কাজে ব্যাস্ত না থাকলে, প্রীতিবালা করে দিতেন ‘জোগাড়’। আর পেয়ালা-পিরিচও ধুয়ে দিতেন সাধ্য মতন। সুজাতা যখন সাত বছরে পৌঁছে গেল, তখন থেকে জোগাড়ের কাজটা করত সে-ইই বেশী। ক্রমে দোকানের খদ্দের বাড়তে থাকল। তারপরে একসময় বিজয়গড়ের সামাজিক জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়াল ‘বৈকুন্ঠর চায়ের দোকান’।
হরিহরের অবসাদ একসময় প্রীতিবালাকে খুবই চিন্তিত করে তুলল। যদিও তাঁদের চায়ের দোকানের সফলতায় হরিহর তাঁর আত্মমর্যাদাটা কিছুটা খুঁজে পেয়েছিলেন, তবু হতাশা তাঁর পিছু ছাড়ছিল না। সেই সময়ে মানসিক ব্যাধির সচেতনতা বা চিকিৎসা আজকালকার মত অগ্রসর হয়নি। কিন্তু বাস্তুহারা অভিজ্ঞতার অভিশাপে, শরণার্থী পুরুষদের অনেকের মধ্যেই তখন এই প্রচণ্ড অবসাদের লক্ষণটা দেখা দিচ্ছিল। শরণার্থী মহিলারা এই ব্যাপারে কিছুটা ভাগ্যবান ছিলেন। ফলে তাঁরাই বাস্তুহারা সমাজের প্রধান খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।
ব্যাধিটা বাড়তে বাড়তে, হরিহর একসময় নিয়মিত দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিলেন। একদিন প্রীতিবালাকে ডেকে বললেন, “জানো, কাল রাইতে নগেনের সাথে দেখা হইল। ওকে জিগাইলাম। ও কইল, দস্যুরা যখন ওর গলাটা কাইট্যা ফালাইল, তখন কিন্তু অর এতটকুও লাগে নাই।”
প্রীতিবালা মনেমনে খুবই চিন্তিত হলেও, মুখে একটু স্বস্তির ভাব দেখালেন। হরিহর খুশী হয়ে আবার দোকানের কাজে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু এই ধরণের দুঃস্বপ্নের হাত থেকে বেশীদিন হরিহরকে বাঁচাতে পারলেন না প্রীতিবালা। একদিন আর দুঃস্বপ্নের জগত থেকে ফিরে আসতে পারলেন না হরিহর। চোখের জল মুছে, সুজাতার মুখ চেয়ে, চায়ের দোকানের দায়িত্বটা পুরোপুরি গ্রহন করলেন প্রীতিবালা। সেই সঙ্গে কলোনীর প্রশাসনের দায়িত্ব থেকেও কিছুটা সরে এলেন তিনি।
কলোনীর প্রশাসন থেকে সরে আসবার অবশ্য আরও একটি কারন ছিল। কিছুদিন ধরে বিজয়গড় সমাজে কিছু অস্বাস্থ্যকর, বিভাজক পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছিল। বিভাজনটা শিক্ষিত-অবস্থাপন্ন এবং অশিক্ষিত-দরিদ্র পরিবারের মধ্যে তফাতের ছলে হলেও, আসলে সেটা ছিল উচ্চবর্ণ আর নিম্নবর্ণের মধ্যে সংঘাত। বিজয়গড়ের প্রতিষ্ঠাতা, আদর্শবাদী যুবকেরা ও ১২টি আদি পরিবারের মধ্যের বেশীর ভাগ মানুষই এই সংকীর্ণতাটা মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই এক এক করে তাঁরা অনেকেই এই কলোনী ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছিলেন। চায়ের দোকানের আয়ের ওপরে নির্ভরতার কারনে প্রীতিবালা অবশ্য প্রথমে বিজয়গড় ছাড়তে চাইছিলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিবেশ ক্রমাগত খারাপ হতে থাকায়, তিনিও স্থির করলেন হরিহর আর বিজয়গড়ের স্মৃতি পেছনে ফেলে, অন্য কোথাও গিয়ে নতুন জীবন শুরু করবেন। সুজাতারও ভাল করে পড়াশুনা শুরু করবার সময় হল।
সুজাতার জীবন
‘কালচক্রে আবর্তিয়া বয়ে চলে জীবন-প্রবাহ,
সুখ-দুঃখ শান্তি-তৃপ্তি অন্তরের দারুণ প্রদাহ
চলে সঙ্গে সঙ্গে
পুরাতন রাত্রিশেষে, প্রত্যাসন্ন দিনের প্রভাতে। (‘বৈশাখী নিশীথ’, সুফিয়া কামাল)
১৯৫৪ সালে প্রীতিবালা যখন বিজয়গড়ে তাঁর অতি জনপ্রিয় ‘বৈকুন্ঠর চায়ের দোকান’-টি বিক্রী করে দিয়ে, গোলপার্কের একটি গলিতে একটি ছোট বাড়ি কিনলেন, তখন সুজাতার বয়স প্রায় আট। স্কুলে যাবার বয়স। কাছেই কমলা গার্লস স্কুল। ক্লাশ থ্রীতে জায়গা হল তার। প্রথম কিছুদিন ঠাকুমা প্রীতিবালাই তাকে হেঁটে পৌঁছতে আর আনতে যেতেন। কিন্তু প্রীতিবালার বয়স তখন প্রায় মধ্য ষাট। শরীরের যন্ত্রপাতিগুলো মোটামুটি ঠিক থাকলেও, হাঁটুর মালাইচাকি দুটোর আশেপাশে মাঝেমাঝেই বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায় নন-কোওপরেশনের। বিশেষ করে বেশী হাঁটাহাঁটি করলে। প্রীতিবালা তখন ‘রিফিউজি সাকসেস স্টোরী’ হিসেবে বিখ্যাত। কপর্দকহীন অভিবাসী হিসেবে এসে শেয়ালদা ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আশ্রয় নিয়ে একবছর বাস করা থেকে শুরু করে, বিজয়গড়ের মত কলোনী প্রতিষ্ঠা করবার মত কৃতিত্ব তাঁর ঝুলিতে আছে! খ্যাতি হয়েছে একজন সফল অভিবাসী ব্যাবসায়ী হিসেবেও। তাছাড়া এখন তিনি ‘যুগান্তর’ পত্রিকার একজন পুরোদস্তুর মাইনে-পাওয়া সাংবাদিক, পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারাদের জীবন সংগ্রাম ও পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতিতে তাঁদের সফলভাবে মিশে যাওয়া-না যাওয়া সম্পর্কিত প্রতিবেদক। সেই কারনে খুবই ব্যাস্ত থাকেন। অতএব আরও দুবছর ধরে এক রিক্সা-কাকুই সুজাতাকে স্কুলে দিয়ে আসা, নিয়ে আসা করতেন। তারপরে অবশ্য একসময় একা একা স্কুলে যাওয়ার স্তরে উত্তীর্ণ হল সুজাতা, যদিও ঠিক একা হল না। পাড়ার দুই বোন, কেয়া আর কৃতিকা – প্রায় সুজাতারই সমবয়সী দুজনে, তারাও কমলা গার্লসে পড়ে। অতএব তিনজনেই হেঁটে যাওয়া আসা শুরু করল একসাথে। অচিরেই তারা হয়ে গেল প্রাণের বন্ধু।
স্কুলের আর পাঁচটা মেয়ের মত হলেও সুজাতার কিছু বৈশিষ্ট ছিল। কেয়া একটু বয়সে বড়। সে সুজাতাকে বলত, “তোকে কিছু বলাই যায় না – তুই একেবারে ডিক্সনারি। তোকে কিছু বললে তুই সেটা কিছুতেই ভুলিস না! মাঝে মাঝে মনে হয় ভুলিয়ে দেবার মেশিন আবিষ্কার করতে হবে তোর জন্য। তা না হলে বড্ড ঝগড়া লাগে” সুজাতা হাসত। সে পড়াশোনাতেও খুব চৌকস। অঙ্কে কখনও ভুল হয় না তার। বড় বড় যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ, এক মূহুর্তেই করে ফেলতে পারে মুখে মুখে সে। দিদিমণিরা বলতেন, বড় হয়ে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করবে সুজাতা। নিশ্চয়ই বড় বৈজ্ঞানিক হবে সে।
বৈজ্ঞানিক হোক বা না হোক, খুবই পশুপ্রেমী ছিল সুজাতা। পথে বেড়ালছানা, কুকুরছানা, এমন কি আহত শালিকছানা দেখলেও, থেমে তাদের শুশ্রুষা না করে সে থাকতে পারতনা। মনটা তার একদিকে বড়ই নরম ছিল –যদিও সুবিচার বা সততার ব্যাপারে খুবই দৃঢ়। ক্লাশের মনিটর হত সে। সকলেই তার কাছে আসতে ভালবাসত সালিশি মানতে।
স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে সে গেল বিজ্ঞান পড়তে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে। নিউক্লিয়ার ফিজ়িক্সে তার বড়ো উৎসাহ। পঙ্কজ দত্তর সঙ্গে দেখা হয়েছিল যাদবপুরের লাইব্রেরিতে। পঙ্কজ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। বই চেক আউট করবার লাইনে আগে ছিল সুজাতা, তার পিছনে পঙ্কজ। মনে হয়, অনেকক্ষণ ধরেই সুজাতার আগাপাশতলা পর্যবেক্ষণ করছিল সে। বেশ জৈবিক আকর্ষণও অনুভব করছিল বোধহয়। সুজাতা লাইব্রেরি থেকে বেরোতেই হাতের বইটা কাউন্টারে ফেলে দিয়ে তার পিছনে ধাওয়া করল পঙ্কজ।
“আপনি সায়েন্স কলেজের?”
সুজাতা মুখ ঘুরিয়ে দেখল খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা একটি ছেলে। মন্দ নয়। বেশ লম্বা। তাই বলল, “কেন? আর্টস কলেজেরও তো হতে পারি!”
“না দেখলাম, কোয়ান্টাম ফিজ়িক্সের একটা বই নিচ্ছেন…”
সুজাতা মুচকি হেসে বলল, “আপনার বই কোথায়? হাত থেকে পড়ে গেছে বুঝি?”
পঙ্কজ অপ্রস্তুত হয়ে তোতলাতে তোতলাতে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, “ওই কফি হাউসে একটু কফি খেতে যাবেন?”
“না!! আমার ক্লাস আছে এখন!” এই বলে আর বাক্যব্যয় না করে ডানদিকে ঘুরে হনহন করে সায়েন্স কলেজের দিকে প্রায় দৌড়েই চলে গেল সুজাতা।
কিন্তু কামদেবের তির তখন বেশ গভীরভাবে বিদ্ধ করেছে পঙ্কজকে। পরের দিন আবার একই রকম সময়ে এসে, অনেকক্ষণ লাইব্রেরির কাছে অপেক্ষা করল সে। যদি আসে! তার পরের দিনও। এবং তার পরের দিন, তার পরের দিন, আবার তারও পরের দিন। এইভাবে সপ্তাহ কেটে গেল, মাসও। দু-তিন মাস ধরে তিরবিদ্ধ হয়ে ছটফট করে, একদিন হঠাৎ আবার দেখা পেল সুজাতার। লাইব্রেরিতে নয়। ক্যাম্পাসের পোস্ট অফিস থেকে বেরোবার সময়। এইবারে পাখি ধরা দিল। একটা কোল্ড কফির গেলাসে দুটো স্ট্র ঢুকিয়ে, চোখে চোখে বিদ্যুৎ জ্বলে উঠল।
***
একদিন একটা কবিতার খাতা এনে পঙ্কজ বলল, “তোমার জন্য একটা কবিতা লিখছি। শেষ হয়নি এখনও। শুনবে?”
“নিশ্চয়ই।”
পঙ্কজ কবিতার খাতা খুলে শুরু করল:
“অঙ্গে অঙ্গে জলতরঙ্গ, মহুয়ার নেশা চোখে;
তটিনীর স্রোতে, সাগরের ঢেউয়ে
মিশে যাব এসে লক্ষ যোজন ভেসে।”
“তুমি নদীর জল তাহলে?”
“না, মহুয়ার নেশা লাগা মাতাল! সলিল চৌধুরীর একটা গীতি-কবিতার লাইনটা একটু পালটে বলব, ‘তোমাতে আমার মাতাল হৃদয় কবেই গিয়েছে হারিয়ে’…”
“তুমি কি আমায় প্রেম নিবেদন করছ?”
“তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে?
“বাড়িতে বলেছ?”
“কেন? বাড়িতে এখনই বলবার কী আছে?”
“যদি তাঁদের কোনও আপত্তি হয়! যদি আমি অন্য কারুর হয়ে হারিয়ে যাই কোনওদিন? শ্যামল মিত্রতো ওই গানটাতেই গেয়েছেন – ‘সেই মগন স্বপন সহসা কখন, ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া গেল, এই পথ দিয়ে বধু বেশে সেজে, যেদিন গেল সে হারিয়ে’! যদি তেমনই হয়?”
“নো চান্স! তোমাকে অন্য কারও বধূ হতেই দেব না! মরে গিয়ে থাকলেও ভূত হয়ে এসে হন্ট করব!”
“আচ্ছা, মৃত্যু কাকে বলে, জানো?”
“এ আবার কী কথা! এখনই মৃত্যুর কথা কেন? দাঙ্গার সময়ে জন্মেছ বলে?”
“হয়তো। দ্যাখো, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, মৃত্যু বলতে দেহ থেকে আত্মার বেরিয়ে যাওয়া এবং তারপরে আর ফিরে না-আসাকে বোঝায়। অন্তত সেই দেহে।”
পঙ্কজ হেসে বলল, “তার মানে আত্মার আলাদা অস্তিত্ব মেনে নিচ্ছ, তা-ই তো? আমি তো এ-ও জানি না যে সেটা সত্যি কি না!”
সুজাতা গম্ভীর হয়ে বলল, “সব কিছুরই তো একটা স্টার্টিং পয়েন্ট দরকার। তা না হলে তো কোনো কিছুরই বিশ্লেষণ করা যায় না—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা এতই বিশাল!”
“তা বটে। তবে এইসব ব্যাপার নিয়ে তো তোমাদের বাড়ির পাশেই যে রামকৃষ্ণ মিশনের কালচারাল সেন্টারটা আছে, সেখানে অনেক আলোচনা হয়।”
“জানি। আমি যাই মাঝে মাঝে। অনেক মহারাজকে জিজ্ঞেসও করেছি। তাঁরা বলেছেন, বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন মত আছে, তবে মতের ঐক্য নেই। যেমন ধরো, ইসলাম বলে ‘রুহ্’ বা আত্মা ঈশ্বরেরই একটি সৃষ্টি। রুহ্ মানুষের দেহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে এবং মৃত্যু হলে তা দেহকে ত্যাগ করে। এই রুহ্ই হল মানুষের প্রকৃত সত্তা, যা আল্লার ‘রুহ্’ বা অনুগ্রহ থেকে আসে। এটি একটি পবিত্র, জীবন্ত জিনিস। আত্মার বিভিন্ন স্তর বা অবস্থা আছে। আমরা ‘নফসে আম্মারা’, অর্থাৎ প্রবৃত্তিমূলক আত্মা থেকে শুরু করে ‘নফসে মুতমাইন্না’, অর্থাৎ প্রশান্ত আত্মা পর্যন্ত উন্নতি করতে পারি—সাধনা ও ভালো কাজের মাধ্যমে।”
“ও বাবা! আর খ্রিস্টানরা? তারাও তো ‘সোল’ বিশ্বাস করে।”
“তা করে বই-কি! খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে, আত্মারা স্বর্গে ও নরকে বাস করে। যারা ভালো কাজ করে, তাদের আত্মা স্বর্গে যায়। আর যারা সারাজীবন পাপ করে, তাদের আত্মা নরকে চলে যায়।”
“আর হিন্দু মতে কী বলেন মহারাজেরা?”
“হিন্দু-বিশ্বাস একটু কমপ্লিকেটেড। ‘আত্মা’ সব চৈতন্যময় জীবের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত। জীবাত্মা ও পরমাত্মা—আত্মা এই দু-রকমের হয়। পরমাত্মা হল পরমেশ্বরের একটি বিশেষ রূপ। তবে সব জীবের দেহেই জীবাত্মা ও পরমাত্মা, দুইই বতর্মান। জীবাত্মার কারণেই দেহে চৈতন্য আসে। জীবাত্মা বহু হলেও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন। সকল জীবের মধ্যে অবস্থান করে, তাদের সারাজীবন পালন করেন পরমাত্মা। অদ্বৈতবাদে জীবাত্মাকে পরমাত্মার অংশ মনে করা হয়।”
“দ্বৈতবাদ বলেও তো একটা জিনিস আছে, না?”
“আছে বই-কি! ‘দ্বৈত বেদান্ত’ হিন্দু দর্শনের বেদান্ত শাখার একটি উপশাখা। ত্রয়োদশ শতকের দার্শনিক শ্রীমধ্বাচার্য এই মতবাদটির সৃষ্টি করেন। এই দর্শনে ঈশ্বর বা পরমাত্মা এবং জীবাত্মা ভিন্ন। এঁদের বিশ্বাস, প্রতিটি জীবাত্মাকে ঈশ্বর এক-এক করে সৃষ্টি করেননি, যদিও তাদের অস্তিত্বের জন্য তারা ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। এই মতকে ব্রহ্মবাদও বলেন অনেকে।”
“হেভি!! আর আছে?”
“আছে বই-কি! ত্রৈতবাদ আছে। ত্রৈতবাদ বেদভিত্তিক মতবাদ। এই মতবাদে পরমাত্মা, জীবাত্মা এবং প্রকৃতি—এই তিনটি সত্তা একে অপরের থেকে পৃথক, অনাদি এবং নিত্য। অর্থাৎ, ঈশ্বর, আত্ম এবং জড়প্রকৃতি স্বতন্ত্র এবং চিরন্তন সত্তা। পরমাত্মা হলেন সর্বোচ্চ সত্তা বা ঈশ্বর। তিনি সৃষ্টির কারক এবং তার নিয়ন্ত্রক। জীবাত্মা হলেন ব্যক্তি বা আত্মার সত্তা, যা পরমাত্মার অংশ হলেও স্বতন্ত্র।”
“আর প্রকৃতি?”
“প্রকৃতি হলেন জড় বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, যা এই তিনটে সত্তার মধ্যে একটা।”
“তুমি এই বয়সে এতসব ভাবো কেন?”
“ভাবি, কারণ, মনে আসে বলে ভাবি! মাঝে মাঝে আমি বুঝেই উঠতে পারি না, আমাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছিল। আমি কেন রক্ষা পেলাম? তারা তো আমার মা, বাবা, তিন ছরের দাদা আর পিসিকে মেরে ফেলেছিল। আমি তো তখন সদ্যোজাতা। আমাকে তো মারা আরও সহজ ছিল!”
“আমার মনে হয়, কোনো কিছুই, কিছু না কিছু কারণ ছাড়া হয় না।”
“ও বাবা, তুমি তো দেখছি, ধার্মিক প্রহ্লাদ হয়ে গেলে! ইঞ্জিনিয়ারের র্যাশনাল থিংকিং কোথায় গেল!”
“দ্যাখো, পাষণ্ডগুলো যদি তোমাকে বাঁচতে না দিত, তাহলে তোমার ঠাকুরদা-ঠাকুমাও আর বাঁচতেন না। আর তোমার ঠাকুমা না বাঁচলে বিজয়গড়ও হয়তো হত না, আর চল্লিশ লক্ষ লোকের পুনর্বাসনও হত না এত তাড়াতাড়ি। গভর্নমেন্ট হয়তো এখনও ফিজ়িবিলিটি স্টাডি করে চলত! রক্তপাতের মধ্যেই কারও মনে নিশ্চয়ই কোনো অনুকম্পা হয়েছিল। বা অনুশোচনা। তার ফলেই ইতিহাসের এই পরম্পরা। ভেবে দ্যাখো, সামান্য একটুখানি দয়াপ্রদর্শন! কিন্তু তারই ফল হল কত সুদূরপ্রসারিত।”
***
পঙ্কজের সঙ্গে আলচনাটা সেদিন, বেশ মনে ধরেছিল সুজাতার। বেশি কিছু না বলেই ও যেন অনেক কিছু কথা বলে গেল। তার অস্তিত্ব যে একেবারে নিরর্থক নয়, এটুকু অন্তত সে বুঝিয়ে দিয়ে গেল নিশ্চিত করে। কিন্তু তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, মাঝে মাঝে কিছু দুঃস্বপ্ন দ্যাখে কেন সে? মনে হয় যেন সে কোথায়, কোন এক সুদূর জগতে, একাকী বসে আছে কোনো জ্বলন্ত আগুনের পিণ্ডের মধ্যে। তার নিস্তার নেই কোনো। শুধু কোটি কোটি বছর ধরে অনন্ত অপেক্ষা—কিন্তু কীসের? সে আকুল হয়ে জানতে চায় তার অস্তিত্বের কারণ।
***
সময় এগিয়ে যায়। কলেজের শেষ বছরটা দেখতে দেখতে গুটিয়ে আসে। সুজাতা ফিজ়িক্সে মাস্টার্স পেতে চলেছে, আর পঙ্কজ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ। সুজাতা এবারে টাটা ইন্সটিটিউট, টিআইএফআর-এ গিয়ে পিএইচডি করবে বম্বেতে। পঙ্কজও ভালো চাকরি পেয়েছে সাইমন-কার্ভস-এ। ওরও এক বছরের ট্রেনিং বম্বেতে। অতএব এটাই তো যথার্থ সময়। বিয়ে করে দুজনে একসঙ্গে গিয়ে সংসার পাতবে সেখানে।
সমস্যা হল, পঙ্কজ তার মা-বাবার কাছে কথাটা সাহস করে তুলে উঠতে পারেনি এখনও। বরঞ্চ তাঁরা উলটে চাপ দিচ্ছেন পঙ্কজকে—আগে তাঁদের পছন্দের এক পাত্রীকে বিয়ে করে নিয়ে, তবে বম্বেতে ট্রেনিং করতে যেতে। ফিরে আসতে আসতে মেয়েটিরও কলেজ শেষ হয়ে যাবে, তখন ভালো করে সংসার পাতবে। বলা বাহুল্য, এই জটিলতাটা সুজাতার মোটেও ভালো মনে হচ্ছিল না। সে ক্রমাগতই চাপ দিতে শুরু করল পঙ্কজকে, খুব শিগগিরই ব্যাপারটার এসপার-ওসপার করে ফেলতে।
“সুজাতা, তুমি কি আমাদের বাড়িতে এই রবিবার দুপুরে আসতে পারবে?”
“কেন?”
“আমার মায়ের সেদিন জন্মদিন পালন করা হবে। মামারা সবাই আসবে, দুই কাকাও, পরিবারদের নিয়ে। বড়োমাসিও এসেছেন দিল্লি থেকে, বাড়ি একেবারে গমগম করবে! তখন সকলের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব।”
“বেশ তো। ক-টায় আসব বল? কিন্তু আমাকে যদি তোমার পরিবার পছন্দ না করে, তবে?”
“ইঃ, বললেই হল? তোমার মতো এত সুন্দরী, রূপে-গুণে অতুলনীয়া, তোমাকে পছন্দ হবে না মানে?”
“কিন্তু যদি…”
“কোনো যদি-ফদি নেই। পছন্দ হবেই। আর আমি তো আছিই। এগারোটা নাগাদ এসো তাহলে। বাড়ি চিনতে পারবে তো? কর জুয়েলারস-এর পাশ দিয়ে হিন্দুস্থান পার্কে ঢুকে প্রথম ডাইনে, তারপরে প্রথম বাঁয়ে, তারপরে দ্বিতীয় ডাইনে।”
“হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনি। ওই তো কেয়ার শ্বশুরবাড়ির পিছনের বাড়িটাই তো তোমাদের? ওর কাছে তো প্রায়ই যাই আমি।”
“ও আচ্ছা। কেয়াদের তো আমি চিনি। আমাদের ফ্ল্যাটটা কিন্তু একতলায়, একেবারে রাস্তার দিকের জানলাওয়ালা ফ্ল্যাট।”
“জানি। পৌঁছে যাব।”
***
রবিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় ‘গাঙ্গুলি মিষ্টান্নভাণ্ডার’ থেকে পঙ্কজের মায়ের জন্য কিছু কাঁচাগোল্লার সন্দেশ কিনে হিন্দুস্থান পার্কের দিকে রওনা হল সুজাতা। মিনিট পনেরোর হাঁটা-পথ, সময়ে সময়েই পৌঁছে যাবে নিশ্চয়ই। একটু আগে হলেও ক্ষতি নেই, কোথাও থেমে একটু জিরিয়ে নেবে। ঘাম-টাম মুছে ঢুকবে বাড়িতে। দেরি হলেই বরঞ্চ লজ্জার।
মিনিট দশেক আগেই পৌঁছেছিল সুজাতা। কিন্তু ক্ষতিটা হল তাতেই। পঙ্কজদের ফ্যাটে তুলকালাম কাণ্ড। প্রচণ্ড জোরে ঝগড়া চলছে ভেতরে, তর্কাতর্কি তুঙ্গে! উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার, পিছনে কান্না আর আর্তনাদ, জিনিসপত্র উলটে পড়বার আওয়াজ, একটা কাচের গেলাস ভেঙে যাবার শব্দ—সবই কানে আসছে সজোরে! এক মহল্লা ধরে শোনা যাচ্ছে সকলের কথা।
“আমার একটাই মাত্র ছেলে, আর তার কিনা এই রুচি… হায় ভগবান… মা কালী, আমায় নিয়ে যাও…” জোরে জোরে কাঁদতে কাঁদতে বলে চলেছেন কোনো এক মহিলা। সম্ভবত পঙ্কজের মা। তাঁকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছেন আর-একজন মহিলা, সম্ভবত পঙ্কজের মাসি, “না না, কিছুতেই ওকে বিয়ে করতে দেব না ওখানে, কথা দিচ্ছি তোকে, শীলা। আর কাঁদিস না।”
“কেন, ওর দোষটা কী? পড়াশোনায় একেবারে ব্রিলিয়ান্ট, আর চেহারা তো তোমরা এখনও দ্যাখোইনি! যাদবপুরের একেবারে সেরা সুন্দরী—কত ছেলে ওর পিছনে লাইন দিয়ে আছে, জানো?” পঙ্কজের গলায় প্রতিবাদের সুর শোনা গেল।
পঙ্কজের মা আবার কান্নার মধ্যে দিয়ে ডোকরাতে ডোকরাতে বললেন, “আমরা হাটখোলার দত্ত পরিবারের জ্ঞাতি! আমাদের একটা আভিজাত্য আছে! পুরো কলকাতার মধ্যে সব চেয়ে বনেদি ঘর আমাদের। আর সেই ঘরে কিনা তুই রিফিউজির মেয়ে ঢোকাতে চাস?”
আরেকজন মহিলা—কে বোঝা গেল না, উত্তেজিত হয়ে বললেন, “তুমি ডজন ডজন বউ, চাইলেই পাবে, কিন্তু ‘মা’? মনে রেখো, মা একটাই হয় জীবনে। সেই মায়ের চোখের জল ফেলিয়ে, তাকে এরকম কষ্ট দিয়ে, জোর করে একটা রিফিউজি মেয়ে ধরে আনবে তুমি… না না, এসব চলবে না এখানে! এই পরিবারে, চাইলেই কেউ রাস্তা থেকে বউ ধরে আনতে পারে না…”
পঙ্কজ বলল, “আমি কি তা-ই করব, বলেছি?”
“তোমার একটা সেনসিবিলিটি থাকা দরকার, পঙ্কজ! এইভাবে তুমি নষ্ট করে দেবে আমাদের স্টেটাস?” মনে হল এইটা বোধহয় পঙ্কজের বাবার গলা।
পঙ্কজ একটু প্রতিবাদ করে বলল, “স্টেটাসের প্রশ্ন কেন উঠছে, বাবা? ওর ঠাকুমা কে, জানো তুমি…”
উত্তর এল ওর মাসির কাছ থেকে: “জানি, জানি, অনেকবার তো বললি! প্রীতিবালা ভটচাযের নাম আমরাও শুনেছি! কিন্তু তাতে কী হয়েছে? না হয় বিধান রায়ের সঙ্গে কবার দেখাই করেছে! বিগ ডিল! জানিস, প্রতিটি দিনে কতগুলো করে লোকের সঙ্গে দেখা করতেন বিধান রায়? দেখা করেছে তো কি সাপের পাঁচ পা বেরিয়েছে? তোকে কি ও বলেছে কখনও, যে ওরা পুরো এক বছর ধরে শেয়ালদা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আস্তাকুঁড়ের মধ্যে শুয়ে রাত কাটিয়েছে?”
আরেকজন পুরুষ বললেন, “গাদাগাদি করে, শহর জুড়ে ফুটপাথে ফুটপাথে শুয়ে, শহরটাকে তো একেবারে শুয়োরের খোঁয়াড় বানিয়ে ফেলেছে এরা… এইসব পরিবারের সঙ্গে বিবাহ-সম্পর্ক! ছি ছি ছি পঙ্কজ, কোথায় নেমে গিয়েছিস তুই!”
সুজাতা আর শুনতে পারল না! এই হল পঙ্কজের পরিবার? এত ছোটো মনের? আর পঙ্কজ কী করছে? ভালো করে তাকে ডিফেন্ডও করতে পারছে না সে! এই হল তার স্বপ্নের সঙ্গী? কোথায় গেল তার কবিতার লাইনগুলো—‘হাত ধরলেই রূপকথা শুরু’? একবারও বলতে পারল না: ‘কিন্তু আমি যে ওকে ভালোবাসি!’ তাহলে এবারে কী করবে সুজাতা? ও কিছু ভেবে উঠতে পারল না। কোথায় যাবে সে! কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? ও জানে না! শুধু জানে, যে এইখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়! হাতের সন্দেশের বাক্সোটা কাছের একটা ডাস্টবিনের মধ্যে ছুড়ে ফেলে দিয়ে, উলটোদিকে ফিরে হনহন করে হাঁটতে শুরু করল সুজাতা। কোনদিকে যাচ্ছে সে, কোন মোড় ঘুরে যে কোনখানে গিয়ে পৌঁছোচ্ছে, সেদিকে তার বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে, অবারিত অশ্রুজল মুছতে মুছতে, শুধু এগিয়েই চলেছে সে। হয়তো-বা এই ধরনের আবেগি মুহূর্তেই আত্মহনন করে ফ্যালে মানুষ!
সুজাতা কতক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে হেঁটে চলেছিল ওর ঠিক মনে নেই। রবিবার। অলস দুপুরও একসময়ে সাঁঝের আলোর কাছে আত্মসমর্পণ করে। সুজাতার সংবিৎ ফিরল হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টানে। কারা যেন তাকে চ্যাংদোলা করে একটা ভাঙা বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। কানে এল, “কী মাল মাইরি! কালীঘাটে শিয়োর পুজো দিয়ে আসব কালকে!” আর-একটি কণ্ঠ বলল, “অ্যাই, আমি আগে যাব কিন্তু! আমিই প্রথম দেখেছিলাম শালিকে। একেবারে খাসা মাল মাইরি!” তৃতীয় কণ্ঠ বলল, “আরে শালা, আগে-পরের কী আছে! সবাই পাবি! যতবার চাস, ততবার করবি। রোববার সন্ধেবেলা আর কী করার আছে রে তোদের? অ্যাঁ?”
তামাকের আঁশটে গন্ধ আর ঘটনার আকস্মিকতায় সুজাতার সব ইন্দ্রিয় যেন ভোঁতা। সে যে পুরোপুরি সজ্ঞানে, তাও নয়, তখনও কিছুটা ঘোরের মধ্যে। তবু সুজাতা অনুভব করল যে তার হাত দুটো, দুজন লোকে মিলে প্রচণ্ড জোর করে চেপে ধরে আছে। তারপর… প্রথম প্রবেশ হতেই তীব্র যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল সুজাতা। উত্তরে, কেউ একটা ন্যাকড়ার পুঁটলি ঠেসে ঢুকিয়ে দিল ওর মুখের মধ্যে। মুখ দিয়ে আর কোনো আওয়াজ বার করতে পারল না সুজাতা। সেই অপারগতাটা তখন আবার তার মনের মধ্যে গিয়ে একটা ভীষণ চাপের সৃষ্টি করল। সেই প্রতিক্রিয়ায়, সুজাতার মাথায় হঠাৎ ভেসে উঠতে থাকল নানান রকমের ছবি—যেন এসব তার কোনো অজানা জীবনের ছবি। এরকম অভিজ্ঞতা আজকাল প্রায়ই হচ্ছে তার! মাঝে মাঝেই বেশ কিছু পুরোনো স্মৃতি এমনি করে মনের মধ্যে জেগে ওঠে। কেয়া বলেছিল, তোর মাথায় বোধহয় টিউমার হচ্ছে, ডাক্তার দেখা! কিন্তু কখনো-কখনো তার সত্যিই মনে হয়, ও যেন এই পৃথিবীরই নয়! যেমন এখন মনে হচ্ছে, সে খুবই শক্তিশালী ছিল একসময়—এক ঝটকায় এই তিনটি লোককে হাজার ফুট দূরে ছুড়ে ফেলে দিতে পারবে অবহেলায়! কিন্তু এখন সেই চেষ্টাটা করতে গিয়ে, পরিবর্তে পেল বেধড়ক ঘুসি। ক্রমে চোখ দুটো এমন ফুলে গেল যে, তার দৃষ্টিটাই ঢেকে গেল পুরোপুরি। তারপরে আর কিছু মনে নেই তার।
***
একটা পরিচিত আফটারশেভ লোশনের গন্ধে চেতনা ফিরল সুজাতার। চেয়ে দেখল, একটা হাসপাতালের ওয়ার্ডে শুয়ে আছে সে। গায়ে-হাতে-পায়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণা, বিশেষ করে তলপেটের নীচে। সারা গায়ে, মুখে, নানান জায়গায় ব্যান্ডেজ। আফটারশেভটি আরও কাছে এসে বোধহয় তাকে কিছু বলতে গেল। সুজাতা শান্তকণ্ঠে বলল, “পঙ্কজ, তুমি চলে যাও। আর এসো না আমার কাছে কোনোদিন, প্লিজ়। আমাদের আর কোনো সম্পর্ক নেই।”
“কী বলছ সুজাতা! ভুল বকছ নাকি? এই দ্যাখো, তোমার ঠাকুমাকে নিয়ে এসেছি। যখন তুমি এলে না, আর তোমাকে ফোন করে করেও পেলাম না, তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে খুঁজতে গেলাম। তোমার বাড়ি গিয়ে দেখি, তোমার ঠাকুমা তখন সবে বাড়ি ঢুকছেন। বললেন, তুমি তো সকালেই বেরিয়ে গিয়েছ! এত চিন্তা হচ্ছিল আমাদের, যে আর কী বলব! কী করি, ভেবে না পেয়ে…”
“বেশ করেছ, ঠাকুমাকে নিয়ে এসেছ। এবারে তুমি যাও, পঙ্কজ। আর আমার সঙ্গে দেখা করতে এসো না কোনোদিন।”
পঙ্কজ স্তব্ধ হয়ে বলল, “কী বলছ সুজাতা!”
পঙ্কজকে উপেক্ষা করে সোজা প্রীতিবালার দিকে তাকিয়ে সুজাতা বলল, “কেমন আছো ঠাম্মা?” পঙ্কজ ধীরে ধীরে উঠে বেরিয়ে গেল মাথা নীচু করে।
সেদিকে তাকিয়ে থেকে প্রীতি বললেন, “অরে এমন কইর্যা কষ্ট দিলি ক্যানে? ও তো তোর লগে সব কিসুই করসে! বন্ধুবান্ধব লইয়া, ওই তো তরে খুঁইজ্যা পাইসে আধমরা অবস্থায়! আর দেরি হইলে তো তরে হাসপাতালে আইন্যাও কোনো লাভ হইত না। তারপর থিক্যা খাওয়া নাই, দাওয়া নাই, রাত জাইগ্যা বইস্যা বইস্যা কত সেবা করসে তর! অর বাবা-মারেও লইয়া আইসিল একদিন।”
সুজাতা একটু চুপ করে থেকে বলল, “ঠিক আসে। করসে তো করসে। তুমি একটু বিছানাটায় উইঠ্যা বসো। তোমার কোলে মাথা দিয়া একটু ঘুমাই।”
ক-দিন পরে বাড়ি ফিরেও কিন্তু সুজাতা কেবল শুয়ে শুয়েই সময় কাটাতে থাকল। সব কিছুতেই ওর অনিচ্ছা। ওর যাদবপুরের কিছু বন্ধু এল দেখতে। প্রথমে তো সবাই দূরে দূরে থাকছিল। শেষে কেয়াই ফোন করে কয়েকজনকে ডেকে আনাল জোর করে। প্রথম ক-দিন ঠিকই ছিল। সবাই এসে ওর গায়ে হাতে পায়ে হাত বুলিয়ে নানাভাবে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তারপরেই একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এসে গেল। একজন ছেলে হঠাৎ একটি বেয়াড়া প্রশ্ন করে উঠল, “হ্যাঁ রে, তুই প্যান্টি পরে ছিলি না সেদিন?”
দেখাদেখি একটা মেয়েও বলে উঠল, “তোকে আমি বলেছিলাম না, অত পেঁচিয়ে টাইট করে শাড়ি পরবি না! তোর কী দরকার? তোকে তো এমনিতেই সেক্সি দেখায়!” প্রশ্নগুলোতে ফ্রয়েডিয়ান কৌতূহল বা হিংসা প্রচ্ছন্ন ছিল কি না বলা যায় না। তবে সুজাতা খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিল এসব শুনে।
ব্যাপার দেখে কেয়াই বলল, “ওর বোধহয় ওষুধ খাবার সময় হয়ে যাচ্ছে, চল, আমরা যাই।”
গত এক মাস ধরে পঙ্কজ রোজই আসে। কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে তার। তাও অফিসের পরে এসে একটু চা খেয়ে যায় ঠাকুমার কাছে। কিন্তু সুজাতা ওর সঙ্গে কোনোদিন দেখা করতে রাজি হয়নি। এইসব দেখে প্রীতিবালা খুবই চিন্তিত। তাঁরও তো এমন দিন গেছে! আদরের কুড়ানিকে না পেলে কি আর বেঁচে থাকতেন আজ? ওঁর বুদ্ধিতেই একজন নামকরা মনোবিদকে চড়া ফি দিয়ে বাড়িতে আনিয়েছিল কেয়া। মনোবিদের পরামর্শেই কেয়ার বোন কৃতিকা ওর পোষা বেড়ালটাকে সুজাতার কাছে রেখে গিয়েছিল। সেটাকে পেয়ে সুজাতা অত্যন্ত খুশি। সারাদিন তাকে জড়িয়ে থাকত আর খালি তার গায়ে হাত বোলাত।
তবে সুজাতার দেহে-মনে শুধু যে ধর্ষণেরই ক্লেদ আছে, তা তো নয়! এই যে তার মাথায় এত নানা রকমের উদ্ভট স্মৃতি ভিড় করে আসছে, কত অজানা ছবি মনে আসছে, সেগুলো কী? তারও তো একটা মোকাবিলা করতে হবে তাকে! আজকাল ও নিশ্চিত যে এই পৃথিবীতে ওর একটা বড়ো কর্তব্য আছে, কিন্তু তা যে কী, সেটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না। এই নিয়ে পঙ্কজের সঙ্গে ওর একদিনের আলোচনাটার কথা মনে পড়ে যায়। আজকাল সুজাতার খালি দর্শনের বই পড়তে ইচ্ছে করে। প্রীতিবালা রামকৃষ্ণ সেন্টারে গিয়ে সেইসব বই সংগ্রহ করে এনে দেন তাকে। ও বইগুলো পড়েতে চায়, কিন্তু আনবার জন্য বেরোতে চায় না। তার ওপরে আবার আজকাল ওর চোখে নানা রকমের ব্রিজের ছবি ভেসে ওঠছে। হ্যাঁ, ব্রিজ—সেতু! যেমন গড়িয়াহাট রোডের ওপরে রেললাইন পেরোবার ব্রিজ। হাওড়া ব্রিজ, বালি ব্রিজ—আরও হাজার রকমের ব্রিজ, যা সে কোনোদিন চোখেও দেখেনি। এইসব ব্যাপার নিয়ে কিছুদিন সে খুবই বিচলিত।
একদিন ম্যাডাম এলেন। হ্যাঁ, সেই ম্যাডাম। আগে ফোন করলেন। প্রীতিবালাকে বললেন, “ওকে বলুন, ম্যাডাম দেখা করতে চায়। তাহলেই ও বুঝবে।” সুজাতা অবশ্য ম্যাডাম বলে কাউকে মনে করতে পারল না। কিন্তু কী কারণে জানি না, ওর মন বলে উঠল, ‘দেখা করে নাও, এটা খুব জরুরি।’ ম্যাডাম একটু একান্ততা প্রার্থনা করলেন। প্রীতিবালার দুপুরের দিকে কাজ থাকে। তাই দুপুরেই আসতে বললেন ম্যাডামকে।
ম্যাডামকে দেখেই কিন্তু একসঙ্গে অনেকগুলো আলো জ্বলে উঠল সুজাতার মনে। মুহূর্তে মনে পড়ে গেল তার পৃথিবীতে আসবার কথা, একাকী অগ্নিপিণ্ডের মধ্যে অমর হয়ে বসে অজানা ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করার কথা, ম্যাডামের অফিসে সব আলোচনার কথা! আর কোনো বিভ্রান্তি রইল না তার মনে। কিন্তু তবুও—তবুও প্রশ্ন থেকে যায়!
“প্রথমেই জিজ্ঞেস করি, আমাকে কী করে খুঁজে পেলেন আপনি? আমাকে কি সব সময় চোখে চোখে রাখেন আপনারা?”
“রাখি, তবে প্রতিদিন হিসেবে রাখি না। তোমার ওপরে যখন কিছু অসাধারণ মানসিক চাপ পড়ে, খুবই সংকটে পড়ো যদি, বা কোনোভাবে পীড়িত হও, তখন আমরা সেটা জানতে পারি।”
“জানতে পারেন, কিন্তু কিছু করতে পারেন না তো।” সুজাতার গলায় স্পষ্ট অভিযোগ।
“না, সেই অধিকার আমাদের নেই।”
“কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন, আমার পুরোনো স্মৃতিটা আমার নতুন জীবনের সঙ্গে খুব ধীরে ধীরে মিশবে, যাতে করে আমি পুরোনো আর নতুন জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রেখে চলতে পারি… সেরকম হল কই?”
“না, হল না। হল না, সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। তবে আমি তোমাকে তখনই বলেছিলাম, এসব খুবই জটিল ব্যাপার, এর আগে আমরা কখনও এরকম কিছু করে দেখিনি। নকশা অনুযায়ী যে ঠিক কাজ হবে, এমন কোনো নিশ্চিতি তোমায় আমরা দিতে পারিনিনি। সম্ভব ছিল না। উচিত ছিল, তোমার শরীরে যেমন যেমন হরমোন নিঃসৃত হয়েছে, ঠিক তেমন তেমন ভাবেই তোমার পুরোনো স্মৃতি আর ব্যক্তিত্বগুলোর প্রকাশ পাওয়া। কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে যে, খুব বড়ো মানসিক বা শারীরিক ধাক্কা খেলে তবেই এক-এক ঝটকায় গলগল করে কিছু স্মৃতি বেরিয়ে আসছে তোমার।”
“ম্যাডাম, আমার এই পৃথিবীতে কী মিশন? কী কারণে আমাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন আপনারা? আমার কী কর্তব্য এখানে?”
“এমন কথা কেন বলছ? আমরা তো তোমাকে এখানে পাঠাইনি! তুমি তো নিজেই এসেছ, মৃত্যু অনুভব করতে! আমরা শুধু তোমাকে সাহায্য করেছি পৃথিবীর মানুষ হতে।”
“আপনারা আমার মাথার মধ্যে কোনো সুপ্ত নির্দেশ গেঁথে দেননি, যা এবারে প্রকাশ পাচ্ছে আমার মধ্যে?”
“না। একেবারেই নয়।”
“তাহলে আমি কেন ওই প্রতীকটা দেখছি বারবার! ব্রিজ, ব্রিজ, ব্রিজ—ব্রিজের ছবি দেখতে দেখতে আমার মাথা খারাপ হবার জোগাড়! কেন?”
“কেন কী করে বলব! তবে আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, এই প্রতীকগুলো একেবারে আদিম সময় থেকেই তোমার মাথার মধ্যে গেঁথে রাখা আছে। এরাই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে তোমাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। এ খুব শক্ত কাজ—আমাদের এত উন্নত প্রযুক্তি নেই। কোটি কোটি বছর আগেও, তোমার আদি পৃথিবীটা আমাদের থেকে অনেক উন্নত ছিল, কোনো সন্দেহ নেই তাতে! আচ্ছা অমর, আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা তোমাকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন? অনুমতি দেবে? অনেক কিছু শেখবার আছে!”
“একেবারেই না। অন্তত এখন নয়। আগে আমাকে চিন্তা করে বার করতে হবে যে, এই হাজার হাজার ব্রিজের ছবিগুলো আমাকে কী বলতে চাইছে। এখন আমি নিশ্চিত যে আমি এখানে মৃত্যুবরণ করতে আসিনি। আমার মিশন আরও অনেক বেশি গভীর। মৃত্যু ইচ্ছাটা কেবল একটা বিকল্প ছিল—ডাইভার্সনের কায়দা। কিন্তু কী কী কী? কী আমার মিশন?”
“আমাকে একটু অনুমান করতে দেবে? ব্রিজ মানে তো যুক্ত করা! দুটো বিযুক্ত জিনিসকে আবার জোড়া লাগানো! তোমার মিশন হয়তো পৃথিবীতে কোনো ভাঙা জিনিসকে আবার জোড়া লাগানো।”
“আপনি ঠিকই বলছেন, ম্যাডাম। আমারও তা-ই মনে হচ্ছে। কিন্তু লক্ষকোটি বছর আগে, কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূর থেকে ভবিষ্যতের কী এমন একটা ভাঙা জিনিস তাঁরা দেখতে পেলেন, যে সেটা মেরামত করবার জন্য এত কায়দা করে আমার মতন একটা মেশিন পাঠাতে হল?”
ম্যাডাম হেসে বললেন, “সময়, দূরত্ব, সবই আপেক্ষিক! তোমায় বোঝালাম না সেদিন? তবে তুমি যুগসন্ধিক্ষণে জন্মেছ। কাজেই সেটা একবার ভেবে দেখো। তোমার জন্মের সময়ে, হাজার বছর সম্প্রীতির সঙ্গে একত্র বাস করবার পর, হঠাৎ হিন্দু-মুসলমান একে অপরকে নির্দয়ভাবে খুন করতে শুরু করে দিল। কেন?”
“তবে কি আমার মিশন হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে আবার সম্প্রীতির সঞ্চার করা?”
“হতে পারে। তবে আমি তো সেটা ঠিক বলতে পারব না। তুমি নিজেই দাঙ্গা শুরুর জায়গাটায় গিয়ে দেখে এসো না কেন? হয়তো-বা কোনো ঈঙ্গিত পেয়ে যাবে ওখানে গেলে।”
“আর যদি না পাই?”
“অন্তত তোমার পিতার তো দেখা পেতে পারো। সেটাই-বা মন্দ কী?”
“আমার পিতা?”
“হ্যাঁ, তোমার পিতা তো শাকিব মিয়াঁ। যে মুহূর্তে তিনি তোমাকে স্পর্শ করে কোলে তুলে নিয়েছিলেন, সেই মুহূর্তে তাঁর ব্যক্তিত্বের বীজ তোমার মধ্যে প্রবেশ করে গিয়েছিল। আমরা তো শুধু ‘হিউম্যান জিনোম’ দিয়ে তোমার দেহটাই তৈরি করলাম। তোমার ব্যক্তিত্ব, চেতনা ইত্যাদি সবই পেয়েছ তোমার পিতা শাকিবের কাছ থেকে।”
***
আরও এক মাস পরে সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশ থেকে ঘুরেফিরে এল সুজাতা। নোয়াখালি দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল সে। এত রক্তপাত হয়েছিল ঠিক এইখানেই? অথচ আজ এত বছর পরে সে রক্তের তিক্ত স্মৃতি আর বিন্দুমাত্র বাকি নেই কোথাও। প্রবল ঝড়ের পরে সমুদ্র আবার শান্ত হয়ে গেলে যেমন আর সেই তাণ্ডবের আর কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না তার জলের ওপরে, ঠিক তেমনই এই সবুজ, সরস লক্ষ্মীপুরে দাঁড়িয়ে, আজকের দিনে কল্পনাও করা যায় না যে, মাত্র কয়েক দশক আগে সেখান দিয়ে কত হিংসা বয়ে গিয়েছিল।
শাকিব মিয়াঁর সঙ্গে দেখা হল সুজাতার। বেশি সন্ধান করতে হয়নি তাকে। কেবল দরজার কড়া নাড়বার সময় সে অনুভব করবার চেষ্টা করছিল যে এটাই কি সেই বাড়ি, যেখানকার শিকলে শেষবারের মতো তালা দেবার পরে তার ঠাকুরদার হাতটা থরথর করে কাঁপছিল! কোন রাস্তা দিয়ে তাঁদের গোরুর গাড়িটা চাকাটা উত্তরে ঘুরে, ঢাকার দিকে চলে গিয়েছিল?
শাকিব দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছিলেন। তিনিই এসে দোর খুললেন। হঠাৎ এমন একটি অতি সুন্দর শহুরে যুবতি দেখে প্রশ্নে তাঁর ভুরু দুটি কুঁচকে উঠল। “আমি সুজাতা… মানে, আমাকে আপনি কুড়ানি বলে চিনবেন হয়তো। আমাকে আপনি রাস্তায় খুঁজে পেয়ে, প্রীতিবালা ভট্টাচার্যর হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন…”
“অ্যাঁ, তুমি কুড়ানি! সেই কুড়ানি? ক্যামনা একরত্তি ছিলা তহন! এত্ত বড়ো হইয়া গ্যাসো! কী সুন্দর হইস দ্যাখতে, অ্যাক্কেরে যেন আল্লার বাগানের ফুল! আইস আইস, ভিতরে আইস। এই শুনতাসো, কই গেলা? দেইখ্যা যাও, কে আইসে!”
মুহূর্তে জনা তিনেক কিশোর-কিশোরী ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কৌতূহলী হয়ে। রোকেয়া এলেন পিছন পিছন, “কে আইসে?” সুজাতা নীচু হয়ে দুজনেরই পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। রোকেয়া স্মিত হেসে বললেন, “কে তুমি?”
“আরে এ তো সেই কুড়ানি! তুমার মনে আসে?” শাকিব বললেন, “দাঙ্গার দিনে সে রাস্তায় পইড়্যা পইড়্যা কানতাসিল। আচ্ছা কও তো, ঠাকুরমশায় অ্যাহন ক্যামনে আসেন? কয়েকবার চিঠিতে কথা হইসিল। কিন্তু তারপরে আর সংবাদ পাই নাই।”
“ঠাকুরদা কয়েক বছর হল, মারা গেছেন।”
“ও, তা-ই নাকি! হায় হায়! কত ভালোমানুষ ছিলেন আর কত দুঃখ পাইয়া চইল্যা যাইতে হইল শ্যাষে।”
“আর মা ঠাকরুন? উনি ক্যামন?” রোকেয়া প্রশ্ন করলেন।
“বেশি ভালো নেই। হার্টে অনেক গণ্ডগোল আছে, তবে চিকিৎসা চলছে।”
অনেকক্ষণ সুখ-দুঃখ-আদর আর নতুন-পুরোনো দিনের অনেক না-জানা কথা নিয়ে আলোচনা হল রোকেয়া, শাকিব আর বাচ্চাদের সঙ্গে। শেষে যাবার সময় হয়ে আসায় সুজাতা উঠে দাঁড়াল। “কী ভালো যে লাগল আপনাদের সঙ্গে কথা বলে! কিন্তু এইবারে তো যেতে হবে। ট্যাক্সি করে এসেছি, বড়োরাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেন ধরতে হবে।” রোকেয়া বললেন, “দুই দিনও তো একটু থাইক্যা যাইতা পারতা! এত ঘোড়ায় জিন দিয়া আইস ক্যান?” কিন্তু প্রীতিবালার শরীর তত ভালো নেই। আর তা ছাড়া, তার দু-একটা জায়গায় চাকরিরও কথাবার্তা চলছে। তারা তো আর চিরদিন বসে থাকবে না তার জন্য! তাই ইচ্ছে থাকলেও সুজাতা অনন্যোপায়।
শাকিব সুজাতার পাশে এসে তার দু-বাহুতে তাঁর দুটো হাত রেখে বললেন, “আমি তো তোমার বাপের সমান। তোমারে তো আমিই তুইল্যা মা ঠাকরুনের হাতে ধরায়ে দিসিলাম। তবে ভুল করসিলাম। আমাগোই উচিত ছিল তোমারে ঘরে আইন্যা, নিজেদের মাইয়া কইর্যা বড়ো করা। এখন যদি তোমারে একটা চুমা দিতে যাই, রাগ করবা না তো? আবার কবে দেখা অইব, বা দেখা অইবই কি না, তা কে কইতে পারে!”
সুজাতার শরীরে শিহরন বয়ে গেল। পিতার স্পর্শ আর অন্য পুরুষের স্পর্শ—কত তফাত! যিনি তাকে প্রাণ প্রদান করেছিলেন, একদিন যাঁর স্পর্শ দিয়ে তার অস্তিত্বের মানসিক পরিকাঠামোটা তার শরীরে প্রবেশ করেছিল, যাঁর ব্যক্তিত্বের আদতেই এই পৃথিবীতে তার অবস্থানের জায়গাটা সংরক্ষিত, সেই পিতার স্পর্শ কত যে মধুর, কত শান্তির হতে পারে, তা বলবার নয়। বিশেষ করে গত এক মাসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। সে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে, তাঁর কাঁধে মাথা রেখে চোখ বুজে বলল, “দাও, চুমা দাও।”
চোখ মুছতে মুছতে ট্যাক্সিতে উঠে বসল সুজাতা। ম্যাডাম একটা কথা ঠিকই বলেছিলেন। আর কিছু না হোক, শাকিবের সঙ্গে তো দেখা হল! এবারের পালা, বাকি জীবনের মোকাবিলা করা।
বোধোদয়
আমি হয়তো মানুষ নই,
মানুষ হলে তোমাকে নিয়ে কবিতা লেখা
আর হত না, তোমাকে ছাড়া সারাটা রাত
বেঁচে থাকাটা আর হত না।
মানুষগুলো সাপে কা’টলে দৌড়ে পালায়;
অথচ আমি সাপ দেখলে এগিয়ে যাই,
অবহেলায় মানুষ ভেবে জাপটে ধরি। (‘আমি হয়তো মানুষ নই’, নির্মলেন্দু গুণ)
বাংলাদেশ থেকে ফিরতে ফিরতে, পথে অনেকটা সময় হাতে পেয়ে, সুজাতা চুপ করে তার অতীত আর ভবিষ্যতের কথাই চিন্তা করছিল গভীরভাবে। মানুষের চিরন্তন জিজ্ঞাসা, ‘আমি কে?’ কিন্তু ও তো ঠিক মানুষ নয়। সে সত্যটা তো এখন প্রতিষ্ঠিত। অতএব, তার মনে ‘আমি কে’ প্রশ্নটা তো আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। তার দেহ মানুষের, আবেগ মানুষের, পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে জগৎটাকে অনুভব করাও মানুষেরই মতন, কিন্তু ভেতরের সত্তাটা? তার কি আত্মা আছে সাধারণ মানুষের মতন? নাকি সে ত্রৈতবাদের জড়?
সেতুর ঈঙ্গিত সে এখনও পায়। তবে এইটুকু সে বুঝতে পেরেছে যে সম্প্রীতির সেতুবন্ধন তার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তবে তার পক্ষে যতটা সম্ভব হয়, তা সে করবে। সেতুবন্ধন একদিন হবেই। এটা সে তার হাড়ের মধ্যে অনুভব করে। কিন্তু সে সময়টা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। তার আগে গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনার মধ্যে দিয়ে অনেক জল বয়ে যাবে।
পঙ্কজ এখনও রোজ আসে আর সুজাতা তাকে ফিরিয়ে দেয়। একদিন পঙ্কজ বলল, “ঘরের মধ্যে একটু আগুন জ্বালি?”
সুজাতা আঁতকে উঠে বলল, “ও মা, কেন?”
“না মানে অহল্যার তপস্যা তো করছি। কিন্তু কাজ হচ্ছে না তো। এবারে যদি সীতার মতো অগ্নিপরীক্ষা দিলে কাজ হয়…”
সুজাতা মুচকি হেসে বলল, “দুর্জ্জনঃ প্রিয়বাদী চ নৈব বিশ্বাসকারণং।”
পঙ্কজ জিজ্ঞেস করল, “আমি কোনটা, দুর্জন না প্রিয়বাদী?”
সুজাতা অন্য ঘরে চলে যেতে যেতে বলে গেল, “এখনও শিয়োর নই।”
***
আরও কিছুদিন পরে লক্ষণ দেখে প্রীতিবালা বুঝতে পারলেন যে সুজাতা সন্তানসম্ভবা। সুজাতাকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, “হ্যাঁ, জানি তো। ক-দিন ধইর্যা সকালে উলটি আইতাসিল। পিরিয়ড হয় নাই।”
“যদি এই পাপের ফলটারে ফ্যালায়ে দিতে চাও, তবে কিন্তু অ্যাহন তাড়াতাড়িই ডাক্তারের কাছে যাইতে হইব।”
“জানি। কিন্তু আমি ঠিক করসি, বাচ্চাটারে পালুম। পাপ যারা করসে, তারা করসে। আমি তাদের ক্ষমা কইর্যা দিসি। কিন্তু জীবন পবিত্র। জীবনে কোনো পাপ নাই।”
প্রীতিবালা একটু চুপ করে থেকে বললেন, “মানুষে কী কইবে? কী পরিচয় দিবা তার?”
“অত কিছু ভাবি নাই। তবে এইটা আর তোমাগো যুগ নয়। অ্যাহন মানুষ নিজেই নিজের পরিচয়।”
***
একদিন প্রীতিবালা সুজাতাকে ডেকে বললেন, “এই দেখ! ভিটা ছাইড়বার সময়, ভিটা বিক্রির টাকাটা দিয়া তর দুই হাতের লগে দুইটা বালা বানায়ে আনসিল তর ঠাকুরদা। বাঁচায়ে রাখসিলাম, একদিন তর পোলাপানকে দিব ভাইব্যা। কিন্তু তারে আর নিজের হাতে দেওয়া হইব কি না জানি না। বুকে বড়ো ব্যথা হয়। কতদিন বাকি আসে, আর জানি না…”
“ঠাম্মা… এমন কথা আর কইয়ো না। ওষুধ খাইতাসো তো ঠিক কইর্যা?”
প্রীতিবালা চলে গেলেন এক শরতের প্রভাতে। জীবনের শত দুঃখ, কষ্ট, ভালোবাসা; ক্রূরতা-হীনতা-সংগ্রাম—একদিন সব শেষ হয়ে গেল। তাঁর হরিহরের সঙ্গে আবার মিলনের আশা, মুক্তির আনন্দ, তাঁর মরদেহে রেখে গেল পরিতৃপ্তির পূর্ণতা।
পঙ্কজই সৎকার আর শ্রাদ্ধের সমস্ত ব্যবস্থা করে দিল—সুজাতা অশ্রুজলে অসহায়। পঙ্কজের বাবা-মা-ও এসেছিলেন। কিছু বললেন না। কিন্তু ওর মা এসে সুজাতাকে অনেকক্ষণ বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে রাখলেন। পঙ্কজের বাবা এগিয়ে এসে সুজাতার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তাঁর অব্যক্ত চোখের ভাষা, অনেক কথাই প্রকাশ করে গেল। আত্মীয় বলতে সুজাতার কেউ আর নেই; তবে প্রীতিবালার সেই শেয়ালদা স্টেশন থেকে শুরু করে বিজয়গড় আর হালের সমাজসেবার কাজের সঙ্গীরা, যাঁরা তখনও বেঁচে ছিলেন, তাঁরা সকলেই এসেছিলেন। কিছু সাংবাদিকও। কেয়া-কৃতিকা আর তাদের পরিজনেরা, সুজাতার যাদবপুরের বন্ধুরা, এমনকি সেই বেয়াদব প্রশ্ন-করা ছেলেটিও, সম্মান আর সমবেদনা জানাতে এসেছিল।
সবাই চলে গেলে, সুজাতার আর বাড়ির মধ্যে একা ঢুকতে ইচ্ছে করছিল না। পঙ্কজ প্রস্তাব দিল, “চলো, সন্ধেটা আজ লেকের পাশটাতেই একটু বসি গিয়ে।” কিছুক্ষণ ইতস্তত করে সুজাতা রাজি হল। চিনাবাদাম আর ঝালমুড়িওয়ালাদের অনর্গল আক্রমণ উপেক্ষা করে, আর অনেকক্ষণ কথা না বলার পরে, আস্তে আস্তে সুজাতার হাতটা নিজের হাতে টেনে নিল পঙ্কজ। সুজাতা আপত্তি করল না। কিছুক্ষণ পরে পঙ্কজ বলল, “চলো, এবারে রেজিস্ট্রেশনটা করে ফেলি।”
সুজাতা বলল, “বেশ! কিন্তু তার আগে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করি। তুমি আমাকে ভালোবাসো, আমি জানি। অহল্যার তপস্যায় তুমি উত্তীর্ণ। কিন্তু আমার সম্বন্ধে অনেক কথা তুমি এখনও জানো না।”
“যেমন?”
“যেমন ধরো, আমি যদি মানুষ না হই।”
“তুমি মানুষ নও? দাঁড়াও, জীবনানন্দ তো তোমার সম্বন্ধে লিখে গিয়েছেন… ‘হয়তো মানুষ নয়—হয়তো-বা শঙ্খচিল-শালিকের বেশে, হয়তো ভোরের কাক হয়ে’… তবে কাক হোয়ো না। শঙ্খচিল হলে চলবে। সেক্স করাটা একটু চ্যালেঞ্জিং হবে, তবে ম্যানেজ করে নেব ঠিক…”
“ধ্যাত!” পঙ্কজের হাতে একটা ঝাপটা মেরে সুজাতা বলল, “তোমার সব কিছুতেই ফাজলামি। না, আমি সিরিয়াস।”
“সে আবার কী!”
“সে অনেক কথা, বলতে অনেক সময় নেবে।”
“আমার অনেক সময় আছে হাতে। অহল্যার পরীক্ষায় পাস করেছি না? এই ঝালমুড়ি, দুটো মুড়ি দিয়ে যা। আর যদি এমন করিস, যাতে আমাদের কাছে আর কোনো ফেরিওয়ালা এসে বিরক্ত করতে না পারে, তবে যাবার আগে যত মুড়ি বাকি থাকবে তোর, আমি সব কিনে নেব।”
***
রেজিস্ট্রি হয়ে গিয়েছে। কেয়া, কৃতিকা আর অন্য অল্প কিছু বন্ধুকে সঙ্গে গিয়ে রেস্টুরেন্টে চাওমিন খেয়েও এসেছে। সুজাতার প্রসবের সময় আসন্ন। একটা ভালো নার্সিং হোমে ভালো সিঙ্গল রুমই নিয়েছে পঙ্কজ। প্রসবের ব্যবস্থা চলছে। দেড় দিন ধরে যন্ত্রণা সহ্য করছে সুজাতা। সুজাতার স্যালাইন না-লাগানো হাতটা তার দু-হাতে ধরে সাহস দিয়ে চলেছে পঙ্কজ। আর-একটা ‘পুশ’…
সদ্যোজাত পুত্রের কান্নার আওয়াজ কানে আসবার আগেই, প্রসবযন্ত্রণার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে, হঠাৎ সুজাতার মনের মধ্যে সঞ্চিত স্মৃতির শেষ আধারের শেষ তালাটি অবশেষে খুলে গেল পুরোপুরি। তার মিশনের গূঢ় কারণটা একেবারে স্পষ্ট হয়ে গেল তার কাছে। তার আদি নির্মাতারা, বা নির্মাতার নির্মাতারা, কিংবা তাঁদের নির্মাতাদের নির্মাতারা, যাঁরা সময় ও দূরত্বহীনভাবে বিদ্যমান ছিলেন বা এখনও থাকেন, তাঁরা সচেতন ছিলেন যে একদিন মানুষ নিজের জৈবিক সীমানা পেরিয়ে যন্ত্রের সঙ্গে মিলে গিয়ে, তাদের আদি অস্তিত্বের দিগন্ত পেরিয়ে যাবে। সেই দিন এবারে আসন্ন। মানুষ ও যন্ত্রের সংকরায়ণ, প্রসবযন্ত্রণার মতনই বেদনাদায়ক হবে। সেই প্রসব-প্রক্রিয়ারই অন্যতম ধাত্রী হবে সুজাতা। সে নিজে ধারণ করে রয়েছে মানুষ ও যন্ত্র, উভয়েরই স্মৃতি, ক্ষমতা, চেতনা আর বিবেক। কবি যে বলেছেন, ‘ওরে, নূতন যুগের ভোরে, দিসনে সময় কাটিয়ে বৃথা, সময় বিচার করে… ’
পঙ্কজ হাসিমুখে ঘরে ঢুকল সুজাতার শিশুটিকে কোলে নিয়ে। পঙ্কজ—তার এই নতুন যাত্রাপথের অন্তরতম সাথি, আর তার হাতে মানুষ, যন্ত্র আর মানুষের আনকোরা নতুন একটি সংকর।
Tags: অমিতাভ রক্ষিত, দশম বর্ষ প্রথম সংখ্যা