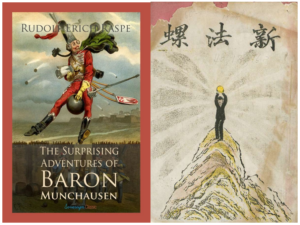ঘনাদা কি মিস্টার ফালুও না কং ইজি? — প্রেমেন্দ্র মিত্রের “ঘনাদা” সিরিজ পরিচিতি
লেখক: ইয়াং ফেং (আর্থার লিউ) অনুবাদ: রাকেশকুমার দাস
শিল্পী: টিম কল্পবিশ্ব
চেংদু সায়েন্স ফিকশন কনভেনশনে উপহার পাওয়া শেষ বিদেশি বই ছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের বইটি। পাশাপাশি কনফারেন্সে ভারতীয় সায়েন্স ফিকশন নিয়ে দীপ ঘোষের উপস্থাপনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। সেই সময় আমার ধারণা ছিল যে এই “ঘনাদা” চরিত্রটি হল ব্যারন মুনচাউসেনের মতো একজন ব্যক্তি (যাকে “ফালুও জিয়াংশেং” বা “দ্য বিগ টকার”নামেও ডাকা হয়), যিনি আপাতদৃষ্টিতে সারা বিশ্ব পরিভ্রমণ করতেন এবং অকল্পনীয় সব কাণ্ডে সামিল হতেন। কিন্তু তার গল্পগুলি এতটাই আজগুবি ছিল যে সেগুলো সত্যি বলে মেনে নেওয়া যেত না।
কিন্তু তার গল্পগুলো পড়ার পর আমার মনে হচ্ছে তিনি মিস্টার ফালুওর থেকে বেশ আলাদা।
আমার মনে হয়, ভারতীয় বিজ্ঞান কল্পকাহিনি এখনও চিনা পাঠকদের কাছে তুলনামূলকভাবে অপরিচিত। অতএব, এখানে লেখকের একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা দেওয়া যাক। প্রেমেন্দ্র মিত্র একজন ভারতীয় কবি, লেখক এবং চলচ্চিত্র পরিচালক, যিনি বাংলা ভাষার সায়েন্স ফিকশনের অন্যতম পথিকৃৎ। এখানে আমি “ভারতীয় সায়েন্স ফিকশন”না বলে “বাংলা সায়েন্স ফিকশন” বলছি, তার কারণ ভারতে বহু ভাষা প্রচলিত রয়েছে, ভাষাভেদে পাঠকমহলও আলাদা আলাদা, ফলে সায়েন্স ফিকশনও প্রায়শই ভাষাভিত্তিক আলাদা আলাদা বৃত্তে গড়ে উঠেছে। দীপ ঘোষও তার বক্তৃতায় এ বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন।
প্রেমেন্দ্র মিত্র একক অভিভাবকের পরিবারে বেড়ে ওঠেন। তাঁর মা অল্প বয়সে মারা যান এবং তিনি তাঁর ঠাকুরদা-ঠাকুমার কাছে তিনি লালিত-পালিত হন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন রেলওয়ের কেরানি, যার ফলে তিনি সারা ভারত জুড়ে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করার সুযোগ পান। ঔপনিবেশিক যুগে, তিনি বিভিন্ন স্কুলে পড়াশোনা করেন, খুব অল্প বয়সেই উচ্চ বিদ্যালয় থেকে পাশ করেন এবং কৃষি বিষয়ে পড়াশোনা করার জন্য একটি মিশন স্কুলে ভরতি হন। পরে সে বিষয়ে আগ্রহী হারিয়ে তিনি বিষয় বদল করেন, সম্ভবত সাহিত্য বা লোকসাহিত্য নিয়ে তিনি স্নাতক পর্যায়ের পড়াশোনা শুরু করেন। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে, এটি তুলনামূলকভাবে একটি স্বচ্ছল পরিবারের ইঙ্গিত দেয়। তাঁর পরিবার স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী ছিল, তাই এমন উচ্চশিক্ষা সম্ভবপর হয়েছিল।

তাঁর সাহিত্যকর্মের সূচনা হয় বিদ্যালয়ে পড়াকালীনই এবং ১৯ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি সাহিত্য জগতে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ভ্রমণ এবং শিক্ষা উভয়ক্ষেত্রেই তাঁর বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা তাঁকে সেই সময়ের সমাজ সম্পর্কে আরও বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে সাহায্য করে, যা তিনি তাঁর লেখার বিষয়বস্তুতে পরিণত করেন। দ্য এনসাইক্লোপিডিয়া অব বেঙ্গল তাঁর লেখার ধরণকে নিম্নরূপে বিবৃত করে:
“… তিনি এই চিন্তাধারাগুলি দরিদ্র শ্রমজীবী শ্রেণীর প্রতি প্রবল সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন, আর সেগুলি তিনি তাঁর স্বদেশীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োগ করেছিলেন… তাঁর উপন্যাসগুলি বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে, সমাজের নানা বিড়ম্বনা ও ভণ্ডামির সমালোচনা তাঁর রচনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য… তিনি তাঁর প্রজন্মের সবচেয়ে অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ এবং প্রভাবশালী লেখক। তিনি নগর জীবনের অন্ধকার, অন্তহীন অসারতা, জীবনের আত্মঘাতী প্রকৃতি নিজে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তাঁর উপন্যাসগুলিতে সেগুলি চিত্রিত করেছিলেন…”
এভাবেই তিনি বৃহত্তর সাহিত্যক্ষেত্রে তার অবদান রেখে গেছেন। সায়েন্স ফিকশন লেখার জন্য তাঁর প্রেরণাও এই চিন্তা থেকেই এসেছে, সেটি হল তরুণদের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ জাগানো। ভারতের উপনিবেশ থেকে স্বাধীন দেশে রূপান্তরের সময়কালে লেখালেখি করা একজন সায়েন্স ফিকশন লেখকের জন্য এই ধরনের আকাঙ্খা খুবই স্বাভাবিক। আমাদের দেশেও অনুরূপ সময়ে (“সতেরো বছরের সময়কাল”) বিজ্ঞানমনস্ক সাহিত্য একই উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল।
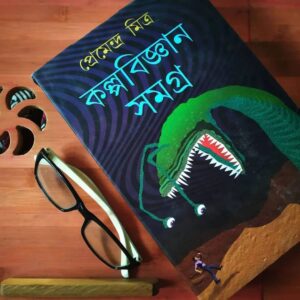
ঔপনিবেশিক আমলের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল, যা সম্ভবত ঔপনিবেশিক সংস্কৃতিরই একটি দান বলা যায়, তা হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশভুক্ত অঞ্চলের মধ্যে আন্তর্জাতিক ভ্রমণ ভারতের উচ্চবিত্ত শ্রেণির জন্য তুলনামূলকভাবে অনেক স্বাচ্ছন্দ্যের ছিল। এতে ‘বিশ্বজনীন ভারতীয়’ পরিচয়ের একটি বাস্তবসম্মত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা পায়। এ নিয়ে আলোচনা ভারতের স্বাধীনতার পরেও অব্যাহত ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘দ্য কাবুলাইটস/ কাবুলিওয়ালা’ (১৯৫৭ সালে চলচ্চিত্রায়িত) এর একটি আদর্শ উদাহরণ, যেখানে ভারতীয় এবং আফগানদের মধ্যে যোগাযোগ তুলে ধরা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত প্রেমেন্দ্র মিত্রও তার উপন্যাসগুলিতে এই বিষয়টিকে তুলে ধরেছেন। এটিই ঘনাদার গল্পগুলিকে বোঝার মূল ভিত্তি। তাহলে, ঘনাদা কে ছিলেন? সংক্ষেপে বলতে গেলে, তিনি একজন সত্যিকারের বিশ্বভ্রমণকারী অভিযাত্রী, প্রকৃতিবাদী এবং একজন আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী নাৎসিবিরোধী যোদ্ধা। মিস্টার ফালুও-র মতো নিছক গুলবাজের চেয়ে ঘনাদাকে বরং হ্যাল রজার ব্রাদার্স, ইন্ডিয়ানা জোন্স এবং জেমস বন্ডের একটি মিশ্রণ বলা যায়। এদের গল্পের সঙ্গে ঘনাদার গল্পের খুব মিল পাওয়া যায়। যেমন বিশ্ব জুড়ে নাৎসি আর উন্মাদ বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার লড়াই এবং তাদেরকে ছাপিয়ে যাওয়া, বা এভারেস্টের চূড়ায় তুষারমানবের সঙ্গে ল্যাসো স্কিইং খেলা। কখনও ঘনাদাকে দেখা যায় একটি আগ্নেয়গিরির হ্রদে হীরা খনন করছেন, কখনও তিনি তিব্বতে ভারী জলের হ্রদ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, বা ভিনগ্রহীদের UFO চুরি করছেন। এমনকী একটি ওয়ার্মহোলের মধ্য দিয়ে তিনি মঙ্গলগ্রহেও পৌঁছে গেছেন।
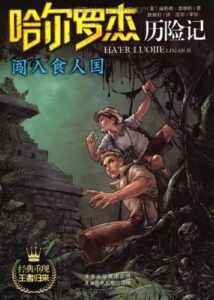
তার দুঃসাহসিক অভিযানের গল্পগুলিতে ঔপনিবেশিক ভারতের চিত্র প্রায় অনুপস্থিত। তবে এই অনুপস্থিতি একটি বিপরীত ধারণা তৈরি করে যে ভারতীয়রাও বিশ্বব্যাপী অভিযানে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে, তারাও শ্বেতাঙ্গদের সমস্ত কার্যকলাপে জড়িত হতে পারে, এমনকী অন্যান্য দেশে বিরল প্রাণী শিকারের জন্য তাদের নিজস্ব দালাল এবং ভৃত্যও নিয়োগ করতে পারে। শুধুমাত্র অভিযানের বৈজ্ঞানিক উপাদানগুলি নয়, এই আন্তর্জাতিক অভিযানকারীর নিজের ভাবমূর্তিটিও অনন্য বিস্ময়ের উৎস হয়ে ওঠে। তবুও, নিজের পরিচয় প্রকাশ করার আগে বা তার ‘ব্যক্তিগত আকর্ষণ’ (প্রায়শই সেটা শারীরিক দক্ষতা) দিয়ে প্রতিপক্ষকে মুগ্ধ করার আগে, ঘনাদাকে মাঝে মধ্যেই ‘কালো ভূত’ বা ‘কালো ইঁদুর’ হিসাবে সম্বোধন করা হয়, যা বারবার ঔপনিবেশিকতার সেই ভূতকে জাগিয়ে তোলে। আরও গভীর বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয় যখন আমরা দেখি যে এই ঘনাদার গল্পগুলি তার চারপাশের পরিচিত লোকদের কাছে মৌখিকভাবে বলা কেবলমাত্র। এই গল্পগুলির বাইরে, তিনি হলেন একটি যৌথাবাসের (মেস-বাড়ি) দ্বিতীয় তলায় বসবাসকারী একজন রহস্যময় মধ্যবয়সি ব্যক্তি। তিনি মাঝে মাঝে প্রথম তলার ভাড়াটেদের সঙ্গে কথোপকথনে লিপ্ত হন এবং তাদের থেকে সিগারেট চেয়ে খেতেই যেন তিনি নিজের অভিজ্ঞতার গল্প বলতে শুরু করেন। এটি এমন একটি দৃশ্য যা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দেশীয় সাহিত্যের ক্লাসিক চরিত্র কং ইজির কথা মনে করিয়ে দেয়।


তবে ঘনাদাকে তার আশপাশের মানুষরা যথেষ্ট সম্মান করতেন, যা হয়তো কং ইজির সঙ্গে মেলে না। গবেষণা করে এবং দীপের সঙ্গে কথা বলার পর আমি জানতে পারি যে, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, কলকাতার জনসংখ্যা আজকের মতো এত ঘন ছিল না। অতএব, মেসবাড়ি ধাঁচের যৌথ আবাসনগুলি কম খরচের হলেও থাকার জায়গা হিসেবে যথেষ্ট ভালো ছিল। অনেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হোস্টেলের মতো, সেই সঙ্গে সবার একসঙ্গে খাবার জন্য একটি ডাইনিং হল। যেহেতু অনেকেই থাকার জন্য দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা পছন্দ করতেন এবং বাসিন্দারা মূলত তরুণ (কিছু জীবনযুদ্ধে সংগ্রামরত ছাত্রসহ), তাই চায়ের দোকান বা রেস্তোরাঁর থেকেও অনেক ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়, আরও মিথোজীবী সামাজিক বন্ধন তৈরি হত সেখানে। এটি ঘনাদার চরিত্র এবং তার গল্পের প্রসারের মূল ভিত্তি হিসেবে ধরা যেতে পারে।
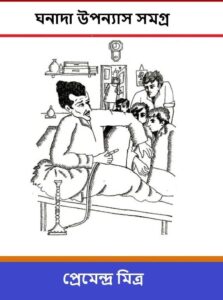
এত কিছুর পরেও, সবাই কি ঘনাদার গল্পগুলো সত্যি বলে মেনে নিয়েছে বলে মনে হয়? নিশ্চয়ই নয়। অনেক গল্পের শেষে, কেউ ঘনাদাকে তার দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করতে বলত, কিন্তু তিনি কখনও প্রমাণ দিতেন না। অনেক গল্পে, শ্রোতারা ঘনাদার উপর ঠাট্টা করার জন্য নানা ফাঁদ পাতার চেষ্টা করত, দেখত যে এই ‘দুঃসাহসিক অভিযাত্রী’ তাদের সঙ্গে সমান চাতুর্যে মোকাবিলা করতে পারেন কিনা। তিনি কখনই তাদের ফাঁদে পা দেননি, তাঁর গল্পগুলিকেই ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তিনি ফাঁদ এড়িয়ে যেতেন। প্রতিটি গল্পের শেষে এই ঠাট্টা করার আগ্রহ ক্রমশ কমতে থাকে তার শ্রোতাদের। ১৯৮৭ সালে শেষ গল্পটি প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত এই প্রাণবন্ত পরিবেশে সিরিজটি চলতে থাকে। পরের বছরের মে মাসে লেখক মারা যান।
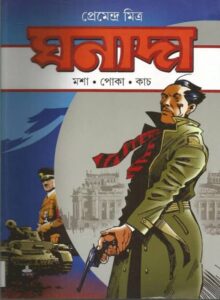
কং ইজির তুলনায় ঘনাদা ভাগ্যবান। সে একজন সম্মানিত ব্যক্তি, এমনকী রঙ্গমঞ্চের ভাঁড় মনে হলেও তাঁর কথা বেশ অর্থবহ। যদি তাঁর অভিজ্ঞতা সত্য হত, তাহলে তিনি তার বৃদ্ধ বয়সে একজন ঋষি হতে পারতেন, যেমন সুইপিং মঙ্ক। পাশাপাশি, তিনি বিশাল জ্ঞানের অধিকারী একজন নিভৃতবাসী, এই জ্ঞান ব্যবহার করে তাঁর চারপাশের লোকেদের প্রভাবিত করতে সক্ষম তিনি। এই চরিত্রটি বিজ্ঞান কল্পকাহিনি এবং সমসাময়িক সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে মূর্ত করে। জ্ঞান কিন্তু গল্প বলার মাধ্যমেই ছড়িয়ে পড়ে এবং টিকে থাকে, যদিও সেই জ্ঞান কখনও অবোধের বধির কানে এসে পড়ে বা কখনও তাকে অতিরঞ্জিত বা রহস্যময় বলে ভুল করা হয়। মানুষ তার বিশ্ব ভ্রমণের গল্পগুলি মনে রাখে এবং অন্তত এটুকু জানতে পারে যে তাদের নিজস্ব অঞ্চলের বাইরেও একটি সুবিস্তৃত পৃথিবী রয়েছে—আফ্রিকান রেইন ফরেস্ট, এশিয়ার তুষারাবৃত পর্বতমালা বা মেরু অঞ্চলের ভালুক এবং পেঙ্গুইন… আবার এও দেখা যায়, এই ধরনের কিংবদন্তিতুল্য অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও, কেউ এখনও একজন নিছক সাধারণ ব্যাক্তি হতে পারে, একটি ছোটো, অন্যদের সঙ্গে ভাগ করা বাড়িতে বাস করতে পারে এবং নিজেকে উপহাসের পাত্রে পরিণত করতে পারে। আমার কাছে, তাঁর এই অটল সংকল্প এবং অন্তর্নিহিত একাকীত্বের বৈপরীত্যই ঘনাদাকে এত আকর্ষণীয় করে তোলে।
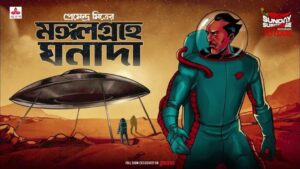
আর এটাই হল কং ইজির ট্র্যাজেডি। তিনি নিজে কোনো গল্পের কথক নন, বরং অন্য কারও গল্পের (বলা ভালো গসিপের) একজন চরিত্র। প্রায়শই এই অবিশ্বস্ত গসিপ বা পরচর্চা তাঁর প্রকৃত সত্তা এবং শিক্ষিত মানুষ হিসেবে তার মর্যাদা কেড়ে নিয়েছে—এমনকী অন্যদের সঙ্গে সমানে কথা বলার যোগ্যতাও হারিয়েছেন উনি। শিশুরাও স্থানীয় রাজনৈতিক শুদ্ধতার প্রতি অনুগত থাকতে তাকে অবজ্ঞা করে এবং তার সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করে। এই অর্থে, চারটি ভিন্ন উপায়ে হুই (‘ফিরে আসা’) চিনা অক্ষরটি লেখার ব্যাপারটি কেবলমাত্র আরেকটা গসিপ শুরু করার উপায় হতে পারে, কিন্তু সেকেলে বুদ্ধিজীবীদের কঠিনভাবে সমালোচনা করা থেকে তা শত যোজন দূরে রয়ে গেছে। বরং এর মধ্যে লুকিয়ে আছে এক গভীরতর বিষণ্ণতা। এই জ্ঞান যা সরাসরি অর্থনৈতিক কোনো প্রাপ্তি এনে দিতে পারে না, নিরক্ষর-অধ্যুষিত সমাজে সেই জ্ঞানের কোনো জায়গা নেই। শুধু তাই নয়, সেই জ্ঞান যদি মানুষকে সমাজে উচ্চমর্যাদা প্রদান করতে অপারগ হয় তবে সেই ব্যাক্তির সম্মানও আর থাকে না। ঘনাদার গল্পগুলি এই সমস্যাটিকে একটি ‘আনন্দময় পরিবেশ’-এর মধ্যে লুকিয়ে রাখে, যা একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সামাজিক আবহে মধ্যে গল্পে গল্পে অনেক কথোপকথনের সম্ভাবনা তৈরি করে। তবে, লু জুন এই “আনন্দময় পরিবেশ” থেকে উদ্ভূত নিষ্ঠুরতাকে অনাবৃত করে দেখিয়েছেন, যদিও এই নিষ্ঠুরতা শুধু যে বুদ্ধিজীবীদের উপরই নিক্ষিপ্ত তা নয়। সহজ করে শুধু এটুকু বলা যায় যে কং ইজি-র জায়গায় আপনি নিজেকে বসাতে পারবে না, যেখানে সবাই আপনাকে গসিপে গসিপে চিবিয়ে শেষে থু-থু করে ফেলে দেবে। এখন কং ইজি মিস্টার ফালুও হতে পারতেন কি না, এইভাবে জীবিকা নির্বাহের উপায় খুঁজে বের করতে পারতেন কি না—তা হয়তো গল্পগুলিকে পুনর্ব্যাখ্যা করার সম্ভাব্য উপায় হিসেবে ধরা যেতে পারে। তবে এটি সম্পূর্ণ আলাদা প্রসঙ্গ, সে নিয়ে পরে গল্প হবে।
Tags: Arthur liu, আর্থার লিউ, দশম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, রাকেশকুমার দাস