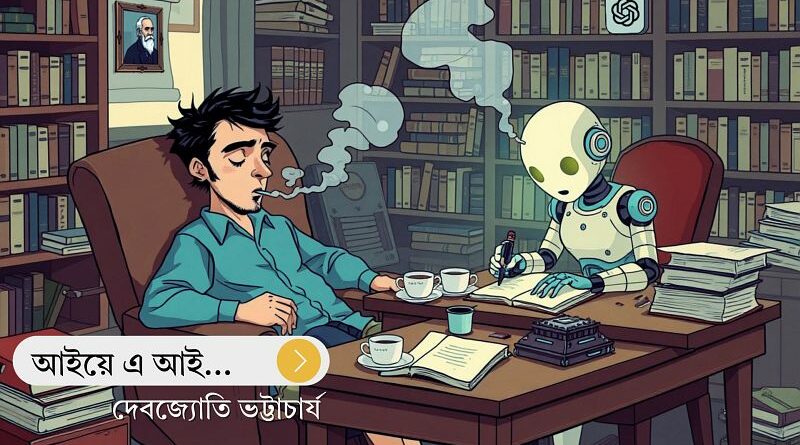আইয়ে এ আই…
লেখক: দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য
শিল্পী: টিম কল্পবিশ্ব
সাহিত্যক্ষেত্রে আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্সের প্রভাব (কিংবা উৎপাত /মহাসংগ্রাম /অস্তিত্বের লড়াই ইত্যাদি ইত্যাদি…) এই নিয়ে দুনিয়া জুড়ে ইদানিং বহু আলোচনা চলছে। এবং এ নিয়ে বিভিন্ন সাবধানতা, আচরণবিধি, যন্ত্র-কুম্ভীলকবৃত্তি প্রতিরোধ, কপিরাইট সংক্রান্ত রক্ষাকবচ ইত্যাদি বিবিধ পদক্ষেপ নেয়াও শুরু হয়ে গেছে। তবে বাংলা সাহিত্যের অভিভাবককূল (sic) এ-বিষয়ে এখনও মাথা বালিতে গুঁজে আরামে চা শিঙাড়া খাচ্ছেন।
প্রশ্ন হল তাঁরা কতদিন এইভাবে কাল কাটাবেন। এর জবাবে বলব, ডেস্কটপ ল্যাপটপ ট্যাব ইত্যাদির আবির্ভাব ও বাংলার সাহিত্য রচনা ও প্রকাশে তাদের ব্যবহারের মধ্য যে অবজার্ভড টাইম ল্যাগ, তাকে মাপকাঠি ধরল নিশ্চিন্তে বলা যায় আর বছর বিশেক বাদে তাঁরা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করবেন, ‘কেসটা ঠিক কী ভাই? খায় না মাথায় দেয়?’
এহেন প্রেক্ষিতে আপনারা যে প্রশ্নটাকে বাংলা বাজারের টাইম স্কেল-এ এত ‘তাড়াতাড়ি’ আলোচনার যোগ্য বলে মনে করে ফেলেছেন, এজন্য প্রথমে একটা ধন্যবাদ আপনাদের প্রাপ্য।
মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং, পুরোদস্তুর ইনটেলিজেন্স ইত্যাদি এআই-এর বিবিধ শাখা, ও বাংলা সাহিত্যে তাদের প্রভাব বিষয়ে প্রযুক্তিগত তত্ত্ব ও তথ্য নিঃসন্দেহে অনেকে লিখে ফেলেছেন। অতএব এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে সে বিষয়ে আর লেবু কচলানো ঠিক হবে না। কারণ টেক পণ্ডিত মহলে “তাবত শোভতে মূর্খ যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে…”
এ প্রশ্নটাকে আমি একটু অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে ও দেখাতে চেষ্টা করি বরং।
প্রশ্ন—আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স কি বাংলা সাহিত্যিকের কলমটা কেড়ে নিতে এসেছে? পারবে কেড়ে নিতে?
আসলে, এ-বিষয়ে ইদানিংকালের নানান প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যবাসরে সগৌরবে চেয়ার ধরছেন যাঁরা, তাঁরা সকলেই মহা আতঙ্কে ‘ওই এলো গেলো খেলো সর্বনাশ হল’ বলে উচ্চরোল তুলছেন মিডিয়ার দরবারে। তা, এঁদের এহেন আতঙ্কের কারণটা ঠিক কী?
এ প্রশ্নের জবাব খুঁজতে প্রথমে আমাদের দেখতে হবে সাহিত্য বস্তুটা কী?
আক্ষরিক অর্থে শব্দটার মানে হল ‘সঙ্গে থাকবার ধর্ম।’ কার সঙ্গে? না জীবনের সঙ্গে। বলা যায়, যে সুসজ্জিত অক্ষরমালা জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে চলে, তা-ই সাহিত্য। আরেকভাবে বললে, ও হল গিয়ে অক্ষরে তৈরি জীবনের একটা পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক মডেল। একটা উদাহরণ দিই।
ধরুন চারটে বর্ণ আছে—এ, সি, টি, আর জি। এবারে কোনো দক্ষ জেনেটিসিস্ট, যিনি জীবনের পাসকোডগুলো জানেন, তাঁর হাতে এই বর্ণগুলোকে দিলে তিনি এদের সাজিয়ে সাজিয়ে এমন একটা বর্ণসমষ্টি গড়তে পারেন, যা হয়ে উঠবে একটা ডিএনএ তন্তুর ফরমুলা। অর্থাৎ কাগজের অক্ষরসজ্জা হয়ে উঠবে বহুমাত্রিক জীবনের একটা দ্বিমাত্রিক মডেল। ওর মধ্যেই ধরা পড়বে একজন মানুষের চেহারা, স্বভাব, চোখের রং থেকে শুরু করে তাঁর কানের তিল, মুদ্রাদোষ, তাঁর চরিত্রদোষ, অঙ্কে,সঙ্গীতে, প্রেমে তাঁর দক্ষতার সম্ভাবনা এমন সবকিছুর অক্ষররূপ।
তা এই চার বর্ণের বদলে, গোটা বর্ণমালাটাকে হাতে নিয়ে যখন ব্যক্তি, বিশ্ব ও জীবন এমন সবকছুরই মডেল গড়ে তোলা হয় কাগজের বুকে(বা পর্দায়) তখন সেই সুপার-জেনেটিকসকে বলি সাহিত্য।
এবারে ধরা যাক একজন কমপিউটার প্রোগ্রামারকে প্রশ্ন করা হয়েছে, সাহিত্য কীভাবে গড়া হয়? নিজের একুশ বছরের জীবনে সে বেচারা সিনট্যাক্স বোঝে। অ্যালগরিদমটাও বোঝে। তারপরে ধরুন, গিয়ে কোডিং, তারপর ধরুন হিউরিস্টিকস এইসব কঠিন কঠিন জিনিস পড়ে পড়ে তার চোখে চশমা উঠেছে অকালে। কাজেই এহেন অভিজ্ঞতার বলে সাহিত্যের কিছু নমুনা পড়ে (তার জার্গনে ‘স্ক্যান’ করে) সে এহেন সাহিত্য গড়বার পদ্ধতির একটা যান্ত্রিক মডেল ভেবে নিতে পারবে সহজেই। সেটা এইরকম—
প্রথমে নিয়মের একটা সেট মেনে মেনে বর্ণ জুড়ে অর্থবহ শব্দ গড়া হবে। (টু ডু—বর্ণমালা ডেটাবেস এ ভরো। সমস্ত পরিচিত শব্দ ডেটাবেস এ ভরো। ইফ যুক্তির প্রয়োগে কোটি কোটি বর্ণসমন্বয় থেকে কয়েক হাজার বর্ণসমন্বয়কে ‘অর্থবহ’ পরিচয়ে সেভ করো।) তারপর শব্দদের আর এক সেট নিয়ম মেনে জুড়ে জুড়ে অর্থবহ বাক্য তৈরি হবে। (টু ডু—সিনট্যাক্স- রুল ১ –কত্তা-ক্রিয়া-কম্মো, রুল ২… রুল ৩… রুল ১২৩২৩৪৫ ইত্যাদি। এর বাইরে সব ওয়ার্ড কমবিনেশন জালি) তারপর আর এক সেট নিয়ম অনুসরণ সেই বাক্যদের জুড়ে জুড়ে রচিত হবে একটা অনুচ্ছেদ বা একটা পুরো কাহিনি। (টু ডু—‘চিড়িয়াখানায় শিশু’ আছে এমন বাক্য ‘হোটেলে রতিক্রিয়া’ আছে এমন বাক্যের সঙ্গে ওভারল্যাপ করবে না। রুলে-২… রুল ৩………… রুল ৪৩৫৬২৭৫৪৫৬৭৫৬৫৫৬)
নিয়মগুলো প্রোগ্রামিং করে দেওয়া কঠিন নয়। কঠিন নয় একটা বিরাট শব্দভাণ্ডার ও থিসরাসকে যান্ত্রিক স্মৃতিতে গুঁজে দেওয়া। এরপর আসবে নিয়মগুলোকে কাজে লাগিয়ে শব্দ, বাক্য ও অনুচ্ছেদ গঠনের অ্যালগরিদম, এবং তা কতটা সঠিক হচ্ছে তার তুলনা করবার জন্য সাহিত্যের ডেটাবেস। এইটে তৈরি করে দিলে, তাকে প্রয়োগ করে, কি-ওয়ার্ডের ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতের লেখা গড়ে তোলা আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্সের কাছে খুব একটা কঠিন কাজ নয়।
তা এইভাবে একজন কমপিউটার প্রোগ্রামার তার সাহিত্য গড়বার অ্যালগরিদমটা বানিয়ে ফেলবে। তবে খুব স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষাপ্রাপ্ত যন্ত্রের গড়া সে সব কাহিনি কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট হবে। বিনা নির্দেশে স্বাধীনভাবে কোনো বাক্য গঠনে তার অপারগতা এর জন্য দায়ী হবে।
এরপর সেই সমস্যাটিকেও পার হওয়া যাবে যন্ত্রের গভীরতর শিক্ষার মাধ্যমে। হিউরিস্টিকসের প্রয়োগে এরপর যন্ত্র কোনো একটা গল্প লিখতে বসে জানা তথ্য ও তত্ত্বের ভিত্তিতে নতুন কোনো পথে চিন্তা করে, নিজের সিদ্ধান্তমতন একটা নতুন সিচুয়েশনকে গড়ে তার কথা লিখে ফেলতে পারবে। এই স্তরে তা হবে তার নিজস্ব সৃষ্টি।
এইবারে দেখা যাক এইসব মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং-টিং করে কীভাবে সে একটা কবিতা লেখে।
তাকে আপনি বললেন, “চাঁদ নিয়ে একটা কবিতা লেখ।”
তার অ্যালগরিদম অমনি বাক্যটাকে বিশ্লেষণ করল। বুঝল তাকে X (কবিতা) বানাতে হবে। বিষয় হবে Y (চাঁদ)। এবারে সে ডেটাবেস-এ X (কবিতা) কাকে বলে সেটা দেখল। সঙ্গে সঙ্গেই অন্ত্যমিল, মিটার, চাঁদ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কবিতার শব্দমালা এইগুলোকে একত্র করে নিয়ে সেই কন্ডিশনদের স্যাটিসফাই করছে এমন সব শব্দ বাছাই করে পাশাপাশি আনল। তারপর সেটার ভ্যালিডেশন করা হল অজস্র এই জাতীয় বাক্যের ডেটাবেস মিলিয়ে। এবং শেষমেষ সে লিখল—
“রাতের আকাশে তারার মাঝে
ঝলমল করে রূপের আভা
আলোয় ভরে দিয়েছে পৃথিবী
মনের মধ্যে জাগিয়েছে স্বপ্নের জীবী”
দুর্বল, তবে কবিতা। তবে, ক-দিন বাদে এইটাই বেশ সবল হবে, তাগড়া হবে। প্রশ্ন হল, তখন? এআই নন, নেহাত সাদামাটা মানুষ, এমন লেখকের গতি কী হবে? ধরুন তাঁকে বললাম চাঁদ নিয়ে লেখো। তিনি সাতদিন ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তারপর দশ লাইন লিখলেন। তারপর পয়সা চাইলেন। ওদিকে, আমার ‘গুগল জেমিনি’ নামক কৃবু (মানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা)কে বলতে সে ওপরের কবিতাটা আমায় এক সেকেন্ডে ফ্রি-তে দিয়ে দিল। তাহলে জয়ঢাকের পুজো সংখ্যার জন্য জেমিনিকে দিয়েই লেখালেই তো হয়। সূচিপত্রের লিস্ট দেব, আর সে যান্ত্রিকভাবে সব মিলিয়ে গুছিয়ে গল্প কবিতা উপন্যাস বানিয়ে দিয়ে দেবে। কাজ শেষ। ল্যাঠা চুকে যায়।
কিন্তু, এতে ল্যাঠা সত্যিই কি চোকে? সে প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হলে আমাদের, সাহিত্যবস্তু নির্মাণের অযান্ত্রিক দিকটার কথায় আসতে হবে।
‘অযান্ত্রিক’ বলাটা অবশ্য পুরোপুরি ঠিক হবে না। যেহেতু মানুষের মস্তিষ্কযন্ত্রে তার উদ্ভব; অতএব এক অর্থে তা যান্ত্রিক তো বটে। তবে এ ‘যান্ত্রিক’ সে ‘যান্ত্রিক’ নয়।
সেটা কেমন? ধরা যাক একজন মানুষ। তিনি সারাটা জীবন সাহিত্য রচেছেন, সংগীত রচেছেন। তাঁর সেই সোনার ফসল নিয়ে সাহিত্যলক্ষ্মী চলেছেন সময়নদীতে খেয়া বেয়ে ভবিষ্যতের দিকে। সেই অদেখা ভবিষ্যতেও সেই ফসলেরা অমর হয়ে থাকবে। অথচ তিনি নিজে সেখানে যেতে পারবেন না। ভবিষ্যতগামী সোনার তরীতে আর তাঁর জড় শরীরের ওঠবার হক নেই। তাঁকে মরণশীল জীবনের ঘাটে বসে দেখতে হবে
“শ্রাবণ গগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরেফিরে
শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি
যাহা ছিল লয়ে গেল সোনার তরী।”
এখানে তাঁর মাথার যে অ্যালগরিদম শব্দগুলোকে এনে জুড়ছে সে অ্যালগরিদমের পেছনে আছে মানবশরীরের একটা পরিপূর্ণ জীবন কাটাবার ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স, এবং আসন্ন মৃত্যুর যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি। সে অভিজ্ঞতা তাঁর স্বোপার্জিত। মস্তিষ্কে ভরে দেওয়া সেকেন্ডারি মেমরি নয়। আর তাই যে শব্দগুলো তাঁর মস্তিষ্করূপ অর্গ্যানিক কমপিউটার এখানে একত্র করছে তা জীবনের অভিজ্ঞতার রসে জারিত হয়ে ওপরের অমর শব্দবন্ধগুলোর জন্ম দিয়েছে।
আর জেমিনিকে যখন “সোনার তরী” নিয়ে একটা মৌলিক কবিতা লিখতে বলছি সে লিখছে—
“নদীর বুকে ভেসে বেড়ায়
সোনার তরী, রূপের আভা
ঝলমলে তারা আকাশ জ্বলে
চাঁদের আলোয় পৃথিবী ঝলে
তার তৈরি দুটো কবিতা পাশাপাশি রেখে দেখুন, বেচারা একই উপমকে ঘুরেফিরে কাজে লাগিয়ে চলেছে। এ কবিতায় শব্দ আছে, অর্থও আছে, মিটারও আছে, কারণ সেগুলো প্রোগ্রামিং করা যায়। কিন্তু প্রাণ নেই। কারণ রচয়িতা নিজে প্রাণহীন। কারণ সে চাঁদ দেখেনি। সে নৌকো দেখেনি। সেই সবই তার কাছে কিছু লজিক, কিছু আলগরিদম, কিছু প্রোগ্রামের সমাহার। তার বেশি কিচ্ছু নয়। বেহালার বাজনা তার কাছে একগুচ্ছ সংখ্যার ওঠাপড়া, তাতে মিউজিক বলে যে অপার্থিব অনুভূতিটা আছে তাতে তার কোনো অধিকার নেই। সে বেচারা যেন একটা চাটু। পিঠে বানায় রোজ। কিন্তু পিঠের স্বাদ কেমন তা জানে না।
সাহিতসৃষ্টিতে তাই এআই-এর একটা সীমাবদ্ধতা থেকে যাবেই চিরটাকাল। তা হল, সাহিত্য লিখতে গেলে জৈব জীবনের ফার্স্ট হ্যান্ড অভিজ্ঞতা ছাড়াই তাকে জৈব জীবনের নানান অনুভূতির কথা লিখে জানাতে হবে। জানাতে হবে গাদা গাদা শব্দার্থ, সিনট্যাক্স আর ব্যাকরণের সূত্রের ট্রাপিজ খেলায় শব্দ গেঁথে গেঁথে, যে শব্দদের সঙ্গে তার অনুভূতির কোনো যোগ থাকবে না। সৎ সাহিত্যের যে আত্মা, ব্যাখ্যাহীন অনুপ্রেরণার যে সাইন্যাপটিক ফ্ল্যাশ সাহিত্যিকের জীবনবোধ আর অভিজ্ঞতা থেকে উঠে এসে তাঁর সৃষ্টিকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে অমর করে তোলে তার নাগাল এআই কোনোদিন পাবে না।
তাহলে? সাহিত্যিক এআই-এর ভবিষ্যৎ কী? বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যে?
আছে। বিরাট ভবিষ্যৎ আছে। বলছি। ইদানিং বাংলা সাহিত্য বেশ লাভজনক হয়ে উঠছে। বৌদ্ধিকভাবে তা চিরকালই পুষ্টিকর ছিল, ইদানিং আর্থিকভাবেও তা কিঞ্চিত পুষ্টিকর হয়ে উঠেছে সাহিত্যজীবীদের কাছে। ফল গত বছর সাতশো পুজোবার্ষিকী বের হওয়া (সাতশো না হলেও তার কাছাকাছি তো বটেই।) বলাবাহুল্য সাতশো পত্রিকা বেরোলে, বা এক বইমেলায় পঞ্চাশ হাজার বই বেরোলে অত লেখা জোগাড় করা প্রকাশকের পক্ষে বেশ কঠিন। আর জোগাড় হলেও তার মান ধরে রাখাটা অসম্ভব। এর নীট ফল, গত কিছুকাল ধরে যা বেরোচ্ছে তার নব্বই শতাংশ ওই—
“ঝলমলে তারা আকাশ জ্বলে
চাঁদের আলোয় পৃথিবী ঝলে”
টাইপের কেস।
এই প্রকাশন ও পত্রিকাদের একটা বড়ো অংশ আবার লেখকদের জন্য বিনিপয়সার ভোজে বিশ্বাসী। পিটুনির ভয়ে অটোওয়ালাকে পয়সা দিতে ভোলে না, কিন্তু লেখককে বুড়ো আঙুল দেখায় মার খাবার ভয় না থাকায়। কাজেই লেখক, ও এহেন প্রকাশক সম্পাদকদের মিউচুয়াল উপকারার্থে এই এআই সাহিত্য অত্যন্ত ভালো কাজে লাগতে পারে।
যেমন ধরুন, আপনার যদি আজ মাঝরাতে পুজোসংখ্যা বানাবার বেগ চাপে তাহলে দুটো মেশিনে জেমিনি আর চ্যাটজিপিটি লাগিয়ে এক রাতে সাতটি হাড়হিম উপন্যাস, চব্বিশ সনসনাতা কাহানি ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি… বানিয়ে ফেলুন। মোটামুটি লজিকালি ঠিকঠাক, বানান ভুল খানিক কম, খাটুনি নেই, খরচ নেই। তারপর সকালে উঠে এআই দিয়ে ছবিগুলো বানিয়ে ফেলে দুপুরে ছাপতে দিয়ে বিকেলে প্রিবুক ঘোষণা করে দিন। তাহলেই হয়ে গেল। বাকি রইল পড়া, তা লোকে কেনে বটে কিন্তু পড়ে কজন? দু-একজনকে বলে একটু আধটু রিভিউ লিখিয়ে দিলেই হল। বিক্কিরি হয়ে যাবে। পড়ে থাকবে না।
অপরদিকে বেচারা লেখক জানে পয়সা দেবে না, আর দিলেও দুশো টাকা আর একটা বিড়ি ধরিয়ে দেবে হাতে। তবু রাত বারোটায় যখন তিপ্পান্নতম পুজোবার্ষিকীর পুঁয়েপাওয়া সম্পাদকের ফোন পাবে ‘দাদা একটা উপন্যাস চাই দশ হাজার শব্দ।’ তখন সেও এআইকে বলে উপন্যাস লিখে তক্ষুনি পাঠিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।
এমনিতেও মধ্যমেধা বা নিম্নমেধার লেখাতে জাস্ট শব্দখেলা থাকে, জীবনবোধ থাকে না। ফলে এখনকার নব্বই শতাংশ লেখার চাইতে তা কোনো অংশে খেলো হবে না।
উপস্থিত এই সত্যিটা অনেকেই বুঝে ফেলছেন। আর তাই মধ্য ও নিম্নমেধার সাহিত্যমহলে এ নিয়ে একটা আতঙ্কের স্রোত বইছে। ওই এলো গেলো খেলো ভাব।
তবে কে কী ভাবছে না ভাবছে, কার ভয় লাগছে আর কার ফুর্তি সেসব থেকে সরে দাঁড়িয়ে যদি একটু স্পেকুলেট করা যায় তাহলে যে ছবিটা বেরিয়ে আসবে সেটা এইরকম বলে মনে হয়—
বাংলা সাহিত্য রচনায় এআই আর একটু উন্নত হলেই বাংলা সাহিত্যের নব্বই শতাংশ লেখা ও লেখক যা মধ্য ও নিম্নমেধাবর্গের অন্তর্ভূক্ত তাদের জায়গায় এআই এসে, মাঝারি ও খেলো প্রকাশকগুলোর সময় ও খরচ দুইই কমিয়ে দেবে। ওর একটা বিরাট রিডার বেস আছে। তারা সেগুলো পড়ে ছবি তুলে সোশাল মিডিয়া মাতিয়ে সুখে থাকবে। ফলে, ইদানিং প্লাবনের মতো ধেয়ে আসা প্লেবিয়ান সাহিত্যজীবী ও উপভোক্তাদের হাতে সেই চুষিকাঠিটি ধরিয়ে দিয়ে, ভালো মানের লেখক, প্রকাশক ও পাঠক, একটু শান্তিতে সাহিত্যচর্চা করতে পারবেন পৃথকভাবে, মধ্যমেধার চোখের আড়ালে।
এইটাই হল গিয়ে টানেলের অন্যপ্রান্তে দেখা দেওয়া আলোটার এক ঝলক। সৎ সাহিত্যের এআইকে ভয়ে পাবার কিছু নেই। সত্যিকারের বাঁচা জীবন থেকে তার জন্ম। তার জোর একগুচ্ছ ইলেকট্রনের ছোটাছুটির চেয়ে অনেক বেশি।
Tags: দশম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য