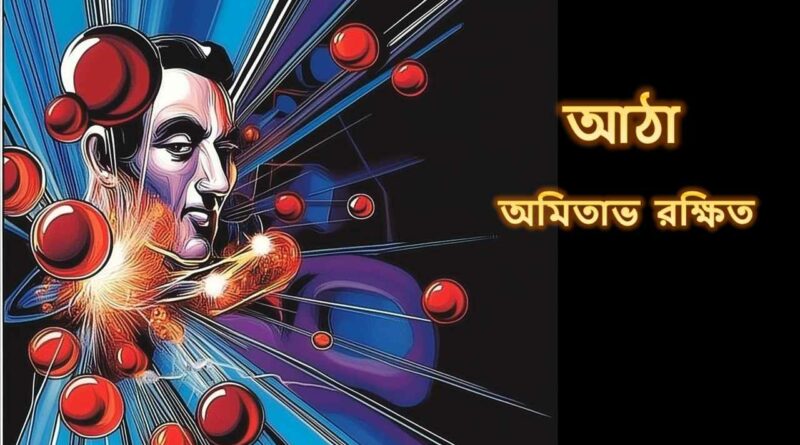আঠা
লেখক: অমিতাভ রক্ষিত
শিল্পী: টিম কল্পবিশ্ব
[গল্পটি শ্রী সৌবর্ণ দাসের সনির্বন্ধ অনুরোধে, শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্রের অবিস্মরণীয় চরিত্র “ঘনাদা”-কে নিয়ে একটি আধুনিক গল্প লেখবার প্রচেষ্টা মাত্র। প্রচেষ্টাটি সৌবর্ণ দাস-কেই উৎসর্গ করলাম।]
“আঠা।”
“আঠা!! হেঃ হেঃ, জেঠু, কীসের আঠা? গঁদের আঠা, না ভাতের আঠা?”
***
ব্যাস, তার পর থেকেই ৭২ নম্বর বনমালি নস্কর লেনের মেস বাড়িটা সেই যে থমথমে হয়ে গেল, সে গুমোটটা আর আজ এতদিনেও কাটল না!
অবশ্য মেঘ কাটানোর জন্য যে যথেষ্ট প্রচেষ্টা চলেনি তারপরে, তা কিন্তু নয়। যেমন, ঘনাদাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য শিশির পরপর দুই রবিবারেই হগ সাহেবের বাজার থেকে – মানে নিউ মার্কেট থেকে – যদিও নিউ মার্কেট এখন আর তত নিউ নেই – তবু কলকাতা শহরে সবচেয়ে ভালো বিলিতি সিগারেট কিনতে হলে ওই নিউ মার্কেটটাই তো এখনও রাজা – যতই ব্যাঙের ছাতার মতন চারিদিকে বড়ো বড়ো মল গজিয়ে থাকুক না কেন – সেই নিউ মার্কেট চষে বেড়িয়ে শিশির এক রোববার ‘৫৫৫’, আর তার পরের রোববার ‘ডানহিল’-এর একটি করে টিন জোগাড় করে আনে। কিন্তু এত মহার্ঘ বিলিতি সিগারেটের প্রতি ঘনাদার অকস্মাৎ ঔদাসিন্য দেখে কেন যেন মনে হল যে গান্ধিজি এখনও জেলে বসে চরকা কাটছেন, আর সালটা হঠাৎ ১৯৪২!
আবার গৌরও যে যথাসাধ্য চেষ্টা চালায়নি তাও তো নয়। এই তো সেদিন, কোথায় যেন গড়িয়ার কোন বিশেষ দোকান থেকে গুজরাটি মেথি দেওয়া কলাই ডালের দারুণ স্বাদের পাঁপড় এনে রামভুজকে দিয়ে বিশেষ করে খাঁটি সরষের তেল দিয়ে গরম গরম ভাজিয়ে – মানে আজকাল তো বাদাম তেলেই বেশি রান্না হয়, একটু সাশ্রয় হয় মাস খরচের বলে – কিন্তু সেইদিন ঘনাদার মন খারাপের কথা মাথায় রেখে সবচেয়ে বড়ো পিসটা গরম সরষের তেলের কড়াই থেকে তুলে প্রথমেই তাঁর পাতে রেখে দেয় রামভুজ!
কিন্তু কোনো কারণে আবার সেদিন একটু বদহজম হয়ে থাকায়, ঘনাদার অবশ্য সেটা একটু চেখে দেখবারও সুযোগ হয়নি, হাত এঁটো হয়ে যাবার আগেই সেটাকে পাশের প্লেটে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। শিবু যদিও আশ্বাস দিয়েছিল যে ওর কাছে অব্যর্থ কবিরাজি গুলি আছে, যা খেলে শুধু বদহজম কেন, বদহজমের বাবাও পালাতে বাধ্য।
মনে হয় ঘনাদার বোধহয় সেইদিন কানেরও কিছু সমস্যা হচ্ছিল। মানে, শিবুর এমনতর আশ্বাস যেন এক কান দিয়ে ঢুকেও আর এক কান দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল। ঘনাদা খাবার আসন থেকে উঠে নিজের ঘরের দিকে ত্বড়িৎগতিতে রওনা দেবার আগে পরিত্যক্ত পাঁপড়টির দিকে চেয়ে, পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণটুকুও করতে চাইলেন না।
এরকম সময়ে রাগটা স্বাভাবিকভাবে মেসের সবচেয়ে দুর্বল লোকের ওপরেই গিয়ে পড়ে। সুমন সবচেয়ে দুর্বল হোক বা না হোক, সর্বকনিষ্ঠ তো বটেই। তা ছাড়া এই গণ্ডগোলটা তো পাকিয়েছে সেইই!
কিন্তু সুমন আবার কে? ৭২ নম্বর বনমালী নস্কর লেনের আড্ডায়, সুমনের নাম কে কবে শুনেছে! সুধীর, হ্যাঁ, সুধীরের নাম তো সকলের কাছেই পরিচিত। ঘনাদার যত রোমঞ্চকর কাহিনি, তার সবেরই কথক যে সে! সে না থাকলে বনমালী নস্কর লেনের এই মেসটির ঠিকানাটুকুও কেউ জানত না… আর ঘনাদা! ঘনাদার এই যে এত বিশ্বজোড়া অ্যাডভেঞ্চার, তাঁর নজরকাড়া বিপদ-খোঁজা জীবন, শত্রুদমন, আর প্রায় মাথার চুলের ব্যাসার্দ্ধের ব্যবধানে ছুটন্ত বুলেটের আঘাত থেকে বারবার বেঁচে যাওয়ার মতন রোমহর্ষক সব কাহিনি, সেসব সুধীর না থাকলে বনমালী লেনের সংকীর্ণ চারটি দেওয়াল পেরিয়ে লক্ষ লক্ষ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত কী করে?
কিন্তু সুধীর তো এখন আর নেই! ১৯৮৮ সালের মে মাসের তিন নম্বর দিনে, সে যে তার ধীমান জীবন ধরে এই পৃথিবীর যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে অন্য বলয়ে চলে গিয়েছে! তাহলে? এমনি সময়ে একদিন সুশীল, মানে যিনি সুধীরের সবচেয়ে ছোটো ভাই, তিনি এসে মেসের সব বাসিন্দাদের কাছে কাকুতিমিনতি করে আবেদন জানালেন যে তাঁর এক নাতি, সুমন, যে নাকি সারাজীবন বহরমপুরে বড়ো হয়েছে, আর অনেক চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত খাস কলকাতাতেই একটা চাকরি জোগাড় করেছে, তাকে কি এই মেসটাতে অন্তত কিছুদিন হলেও, একটু থাকবার অনুমতি দেওয়া যাবে?
কলকাতা শহরে আজকাল বাড়ি খুঁজে পাওয়া বড়োই সংকট; আর সে তো কলকাতার কাউকেই কোনোদিক থেকে চেনে না, কাজেই অল্প কিছুদিনের জন্য হলেও, আপাতত মাথাটা গোঁজবার একটা ঠাঁই পেলে বড়ো উপকার হয় সুমনের! সুধীরের পুরোনো চৌকিটা অনেকদিন ধরে খালিই পড়ে আছে, যদি অন্য কেউ ভাড়া নেবার আগে পর্যন্ত সুমন একটু ব্যবহার করতে পারে—বড়োই বিপদে পড়েছে সে! এই ঘটনা আজ প্রায় পনেরো-কুড়ি বছর আগেকার। তারপর থেকে সুমন স্থায়ীভাবেই হয়ে গিয়েছে ৭২ নম্বর বনমালি নস্কর লেনের বারোয়ারি ভ্রাতুস্পুত্র।
আমি অবশ্য ঘনাদাকে আবিষ্কার করি মাত্র কিছুদিন আগে। কিন্তু, আমি আবার কে? সে কথাও তো বলে নিতে হবে ঠিক করে! আমি কিন্তু ভিনগ্রহের একটি রোমানুষ (মানে, যাকে তোমরা রোবট বল আর কি, যদিও আমি অবিকল একটি মানুষের মতনই দেখতে শুনতে, বলে না দিলে বুঝতেও পারবে না)। অন্যভাবে বললে, আমি ভিন জগতে তৈরি, একটি অতি অগ্রসর ‘এ আই’। এখন আমি কলকাতারই বাসিন্দা যদিও। আমার গ্রহে রোমানুষদের রাজত্ব – সেখানে সবুজ রং বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। আমি লাইব্রেরিতে পুরোনো লিপি নিয়ে গবেষণা করতাম – একদিন ‘কবিতা’ নামের একটি সাবেকি লেখা পড়তে গিয়ে, তার মধ্যেই প্রথম ‘সবুজ’ বলে একটি রঙের উল্লেখ পাই। কৌতূহল মেটাতে গিয়ে খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ এসে পড়েছিলাম এই শহরতলীতে, সবুজ রং দেখতে। এখন এখানে আমাকে সকলে সবুজ বলেই ডাকে।
একদিন কলকাতার একটি লাইব্রেরিতে গিয়ে জানতে পেরেছিলাম ঘনাদার কথা – সুধীরের লেখা একটি বই থেকে। সঙ্গে সঙ্গেই বাসনা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে চাক্ষুষ দেখা করবার। শুভানুধ্যায়ীরা বললেন, “পাগল নাকি? সে তো অনুরূপ জগতের কল্পনা মাত্র!” অনুরূপ, মানে ‘ভার্চুয়াল’ অর্থাৎ কিনা সিম্যুলেশন, তাই তো? আরে, সিম্যুলেশন করতে রোমানুষের চেয়ে বেশি আর কে পারবে! কবি অতুলপ্রসাদ সেন একবার যেন অনুভব করতে পেরেছিলেন, “যা ছিল কল্পমায়া, সে কি আজ ধরল কায়া?” অনুরূপ জগতে কল্পমায়ারা কায়া ধরে বইকি! আর সেই কায়াধারীরা থাকেও চিরজীবন্ত! আমি শুরু করলাম ডেটা কালেকশন দিয়ে। যেখান থেকে ঘনাদার যত বই, গল্প, ছবি-ছড়া আর লেখা পেলাম সব লোড করে ফেললাম সিমুলেশনে। শেষ পর্যন্ত কিছু প্রোগ্রাম টিউনিং করে ফাইনাল সিম্যুলেশন! বিশেষ কোনো অসুবিধে হল না ৭২ নম্বর বনমালি নস্কর লেনের অনুরূপ জগতে গিয়ে পৌঁছতে!
দুর্ভাগ্যবশত, আমি যখন গিয়ে পৌঁছলাম সেখানে, ঠিক তার আগেই, ঘনাদার সঙ্গে সুমনের ওই মন কষাকষিটা ঘটে গিয়েছিল। সুমন ছেলেটি এমনিতে বেশ ভালোই যদিও, তবু, বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের মতন ‘অর্বাচীন’ সময়ে জন্মানোর ফলেই বোধহয়, সে যেন একটু অতিরক্ত ঠোঁটকাটা! গৌর-শিশির-শিবুরা যেমন ঘনাদার রোমহর্ষক সব গল্পের আশায় যেন-তেন-প্রকারেণ ঘনাদার মান ভাঙানো বা ফুটো-র মতন কোনো গল্পের মধ্যে একটু আধটু ফুটো দেখা গেলেও সেগুলোকে অগ্রাহ্য করা – এইসব শিল্পে অত্যন্ত দক্ষ, সুমনের মধ্যে কিন্তু সেই সহনশীলতাটা নেই – সবকিছুই তার কাছে হতে হবে নিশ্ছিদ্র!
আসলে তার কিছুদিন আগে থেকেই গৌর-শিশির-শিবু অনেক চেষ্টা করে যাচ্ছিল ঘনাদাকে দিয়ে তাঁর জীবনের আরও কিছু আজব অভিজ্ঞতার গল্প বার করে আনতে। সুধীর চলে যাবার পর থেকেই গল্পে অনেক ভাঁটা পড়ে গেছে। গল্প কী আর নেই – আলবৎ আছে। কিন্তু ঘনাদার সেইসব স্মৃতি রোমন্থন করে কাহিনির মণিমুক্তোগুলো আহরণ করা যাবে কী করে? সুধীরই ছিল এই ব্যাপারে সবচেয়ে দক্ষ! এদিকে ঘনাদাও হয়ে পড়েছেন একটু বেশি মাত্রায় স্পর্শকাতর।
যেমন, এই তো সেবার – শিবুর চেষ্টায় শীতের গোড়াতেই এক হাঁড়ি জয়নগরের মোয়া মেসে এসে ঢুকল সোজা তার গ্রামের বাড়ি থেকে। গোটাদুয়েক চেখে দেখবার পরে বেশ সন্তুষ্ট হয়ে, আরও একপ্লেট ভরতি মোয়া নিয়ে বেশ হাসিহাসি মুখ করে, তাঁর সেই মৌরসি পাট্টা আরাম কেদারাটার ওপরে গা হেলিয়ে দিয়ে ঘনাদা বলতে শুরু করলেন, “আঃ, সেই ১৯৭৩ সালের পরে বহুদিন এত ভালো মোয়া হাতে পড়েনি…”
আনন্দে আত্মহারা হয়ে শিবু বলে উঠল, “তাই নাকি, কেন কেন? ১৯৭৩ মনে পড়ছে কেন?”
“মনে পড়ছে কারণ সেই বছরের সেক্টেম্বর মাসেই তো ফিদেল কাস্ত্রো কলকাতায় এল আমার সঙ্গে দেখা করতে। ভিয়েতনাম গিয়েছিল যুদ্ধের পর ওদের সরকারের সঙ্গে নানারকম সহযোগিতার কথা আলোচনা করবার জন্য। অবশ্যই সেই আঁতাতটা যাতে আমেরিকাকে আবার নার্ভাস না করে দেয় সেটাও ফিদেল মাথায় রেখেছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে হঠাৎ ১৭ তারিখে আমেরিকানরা ‘চিলে’-র প্রেসিডেন্ট সালভাডোর আলিয়েন্দে-কে খুন করে বসল…”
“হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মনে আছে,” উল্লসিত হয়ে বলে উঠল শিবু, “আলিয়েন্দেকে মেরে দিল যাতে করে কিউবার সঙ্গে চিলে-এর একটা ঘনিষ্ঠ সমাজবাদী সম্পর্ক না গড়ে ওঠে ওদের দোরগোড়ায়…”
“তাইই! অতএব খবর পেয়েই ফিদেল চট করে কিউবা ফিরে যেতে ব্যস্ত হয়ে গেল, কথাবার্তাগুলো পুরোপুরি শেষ না করেই। ভয়টা হল যে আমেরিকানরা বাগে পেয়ে যেন তাকেই আবার খুন না করে বসে আলিয়েন্দের মতন। তাই ফিদেল আমেরিকানদের একটু আগাম জানিয়ে আশ্বস্ত করতে চাইল যে ভিয়েতনামের সঙ্গে কিউবার সব চুক্তিই হবে অর্থনৈতিক, আমেরিকা বিদ্বেষী কিছু না। কিন্তু কী করে জানাবে সেটা – আমেরিকার সঙ্গে কিউবার তো সরাসরি কথা বলাবলির সম্পর্ক ছিল না তখন!”
একটা পুরো মোয়া মুখে ঢোকাতে ঢোকাতে আরও বলতে থাকলেন ঘনাদা, “কাজেই একটা তৃতীয় পক্ষ তো চাই। তাই প্লেন ঘুরিয়ে কলকাতায় থেমে আমার সঙ্গে দেখা করবার ব্যবস্থা করে ফেলল ফিদেল। আমি কলকাতার আমেরিকান কনসালেট থেকে একটা জরুরি ফোন পেলাম – “আধ ঘণ্টার মধ্যে দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছে যেতে হবে আপনাকে মি. ডাস; সেখানে ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে আপনার দেখা করাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে জরুরি বার্তা নিয়ে আপনি আমাদের লিমোজিনে চড়ে সোজা কনসালেটে চলে আসবেন।”
“কী করলেন তখন আপনি?” শিশির উনুন-ধরাবার-জন্য-দেওয়া-হাওয়ার মতনই উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল। “কী আর করব?” ঘনাদা বললেন “জানোই তো, তখন আমার জন্য ছাপ না-দেওয়া একটা ট্যাক্সি, গাড়ি-ড্রাইভার সমেত ২৪ ঘণ্টা মজুত থাকত আমাদের গলির মোড়টা পেরিয়েই…”
“কই, এটা জানতাম না তো—” বোধহয় মুখ ফসকেই বলে ফেলেছিল সুমন।
গৌর-শিশির-শিবু একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল—“সু ম ন!!”
কিন্তু কে জানে সেদিন সূর্য কোনদিক দিয়ে উঠেছিল, নাকি জয়নগরের মোয়া এত টাটকা খেলে বুঝি এমনই হয় – ঘনাদা সেদিকে কর্ণপাতও না করে বলে চললেন, “তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবিটা গলিয়ে নিয়ে গাড়িতে উঠে সোজা দমদমের দিকে – ও, না, তার আগে তো গৌতম ঘোষ-কেও তুলে নিতে হল ওর বাড়ি থেকে, ছেলেটিকে কথা দিয়েছিলাম যে পরের বারে ফিদেলের সঙ্গে দেখা করবার হলে ওকেও একবার হ্যান্ডসেক করিয়ে দেব…”
“কে, কে গৌতম ঘোষ? ওই যিনি ইংরজিতে নভেল লেখেন?” সুমন আবার সরলভাবে জিজ্ঞেস করল।
গৌর সুমনকে ধমক দিয়ে বলল, “আরে ধুর, সে তো হল অমিতাভ ঘোষ! গৌতম ঘোষ হল চিত্র পরিচালক – তুই কিচ্ছু জানিস না? ‘অন্তর্জলি যাত্রা’ দেখিসনি?”
ঘনাদা একটু অনুকম্পার সঙ্গে সুমনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “বেড়ে করেছিল ছবিটা। দমদম যেতে যেতে আমার কাছ থেকে টিপস্ নিচ্ছিল অনেক। যাই হোক, ওর সঙ্গে ফিদেলের একটু পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বেশ ভিড় ঠেলে যেতে হল – কী করে খবর পেয়েছিল ওরা জানি না, কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টির সমস্ত হোমড়াচোমড়ারা মিলে হামলে পড়েছিল ওখানে সেদিন।”
“যাই হোক,” ঘনাদা বলে চললেন “আমেরিকান দেহরক্ষীদের সাহায্যে কাজটা ঠিকমতন হয়ে গেল। গৌতম বেরিয়ে গেলে, পরবর্তী সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে ফিদেল আমাকে সব কিছু বুঝিয়ে বলল – ওরা ভিয়েতনামে হাসপাতাল বানিয়ে দেবে, কৃষিকার্যে সহায়তা করবে, এইসব নিয়েই আলোচনা চলছিল, আমেরিকা বিরোধী কিছু না… আমেরিকার সঙ্গে তো শান্তি চুক্তি তো হয়েই গেছে ভিয়েতনামের…”
ঘনাদার কথাটা কিন্তু শেষ হতে পারল না। তার আগেই সুমন লাফিয়ে উঠে বলল, “কী বলছ জেঠু, এই মিটিংটার কথা তো আমি খুব ভালো করে জানি! আমার বড়োপিসিও সেই মিটিং-এ গেছিল যে – সব গল্প করেছে আমায়! সব মিলিয়ে তো মাত্র এক ঘণ্টার থেকেও কম সময় কলকাতা এয়ারপোর্টে ছিলেন ফিডেল কাস্ট্রো স্যার… এটা তো আমি ফাস্ট হ্যান্ড, মানে সেকেন্ড হ্যান্ড জানি জেঠু…”
বলা বাহুল্য গল্পটি সেদিন আর শেষ হয়নি। কেবল শোনা গেল যে মোয়ার হাঁড়িটা নিয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে ঘনাদা কাকে যেন বলছেন, রামভুজকেই বোধহয়, “যত্ত সব অর্বাচীন! তারাই যেন সব কিছু জানে!!”
এমন নিদারুণ একটা গল্প হাতছাড়া হয়ে যেতে বেজায় নিরাশ হয়ে গেল ৭২ নম্বর ভরা সব বাসিন্দা। কে জানে সে গল্প কোথায় গিয়ে শেষ হত – হয়তো বা ফিদেল কাস্ত্রোকে কীভাবে ঘনাদা সি-আই-এর আততায়ীদের হাত থেকে বার বার বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, সেটা – আমেরিকানরা যে কতবার কতভাবে ফিদেল কাস্ত্রোকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল তার আর হিসেব কে রাখে! অতীতের ডবল এজেন্টের রোল ঘনাদার পক্ষে এমন কিছু অভাবনীয় হত না।
কিন্তু তার বদলে এবার এল খরার পরে খরা – মাসের পর মাস গেল, নতুন কোনো গল্পের (থুড়ি, অভিজ্ঞতার) নাম নেই। শিবু-শিশির-গৌর দিনের পর দিন “তিন-হাত-ডামি” ব্রিজ খেলে খেলে হাল্লাক হয়ে গেল (সুমন ব্রিজ খেলা জানে না, ওটা যেন বড্ড বেশি নগরকেন্দ্রিক কালচার ওর পক্ষে, তাই শিখতেও চায় না) ।
শেষ পর্যন্ত একদিন সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করে রামভুজকে দিয়ে পাঞ্জাবি প্রথায় ‘ব্যাঙ্গন ভর্তা’ – মানে পাঞ্জাবি বেগুন পোড়া – বানিয়ে নিল, আর বানিয়ে মানে কী, তার তরিবতি কী কম, কোথায় টম্যাটো, কোথায় পেঁয়াজ, কোথায় মশলা, সে একেবারে পাঞ্জাবি ধাবা থেকে ধার করে আনা টকটকে লাল মশলা, পেঁয়াজ ভাজা – অর্থাৎ যেসব সরঞ্জাম ছাপোষা বাঙালি রান্নাঘরে ঢোকেই না কোনোদিন, মানে যেসব খাবারের স্বাদ অর্ধেক বাঙালি হালের আগে কোনোদিন চেখেও দেখেনি, সেই সব দিয়ে রামভুজ এক অতি উৎকৃষ্ট পদ বানিয়ে এনে, এক মুখ মিষ্টি হাসি দিয়ে ঘনাদার থালায় পুরো এক হাতা ভরে তুলে দিল প্রথমেই।
এই টেকনিকালার বেগুন প্রস্ততিটি দেখে মনে হল যেন ঘনাদা প্রথমে একটু অবাক হয়ে গেলেন। কিন্তু ৭২ নম্বরের সকলের দৃষ্টি যে তাঁর ওপরেই নিক্ষিপ্ত সেটা ভালো করেই অনুভব করে, বেশ কায়দা করে প্রথমে ডান হাতের তর্জনীটি, তারপরে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি এগিয়ে দিয়ে থালার ওপর থেকে সামান্য এক চিমটে ভর্তা তুলে নিয়ে খুব সাবধানে পর্যবেক্ষণ করতে করতে উন্মুক্ত মুখটির মধ্যে সেটি প্রতিস্থাপন করলেন – ঠিক যেমন করে ‘চন্দ্রায়ন’ থেকে আত্মপ্রকাশ করে ‘প্রজ্ঞান’, চাঁদের দক্ষিণ মেরুর মাটি থেকে ‘রেগোলিথ’-এর ছোট্ট একটু নমুনা তুলে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করবার জন্য তুলে দেয় তার ক্রুসিবল-এর মধ্যে!
অতঃপর ঘনাদার নাসিকারন্ধ্র থেকে শব্দ বেরোল শুধু একটিই – হুম! তারপরে মুখে বলে উঠলেন, “রামভুজ, আর একটু দাও তো বাবা। এইসব অবাঙালি পদ যখন রান্না হয়েছেই, তখন তাড়াতাড়ি শেষ তো করতে হবে!”
আহারান্তে, মানে পুরো দুই বেগুনের করা ভর্তার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ উদরস্থ করবার পরে, সকলের উৎসুক দৃষ্টি এড়াতে এড়াতে, ঠিক বড়ো বড়ো রুই মাছ যেমন প্রায়ই চারটা খেলেও, টোপটা না গিলেই চম্পট দেয়, তেমনি করে, কোনো গল্পের নামগন্ধও না করে, সোজা নিজের শয়নকক্ষের দিকে প্রস্থান করলেন ঘনাদা।
কিন্তু পরের দিনটা ছিল রবিবার। শিবুর আনা গরম গরম জিলিপিগুলো একটার পর একটা মুখে পুরতে পুরতে ঘনাদা কাগজ পড়ছিলেন। তবে ঘনাদার কাগজ পড়া আর আমাদের রবিবাসরীয় পড়া তো আর এক নয়। একজন ডিটেকটিভ যেমন করে খুঁজে বেড়ায় খুনের খবর, তেমনি করে ঘনাদা খুঁজে বেড়ান – কে জানে কীসের খবর – তবে প্রায় তিন চার ঘণ্টা লাগে তাঁর শুধু চতুর্থ পাতাতে পৌঁছতেই! কিন্তু আগের সন্ধেবেলা যদি করা হয়ে থাকে খাঁটি পাঞ্জাবি বেগুন ভর্তা, আর পরের দিন সকালে আসে গরম জিলিপি, তবে তাদের একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া তো হবেই। তাই হঠাৎ উল্লাসিত হয়ে ঘনাদা চিৎকার করে বলে উঠলেন, “আরে, বলে কী, বলে কী – মেদিনা ওটা ঠিইইক করে ফেলেছে! এবারে তো তাহলে ওদের দলবলের নোবেল পাওয়া অবধারিত!”
গৌর-শিবু এবারে একটা জমাটি গল্পের পূর্বাভাস পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিকে ফিরে ঘুরে বসল। শিশির একটা সিগারেটের টিন এগিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, “কে নোবেল প্রাইজ পাচ্ছে ঘনাদা – কে মেদিনা? ‘ওটা’ মানে মেদিনা কী করেছে?”
ঘনাদা নেহাতই অনুগ্রহ করে টিন থেকে একটা সিগারেট নিয়ে জ্বালিয়ে মুখে দিয়ে—মানে কেউ যখন কিছু আদর করে দেয়, তখন তো আর সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে যায় না—তাই সেই সিগারেটে একটা গভীর টান দিয়ে বললেন, “আরে, মেদিনা অ্যাব্লাইকিম্! চিনা বৈজ্ঞানিক!! সেই যে ১৯৯০-এর দশকে দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে, যখন পিটার হিগস আমাকে তাঁর বক্তৃতায় একটু সহায়তা করবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন – মানে, যে কারণে গেছিলাম উত্তর ইংল্যান্ডের ডারহ্যাম ইউনিভার্সিটিতে। বালিকা তখন পিএইচডি করছিলেন ওখানে! আমার তো ওঁকে দেখে তত ভরসা হয়নি প্রথমে, কিন্তু, না, এবারে সে একেবারে ‘গ্লু বল্’-এর অস্তিত্ব প্রমাণ করে দিতে পেরেছে। আরে দারুণ, দারুণ। তাহলে একটা টেলিগ্রাম করে অভিনন্দন পাঠিয়ে দিয়ে আসি তাকে…”
“তাই নাকি, কীসের অভিনন্দন? এখন আর টেলিগ্রাম হয় কিনা জানি না, ঘনাদা, তবে আপনি ই-মেল করতে পারেন” শিবু বলে ওঠে।
পাশ থেকে গৌর বলে, “সেটা আবার কী? ‘গ্লু বল্’ কী হয় ঘনাদা?”
“আরে! ‘সেটা আবার কী হয়’ মানে? কী বলছ তুমি গৌর? এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চারটে মৌলিক শক্তির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী যে শক্তি, যার নাম হল ‘স্ট্রং ফোর্স’ – ওই শক্তির জোরেই তো সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যত কিছু পদার্থ – সূর্য, তারা, গ্রহ, নক্ষত্র, তুমি, আমি, আর, আর, সবজান্তা সুমন পর্যন্ত – সব কিছু যে শূন্যে মিলিয়ে যায়নি বা যায় না, তার একমাত্র কারণ ওই গ্লু বল্, তথা গ্লুয়ন!
ফিদেল কাস্ত্রোর কাহিনিটাকে সেদিন একেবারে গোড়ায় কুড়ুল মেরে নষ্ট করে দেবার পর থেকে সুমন নিজেকে যথেষ্ট সামলে রাখছিল এতদিন। কিন্তু এবারে সে আর থাকতে পারল না। বলে উঠল, “জেঠু, তুমি বলছ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু যা পদার্থ, তার সব কিছুই ওই গ্লু বল্, গ্লুয়ন, এইসব দিয়ে তৈরি করা! মানে, আঠা! হা হা! আঠা বলছ?”
—আঠা।
—হা হা, জেঠু, কীসের আঠা? গঁদের আঠা, না ভাতের আঠা? হাঃ হাঃ হাঃ—সুমন নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে গড়িয়ে পড়ল। অবশ্য তারপরেই হঠাৎ গৌর-শিশির-শিবুর আগ্নেয়গিরিরি মতন উত্তপ্ত মুখগুলোর দিকে চেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার আক্কেল হল। কিন্তু ততক্ষণে যা ক্ষতি হবার তা হয়েই গেছে। জিলিপির ঠোঙাটা পর্যন্ত সঙ্গে না নিয়ে গটগট করে নিজের ঘরের দিকে অর্দ্ধেক রাস্তা পেরিয়ে গিয়েছেন ঘনাদা।
অবশ্য টেবিলে রাখা সিগারেটের টিনটার মধ্যে মাত্র পাঁচ-ছ-টা সিগেরেট পড়েছিল বলে নষ্ট হতে না দেবার জন্য সেটাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু তারপর থেকে আর তাঁর সঙ্গে কারুর মুখদর্শন পর্যন্ত নেই বললেই চলে। ৭২ নম্বর যেন বহিরাতগতর কাছে মুঘল হারেম!
শরীর খারাপের অজুহাতে রামভুজ রোজ তাঁর খাবারটা দরজার সামনে রেখে দিয়ে আসে। এমন কী শ্রাবণ মাসে অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে বলে কয়েকবার বেশ খিচুড়িও রাঁধানো করা হল, সঙ্গে কড়া করে কুচি কুচি কচু ভাজা আর ইলিশ মাছ – মানে কলকাতার কাছে যে কয়েকটা শীর্ণকায় মাছ ধরা পড়ে তাদেরই দুয়েকটি দিয়ে আর কি, বাংলাদেশ থেকে তো আর মাছ আমদানি করা হয় না আজকাল, তাই। কিন্তু তাতেও ঘনাদাকে ‘ঘরছাড়া’ করা গেল না কিছুতেই।
এদিকে সুমনের অবস্থাও তেমন কিছু সুবিধের রইল না। সকলের রাগ তো গিয়ে পড়ল তার ওপরেই! শেষ পর্যন্ত আর ‘প্রেসার’ নিতে না পেরে একদিন সে গৌরকে এসে বলল, “কাকু, আমি কিছুদিন না হয় একটু দেশ থেকে ঘুরেই আসি।” গৌর-শিশির প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠল, “হ্যাঁ হ্যাঁ, যা ঘুরে আয়।” সে আজ বেশ কিছুদিন আগের কথা, তিন-চার হপ্তা তো হবেই।
তবে বেশি গুমোট হলে অবশ্য শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি না এসে থাকতে পারে না। ৭২ নম্বরের ইতিহাসের এই অত্যাধুনিক পরিচ্ছেদেও ঠিক তাই হল। সেদিনটাও একটা রবিবার ছিল। যদিও নাট্যমঞ্চের প্রধান অতিথির উপস্থিতিটা অনিশ্চিত জেনে শিবু আর সেদিন ভোলা ময়রার দোকানের গরম জিলিপি কিনতে যাবে না বলে ঠিক করেছিল। তাই বোধহয় আলসেমি করে বিছানা ছাড়তে একটু দেরি করছিল। আর অন্যদেরই বা কী তাড়া, সপ্তাহের একটি মাত্র দিন, যেদিন বেলা পর্যন্ত ঘুমোলে কারুর কোনো ক্ষতি হয় না, সেদিন কী দরকার তাড়াহুড়ো করে বিনা কারণে শয্যাত্যাগ করবার? রামভুজকে দরজা খুলে দিতে হবে? কিন্তু সে তো কাল রাত্রেই জেনে গিয়েছিল যে এইদিন বাবুরা একটু বেশিক্ষণ ঘুমোবেন। কাজেই সকাল সাতটা পেরিয়ে গেলেই বা কী, আর দশটা বেজে গেলেই বা কার কী!
কিন্তু সবসময় কী সবকিছু ঠিকঠাক চলে? অকালকুষ্মাণ্ড যেমন মাঝে মাঝে অত্যন্ত অকালে আগমন করে ফেলে, তেমনি ভাবেই, মানে ঠিক কাকভোর না হলেও, খবরের-কাগজের-ফেরিওয়ালা-ভোর হতে না হতেই, সদর দরজায় খটাখট করে কড়া নড়ে ওঠে জোরে জোরে!
“কে রে হতচ্ছাড়া!” শিবুকেই উঠতে হল, কারণ দরজার সবচেয়ে কাছে শোয় সেই! তাই তার বিরক্তির আর সীমা রইলনা “কোথায় রোববার একটু দেরি পর্যন্ত জিরোবো, তার উপায় নেই! সাত সকালে কড়া নেড়ে নেড়ে কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে একেবারে! ক্কে শা…”
কিন্তু দরজা খুলতেই, ঝাঁকানো শ্যাম্পেন বোতলের ছিপি খোলার মতন করে একরাশ আবেগ আর উচ্ছাস ঝলকে উঠল সুমনের মুখ থেকে, “শিবুকাকুউউউ, কেমন আছ? তোমাদের যা মিস্ করেছি এতদিন ধরে তা আর বলবার নয়! জেঠু কই – জেঠুউউউ, ঘনাজেঠু, দ্যাখ তোমার জন্য কী এনেছি…”
“এই, আস্তে কথা বল হতভাগা, সবাই এখনও ঘুমুচ্ছে…” ধমক দিয়ে ওঠে শিবু।
হইচই শুনে ততক্ষণে অবশ্য সবাই যে যার কোটর থেকে বেরিয়ে পড়েছে, এমনকী, মায় ঘনাদা পর্যন্ত! ঘনাদাকে দেখে সকলেই একটু অবাক, কারণ তাঁর রাগ-থার্মোমিটারের পারদটা সাম্প্রতিককালে যে কোথায় গিয়ে ঠেকে রয়েছিল তা তো আর কেউ আন্দাজ করতে পারেনি আগে থেকে, কিন্তু তবু সুমনের মতন উচ্ছসিত আর কেউ হয়ে ওঠেনি। সে একলাফে দৌড়ে গিয়ে তো প্রথমেই ঘনাদার পা ছুঁয়ে প্রণাম জানাল। তারপরে একেবারে তাঁর হাত ধরে টানতে টানতে আরাম কেদারাটার ওপরে বসিয়ে দিয়ে বলল, “দাঁড়াও জেঠু, তোমার উপহারটা থলের মধ্যে থেকে বার করি…”
সুমন থলে হাতড়াতে শুরু করলে শিবু গৌরের দিকে তাকিয়ে খাটো গলায় বল, “সুমনের হলটা কী? ওর এমন রূপ তো আর আগে কোনদিন দেখিনি – জানি সেদিনের আহাম্মকিটার প্রায়শ্চিত্ত করবার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু তাই বলে…”
গৌর শিবুর কথা লুফে নিয়ে বলল, “তাই না তাই! বাড়াবাড়ি! টানাটানিতে যে ঘনাদা আবার রেগে ফেটে পড়েননি, তাই রক্ষে! নয়তো এতক্ষণে যা তা অবস্থা হয়ে যেতে পারত।”
ঘনাদা অবশ্য মনে হল এই অকালকুষ্মাণ্ডটির এই অপ্রত্যাশিত অভিনিবেশটি বেশ উপভোগই করছিলেন। তাই তাঁর চটে ওঠবার কোনো লক্ষণ-ই দেখা গেল না। অবাক কাণ্ড!
সুমন থলে হাঁটকে গিফ্ট পেপারে মোড়ানো একটা লম্বাটে মতন জিনিস বার করে ঘনাদার হাতে দিল। ঘনাদা কৌতূহলি হয়ে সেটা দু-তিন বার এহাত-ওহাত করে বললেন, “এটা কী এনেছ?”
“আরে, খুলেই দেখো না কেন জেঠু?” সুমন মুচকি হেসে বলল “মোড়কটা খোল!”
গৌর একটু সন্দিগ্ধ হয়ে বলল – “জোক গিফ্ট নয়তো সুমন? ঘনাদা মোড়ক খুললেই কিছু পট্কার মতন ফাটবে না তো? তোকে কিছু বিশ্বাস নেই – ঘনাদা কিন্তু ওসব পছন্দ করেন না।”
“আরে দূর, ওসব কিছু নয়, মোড়কটা খোলো তো!” সুমন আশ্বাস দিয়ে বলল।
শেষ পর্যন্ত ঘনাদা মোড়কটা খুলে ফেলায় দেখা গেল ভেতরে একটি সরু, লম্বা প্লাস্টিকের কেস, আর তার মধ্যে ভরা একটি চুরুট। “চুরুট?” ঘনাদার গলায় বিস্ময়!
শিবুও বলে উঠল, “চুরুট নাকি?”
“হেঁ হেঁ বাবা, চুরুট তো বটেই, তবে যে সে চুরুট নয়! এক্কেবারে খাঁটি হাভানা চুরুট…” গভীর আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বলে উঠল সুমন “তার ওপরে আবার কমরেড ফিদেল কাস্ত্রোর নিজের হাতে দেওয়া উপহার”
“বলিস কী রে, কাস্ত্রোর দেওয়া উপহার? কাকে? কেমন করে?” গৌর জেরা করে।
“আরে, এবারে দেশে গিয়ে আমি বড়ো পিসিমার বাড়ি গেছিলাম। পিসিকে ঘনা জেঠুর সঙ্গে কমরেড কাস্ত্রোর আলোচনার কথা বলছিলাম। পিসি বলল, ‘ওঃ, সেদিনের কথা এখনও জ্বলজ্বল করছে আমার মনের মধ্যে! ওই দেখ্না, ওই কাচের আলমারিতে একটা চুরুট রাখা আছে। ওয়েটিং রুম থেকে প্লেনের দিকে যাবার আগে ওপরের বারান্দা থেকে কতগুলো চুরুট, জ্যাকেটের পকেট থেকে বার করে আমাদের মতন সব ভক্তদের দিকে তাক করে সেগুলো ছুড়ে দেন কাস্ত্রো! আমি তো সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে গিয়ে গোটা দুয়েক তুলে আমার বটুয়াতে ভরে ফেলেছিলাম। তার একটা তোর পিসো একদিন খেয়ে ফেলল – আর ওই অন্যটা পড়ে আছে এখনও’”
ঘনাদা বিস্মিত হয়ে বললেন, “এইটা সেই চুরুটটা নাকি?” তারপরে প্লাস্টিকের কেস থেকে বার করে সেটাকে একটু নাড়াচাড়া করে নাকের কাছে নিয়ে গিয়ে শুঁকে বললেন, “হ্যাঁ, ঠিক সেই বিখ্যাত ‘হাভানা সিগার’-এর মন মাতানো গন্ধ। আমারগুলো তো কবে শেষ করে ফেলেছি! কিন্তু তোর পিসি দিয়ে দিল তোকে এটা?”
“সহজে কী দেয় জেঠু? অনেক তেল দিলাম, ওর নাতিকে একটা খেলনা কিনে দিলাম, একটা প্লাস্টিকের ‘লেডি বাগ’ কিনে দিলাম, তোমার কথা বললাম – তবে নাকি…”
সুমনের কথা কিন্তু শেষ হতে পারলনা; তার আগেই শিবু ওর কনুই ধরে এককোনে টেনে নিয়ে গিয়ে বেশ কড়া সুরে জিজ্ঞেস করল, “এসব কী শুনছি সুমন? সত্যি, না ভাঁওতা মারছিস?”
সুমন আস্তে করে কনুইটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, “নো আস্ক্, নো টেল্, কাকু!” তারপরে একটু মুচকি হেসে নিজের পোঁটলাটা তুলে নিয়ে শোবার ঘরের দিকে চলে গেল।
ঘনাদা অবশ্য সেদিকে খেয়ালই করছিলেন না। তিনি শুধু ওপরের ঠোঁটটা একটু উঁচু করে, সেটার ওপরে চুরুটটা বসিয়ে নাকের নীচে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কেবল তার ঘ্রাণাস্বাদনই করতে থাকলেন। এরকমভাবে যে কতক্ষণ চলত তা ঠিক বলা যায় না, কারণ এই অবস্থায় কী বলা উচিত তা গৌর-শিশির-শিবু কেউই ভেবে পাচ্ছিল না। তবে কিছুক্ষণ পরে হাতমুখ ধুয়ে, জামা বদলে, সুমন আবার বৈঠকখানা ঘরে ফিরে এল। আর তারপরে ঘনাদার চেয়ারের কাছে, মাটিতে-পাতা ফরাসটার ওপরে গিয়ে বসে আবদার জানাল, “জেঠু, আমি কিন্তু এবারে সেই আঠার “গল্প”-টা শুনব”
ঘনাদা একটু চমকে উঠে (সত্যিই কী?) বললেন, “আরে দূর, ওই গপ্পো আবার কী শুনবি? আর সেটা তো গপ্পো নয় – কেবল জীবনটাকে একটুখানি ফিরে দেখা, মানে আমার এই দুটো চোখের সামনে দিয়েই কত কিছু যে ঘটতে দেখেছি, এই আর কি! সেগুলো আবার বার বার করে কী বলব?”
সুমনের আবদার করবার টেকনিক দেখে গৌর-শিশির-শিবু সবে একটু উৎসাহিত হতে শুরু করেছিল। কিন্তু ঘনাদার কথা শুনে আবার একটু প্রমাদ গুনল। শেষে আবার কেঁচে যাবে না তো? শিশির আর দ্বিধা না করে, চোখের নিমেষে পকেট থেকে লাইটারটা বার করে জ্বালিয়ে, সোজা ঘনাদার নাকের কাছে নিয়ে গেল। ঘনাদা বললেন, “ও, কী? চুরুট ধরাবার জন্য। বাঃ, বেশ বেশ, ব্রাভো!”
ঘনাদা প্রগাঢ়ভাবে চুরুটটায় কয়েকটা টান দিতেই বৈঠকখানাটা তামাকের খুশ্বুতে একেবারে ভরে উঠল। তিনি দু-চারটে ধোঁয়ার গোলক বানিয়ে অলসভাবে বললেন, “তাহলে কী শুনবে বল।”
গৌর একমুখ হাসি নিয়ে বলল, “ওই যে, যে চিনা বালিকার কথা বললেন, কী যেন নাম, সে আবার নোবেল পাবে কেন ভাবছেন?”
“ও, মানে মেদিনা? না না, সে তো আর বালিকা নেই, সে এখন রীতিমতো বড়ো বৈজ্ঞানিক! একসময়ে তো একটু আধটু পড়াশুনা করিয়েছি, তাই শিষ্যা বলে ওকে নিয়ে গর্ব বোধ করি এখন।” ঘনাদা একটু অন্যমনস্ক হয়েই উত্তর দিলেন “ওর কথা শুনবে?”
“আলবৎ” গৌর-শিশির-শিবু তিনজনেই ঘনাদাকে ঘিরে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল ফরাসটার ওপরে, যদিও বাতের ব্যথার জন্য আজকাল সাধারণভাবে ওরা কেউই আর হাঁটু মুড়ে বসতে চায় না। কিন্তু সম্প্রতি অনেকগুলো পর পর “মিসফায়ার”-এর পরে আর ঘনাদাকে পালিয়ে যাবার ফাঁক দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, তাই।
আর সুমন বলল, “হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর কথা শোনবার জন্যই তো মুকিয়ে আছি সেদিন থেকে, জেঠু…”
“আচ্ছা বলছি। কিন্তু ওর কথাটা বলতে গেলে একটু গৌরচন্দ্রিকা করে নিতে হবে, ধৈর্য থাকবে তো।”
“নিশ্চয়ই থাকবে।” সবাই সমস্বরে বলে উঠল।
“হাভানা চুরুটটা ফুরিয়ে গেলেও আমার কাছে নতুন এক টিন সিগারেট আছে।” শিশির আবার তার ওপরে যোগ করে দিল।
“বেশ বেশ। তাহলে গোড়ার কথাটাই বলি।” ঘনাদা একটু গম্ভীর হয়ে বললেন “আমার কিন্তু প্রথম ফিজিক্সে উৎসাহ হয় ছোটোবেলায় উপনিষদ পড়তে পড়তেই…!”
“উপনিষদ? আপনি আর উপনিষদ…উফ্ উফ্…” শিবু হয়তো একটু তাচ্ছিল্য করেই কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ গৌড়ের একটা রামচিমটি খেয়ে কাতরে উঠল।
আর শিবুর মুখের কথাটা মুহূর্তে লুফে নিয়ে গৌর বলল, “ও তাই নাকি? কোন উপনিষদটা ঘনাদা?”
ঘনাদা বোধহয় একটুখানি সন্দিগ্ধ হয়ে বিবেচনা করবার চেষ্টা করছিলেন শিবু-গৌরের খুনসুটিটার কারণটা ঠিক কী, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু না বলে শান্তভাবেই উত্তর দিলেন, “ওই তো সামবেদের ছান্দোগ্য উপনিষদ, ওখানেই তো বলে দেওয়া আছে অদ্বৈতবাদের মূল সূত্র -তৎ ত্বং অসি! এই যে অতি বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তার যে অন্তর্নিহিত সত্ত্বা, যাকে বলা হয় ‘আত্মন’, সেই প্রকাণ্ড পুরুষ, সেই অননুমেয় শক্তি, আর সামান্য আমি, আর জগতের যত জড় ও জীব – আমরা সবাই বিভেদহীনভাবে সেই সত্ত্বার সঙ্গে একাত্ম!”
“তাহলে জেঠু, আত্মন যদি সেই অসীম শক্তি, উপনিষদের ‘ব্রাহ্মণ’ তবে কী? ওখানে তো ব্রাহ্মণ কথাটির উল্লেখ আছে।” সুমন জিজ্ঞেস করে।
“আরে, তুমি তো লাখ টাকার প্রশ্ন করলে হে সুমন। এইসব প্রশ্নের উত্তর পেতে গিয়েই তো হাজার হাজার বছর ধরে অগণিত সাধু, সন্ত, রাজা, মহারাজা, ধনী, গরীব, সবাই সংসার ছেড়ে ধ্যানে গিয়ে বসেছে। কিন্তু মানুষের সীমিত মানসিক ক্ষমতায় এইসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব কিনা তা বলতে পারব না। তবে উপনিষদের ‘ব্রাহ্মণ’ তো আর জাত নির্দেশক নয়, কারণ সেসব সংকীর্ণতা উপনিষদের যুগের অনেক পরে এসেছিল। তবে একরকমভাবে চিন্তা করলে বলা যায় যে যেহেতু আত্মন সর্বব্যাপী, অননুমেয়, এবং আত্মন ছাড়া আর সবই মায়া, সেহেতু আত্মনের প্রকৃত স্বরূপ অনুভব করতে হলে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সাধনা করতে হবে, অন্তর্মুখী হয়ে বসতে হবে, তবে তো! আত্মন আমাদের অভ্যন্তরের গভীরেই বিরাজমান। এটাকেই আমরা সাধারণভাবে ভগবান বলি। সেই সঙ্গে এটাও অনুভব করতে হবে যে ‘ব্রাহ্মণ’ সেই ‘আত্মন’-এরই পরিপূর্ণ অঙ্গ। আর ‘আত্মন’-এর অঙ্গ হিসেবেই, সেই সত্ত্বা বিশ্ব চরাচরের একটি নৈর্ব্যাক্তিক, সর্বব্যাপী সত্বা। এই সত্ত্বাই যেন আমাদের যাবতীয় ইন্দ্রিয়কে বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করেন।”
“বাপরে, ঘনাদা, আমার তো শুনে মাথা টিপটিপ করতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। এর সঙ্গে আপনার ছাত্রী, সেই চিনা বৈজ্ঞানিক আর আঠা-র কী সম্পর্ক?” শিবু একটু অধৈর্য হয়ে পড়ে।
“আরে বলছি বলছি। সম্পর্ক আছে একটা বৈকি! তবে শুধু এইটুকু বলেই প্রসঙ্গটা বদলাই যে আমি উপনিষদেই প্রথম পড়ি যে, ‘প্রকৃতি’ বা ‘পদার্থ’, অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে ‘mass’, তার সঙ্গে ‘শক্তি’, মানে এনার্জি-র একটা ওতপ্রোত সম্পর্ক আছে। আর আমরাও জড়পদার্থ বা প্রকৃতিরই অঙ্গ। এই প্রকৃতি আর শক্তির মধ্যের সম্পর্কটাই আইনস্টাইন বহু সহস্র বছর পরে এসে, আমাদের যুগে আবার বিজ্ঞানের আলোকে আমাদের বুঝিয়েছেন ভালো করে।”
“ও, মানে সেই E=MC2 ইকুয়েশনটা?” গৌর জিজ্ঞেস করে।
“হ্যাঁ, তা বলতে পার একরকম।” ঘনাদা ঘাড় নেড়ে সম্মতি দেন “উপনিষদে শ্বেতকেতুকে তো সেটাই শেখানো হয়েছিল। তাঁকে একটা ডুমুর ফলকে কেটে কেটে, ক্রমান্বয়ে ছোটো থেকে আরও ছোটো টুকরো করতে দেওয়া হয়েছিল। শেষে বীচির অংশে পৌঁছে গিয়ে, সেগুলো কাটতে কাটতে এত ছোটো হয়ে গেল যে তারপরে তাদের আর খালি চোখে দেখাই গেল না। তখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে অদৃশ্য হয়ে গেলেও, অংশগুলো তো তবুও বিরাজমান। সেই অংশ থেকেও তো বিশাল বিশাল মহীরুহ জন্মায়! অতএব সেখানে যে প্রাণসত্ত্বা বিরাজমান, সেই অদৃশ্য, অভেদ্য শক্তিই হলেন জড়বস্তুর সার। তোমাদের কারুর মনে আছে এই গল্পটা?”
গৌর বলল, “হ্যাঁ, গল্পটা একটু শোনা শোনা লাগছে। ঠাকুমা মাঝে মাঝে ঘুম পাড়াবার সময় উপনিষদ আর পঞ্চতন্ত্রের গল্পও বলতেন।”
“ও, তাই নাকি? আর আমি যখন এই গল্পটা প্রথম পড়ি, তখন আমি সবে ফিজিক্স পড়তে শুরু করেছি। অ্যাটম আর সাব-অ্যাটমিক কণাগুলোর কথা পড়তে শুরু করেছি। কাজেই বুঝতেই পারছ, গল্পটা যে দর্শন আর বিজ্ঞানের একটা সঙ্গমস্থলে পড়ে, সেটা বুঝে নিতে একটুও সময় লাগেনি আমার।”
ঘনাদার চুরুটটা নিভে আসছিল। তিনি একটু আগুন চেয়ে নিয়ে দ্বিতীয় দফায় আরেকটা গভীর টান দিলেন। আবার একরাশ চুরুটের সুরভি। “হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম?” কয়েকটা ধোঁয়ার রিং ছাড়তে ছাড়তে ঘনাদা জিজ্ঞেস করলেন।
“আপনি বিজ্ঞানের কথা বলছিলেন – বৈজ্ঞানিক আঠার—” শিশির ধরিয়ে দিল।
“ও হ্যাঁ। মেদিনার রিসার্চের কথা। জান তো, গত একশো-দেড়শো বছরে ফিজিক্স খুব লাফিয়ে লাফিয়ে উন্নতি করেছে। বিশেষ করে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, পার্টিকল ফিজিক্স, কোয়ান্টাম ফিজিক্স, ইত্যাদি।”
“হ্যাঁ, হেডরন কোলাইডার, যেটা জেনিভায় তৈরি করেছে সাহেবরা। সার্ন। আমাদের বহরমপুরের একজন মাস্টারমশাই টাটাতে কাজ পাবার পর সেইখানে প্রায়ই যান।” সুমন কমেন্ট করল।
ঘনাদা শুধু একটু প্রশ্রয়ের হাসি দিলেন শুনে। কিন্তু গৌর একটু বিভ্রান্ত হয়ে বলল, “টাটা মোটরস? তারা জেনিভায় কী করে?”
ঘনাদা তাড়াতাড়ি হেসে বললেন, “না, না, টাটা মোটরস নয়। ও বলছে টাটা ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কথা। কিন্তু ওটা শুধু সাহেবরাই করেনি রে, ভারত সরকারও সার্নের কিছু রিসার্চের আংশিক খরচ বহন করে। তাই আমাদেরও একটু মালিকানা আছে ওটাতে। সেইজন্য অনেক ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরাও ওখানে যাওয়া আসা করে সার্নে।”
“সার্নে ফিজিক্সের কী কাজ হয়?” গৌর জিজ্ঞেস করে।
ঘনাদা অনুকম্পা করে বলেন, “দাঁড়াও একটু। বুঝিয়ে বলছি। গোড়া থেকেই তো ফিজিক্সের প্রধান কাজ ছিল আমাদের যে দৃশ্য পৃথিবী, তাতে যত ঘটনা ও প্রতিঘটনা, সেটা কী করে, কোন সূত্র মেনে চলে, তার অধ্যয়ন করা। তোমরা বলতে পার যে তার কী দরকার ছিল? ফিজিক্সের ‘ফ’ জানবার আগেও তো আমরা ছিলাম, বেশ দিব্বি ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকতাম। মাঝে মাঝে পশু শিকার করতাম। চন্দ্রগ্রহণ কেন হয় জানতাম না। কিন্তু সব কিছু জানবার কী দরকার ছিল সত্যিই?”
“এটা একটা দারুণ প্রশ্ন তুলেছ জেঠু! কেন জানতে চেয়েছি আমরা? কেন?” সুমন জিজ্ঞেস করে।
ঘনাদা বলেন, “এর উত্তর হল, আমরা মানুষ হয়ে জন্মেছি বলে। হাতি বা সিংহ হয়ে জন্মালে তো আর এইসব নিয়ে মাথা ঘামাতাম না! কিন্তু ওই যে, উপনিষদে বলেছে – ব্রাহ্মণ – যার আসল মানে হচ্ছে শিক্ষার্থী! আমাদের মানসের মধ্যের সেই শিক্ষার্থী অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু – এইভাবেই আমরা তৈরি। যাই হোক। উনিশশো শতকের গোড়া অবধি নিউটনের ‘ল’জ অব মোশন’ মোটামুটি ঠিক ছিল। দৃশ্য পৃথিবী ও তার আশপাশের গ্রহ উপগ্রহ কোন নিয়মে চলে, এইসব বেশ ভালোই বুঝতে পেরেছিলাম আমরা। তারপরে শতাব্দীর প্রথম দিকে আইনস্টাইন সাহেবের রিলেটিভিটি থিয়োরি সামনে আসাতে, সেই নিয়মের বাঁধুনিটা আরও একটু পোক্ত হল। নিউটন-আইনস্টাইনের সূত্রগুলোকে বলা হল ‘ক্লাসিকাল ফিজিক্সের ভিত্তিপ্রস্তর।”
“কিন্তু সমস্যা হল, যখন আমরা তার কিছুদিন পরে অনু-পরমাণুগুলোকে শ্বেতকেতুর ডুমুর কাটার মতন করে ভেঙে ভেঙে, আরও সূক্ষ্ম জগতে গিয়ে পৌঁছলাম। তখন ভালো করে অধ্যয়ন করে দেখা গেল যে ক্লাসিকাল ফিজিক্সের সূত্রগুলো সূক্ষ্ম জগতের সঙ্গে আর ঠিক মিলছে না। তখন ১৯২৫ সালে জার্মান পণ্ডিত, ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ, কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সূত্র তৈরি করলেন। সেই সূত্র আর ক্লাসিকাল ফিজিক্সের সূত্র মিলিয়ে আমরা সামনে এগোতে থাকলাম। আমাদের অধ্যয়নের যন্ত্রপাতি আরও শক্তিশালি হল। এইসব মিলিয়ে, ১৯৩০ আর ১৯৭০-এর মধ্যে হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক মিলে ভৌতিক পদার্থ, মানে ‘ম্যাটার’-এর প্রকৃত গঠন নিয়ে অনেক তথ্য আবিষ্কার করে ফেললেন। সেইসব তথ্য মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যত পদার্থকে আমরা শনাক্ত করতে পেরেছি এ পর্যন্ত, তারা সবাই একটা গোনাগুণতি সংখ্যার মৌলিক কণা দিয়ে বিভিন্ন রকম ভাবে মিশিয়ে তৈরি। এবং ওই অতি সূক্ষ্ম জগতের মধ্যে তাদের অস্তিত্ব নিয়ন্ত্রণ করে চার ধরনের মৌলিক শক্তি মিলে। এটাকেই এখন বলা হয় “স্ট্যান্ডারড মডেল অব পার্টিক্ল ফিজিক্স।”
গৌর আর শিশির মিলে এবারে বেশ একটু মাথা চুলকোতে শুরু করল। তাই দেখে ঘনাদা একটু বিরতি দিলেন। সুমন বলল, “বুঝেছি জেঠু। পার্টিক্ল ফিজিক্স হচ্ছে পরমাণুর থেকেও যে সূক্ষ্ম জগৎ, সেই জগতের অধ্যয়ন। আমাদের মাস্টার মশাইও জানি যে পার্টিকল ফিজিক্স নিয়েই কাজ করেন। তা তুমি যে বললে, গোনাগুণতি সংখ্যার মৌলিক কণা দিয়ে সবকিছু তৈরি। সেই কণাগুলো কারা”
“দুই ধরনের মৌলিক কণা আছে, তাদের বলে কোয়ার্ক আর লেপটন্স। তারা দুজনেই তিন রকমের হয় – স্টেবল, বা স্থিতিশীল কণা, এবং দুই ধরনের কম-স্থিতিশীল কণা। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যতকিছু পদার্থ আছে তারা সব ওই স্থিতিশীল কণা দিয়েই তৈরি, কারণ দুই ধরনের কম-স্থিতিশীল কণাগুলো শেষ পর্যন্ত কিন্তু নিজেদের কিছু ওজন হারিয়ে ফেলে স্থিতিশীল কণা হয়েই দাঁড়ায়।”
“আর জেঠু, তুমি যে সূক্ষ্ম জগতের চার ধরনের শক্তির কথা বললে, সেগুলো কী”
“তারা হল, জোরালো, বা স্ট্রং ফোর্স; দুর্বল, বা উইক ফোর্স; ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স; আর গ্র্যাভিটি, বা মাধ্যাকর্ষণ। স্ট্রং বা উইক ফোর্স, দুটোই খুব অল্প পরিসরের মধ্যে কাজ করে, মানে পরমাণুর পরিসরের মধ্যেই তাদের কাজ। কিন্তু ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক আর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিগুলো অন্য দুই ধরনের শক্তির চেয়ে অনেক দুর্বল হলেও, তাদের পরিসর সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী।”
“বুঝেছি। এই পর্যন্ত শিখেই শ্বেতকেতু মূর্ছা গিয়েছিল। তাই উপনিষিদে আর বেশি কিছু বলেনি… ডুমুরের বীজগুলো কেটে অদৃশ্য হয়ে যাবার পরে বোধহয় আর কিছু শেখায়নি। হাঃ হাঃ।” গৌর বোধহয় নিজের মানসিক অবস্থাটাই একটু বর্ণনা করে দিল।
শিশিরও একটু হেসে ফেলল, “হেঃ হেঃ। আসলে তখন তো আর মাইক্রোস্কোপ বা দূরবীন ছিল না। তাই খালি চোখে দেখতে না পাবার পরেই ক্লাশ শেষ হয়ে যাবার ঘণ্টাটা বেজে গেছিল। হেঃ হেঃ।”
শিবু প্রমাদগুণে তাড়াতাড়ি ধমক দিয়ে বলল, “এই, বাচালতা করিস না তোরা! ঘনাদা আজ সময় নিয়ে একটু পার্টিকল ফিজিক্সের সারমর্ম বোঝাচ্ছেন আমাদের, একটু সময় নিয়ে মন দিয়ে শোন।”
কিন্তু বোধহয় চিন্তার কারণ ছিল না, কারন ঘনাদা শিশির-গৌরের তির্যক মন্তব্য শুনেও কর্কশ কিছু বললেন না। শুধু একটু মোলায়ামভাবে বললেন, “আরে উপনিষদ তো আর বটতলায় ছাপা পাঠ্যপুস্তক ছিল না! এটা ছিল আমাদের পার্শ্ব-পরিবেশকে একটু দার্শনিকভাবে বিশ্লেষণ করবার প্রচেষ্টা মাত্র। কিন্তু সেইসব দার্শনিক চিন্তাধারা এতই প্রগতিশীল ছিল যে ওখানে সেই হাজার হাজার বছর আগে যেসব কথা বলা আছে, তাই পড়ে ও শুনে কিছু কিছু প্রথম সারির আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও, যেমন হাইজেনবার্গ, অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পারমাণবিক জগতের নিয়ম-পন্থার গাণিতিক বিশ্লেষণ করতে করতে যে সব ‘সত্য’ তাঁরা তখন খুঁজে পাচ্ছিলেন, সেগুলো তাঁরা নিজেরাই মন খুলে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কারণ তাঁদের বিশ্লেষণের কিছু কিছু তাৎপর্য, সাধারণ বুদ্ধিতে তেমন একটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছিল না। ঘটনাক্রমে এই সব ব্যাপারে উপনিষদের কিছু কিছু লেখার ব্যাখ্যা শুনে বা পড়ে, তাঁরা আশ্বস্ত হতে পেরেছিলেন যে সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা না গেলেও, তাঁদের আবিষ্কারগুলোর দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তিও কিছু আছে। এমনকী স্বয়ং আইনস্টাইনও একটা ব্যাপারে খটকা লাগার জন্য বেশ কয়েকবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন – ওঁর সঙ্গে উপনিষদের কিছু কথা মিলিয়ে নিতে। কিন্তু সে গল্প আরেকদিন বলব।”
“কিন্তু জেঠু, আঠা? আঠার গল্প কিন্তু আজই শুনব।” সুমন সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়।
ঘনাদা হেসে বললেন, “হ্যাঁ, সেই দিকেই তো যাচ্ছি। কিন্তু এই গৌরচন্দ্রিকাটা না করে নিলে তোমরা আঠার মাহাত্ম্য ঠিক বুঝবে না।”
“বেশ, তাহলে এবার বলো! সেই চিনে বালিকাটি এর মধ্যে কী করে আসছে?” সুমন জোর করে।
শিবু একটু ধমকে বলে, “বালিকা নয়, বৈজ্ঞানিক! সে নোবেল প্রাইজ পেতে চলেছে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই। ঠিক কিনা? ঘনাদা?”
ঘনাদা সায় দিয়ে বললেন, “হ্যাঁ, একেবারে ঠিক। কেন বলছি শোন। পারমাণবিক জগতের মধ্যে যে চারটি শক্তি বিরাজ করে, তারা আর একধরনের কণার মাধ্যমে তাদের কাজ চালায়। কিন্তু এই কথাটা বলে তোমাদের আরও বিভ্রান্ত কেন করলাম? কারণ গাণিতিক বিশ্লেষণ করে এই ধরনের কিছু কিছু কণা, যারা আসলে শক্তির দালাল, যদিও ভদ্র সমাজে তাদের বলতে হয় ‘শক্তিকণা’, তাদের আবিষ্কার করেন আমাদেরই মতন একজন রক্তমাংসের বঙ্গসন্তান – ড. সত্যেন বোস। তাঁর সম্মানে এইসব শক্তিকণাদের বলা হয় ‘বোসন’। বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিকস-এর নাম শুনেছ বোধহয়। সেইটা আমাদের বড়োই গর্বের বিষয়।”
শিবু বলল, “আমি কিন্তু এতশত জানতামই না, ঘনাদা।”
ঘনাদা বললেন, “সেই জন্যই তো বলা। চার ধরনের পারমাণবিক যে শক্তিগুলোর কথা একটু আগে বলছিলাম, তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব শক্তিকণা বা দালাল আছে। ইলেক্ট্রোম্যাগ্নেটিক শক্তির দালাল হচ্ছে ‘ফোটন’ বা ‘আলোর কণা’। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দালালের নাম দেওয়া হয়েছে ‘গ্র্যাভিটন’। কিন্তু সে দালালের এখনও পর্যন্ত টিকিও দেখা যায়নি, সে কেবল গণিতের জগতে২ই আছে। যে বৈজ্ঞানিক প্রথম তাদের শনাক্ত করতে পারবেন, তিনি নিঃসন্দেহে নোবেল পাবেন।”
সুমন প্রশ্ন করল, “কিন্তু শনাক্তটা করবে কী করে? তারা নিশ্চয়ই খুবই ছোট – মাইক্রোস্কোপেও তো দেখা যাবে না বোধহয়? যাবে?”
ঘনাদা হেসে বললেন, “এবারে আবার একটা লাখ টাকার প্রশ্ন করলে হে তুমি। তুমি তোমার মাস্টার মশাইয়ের কাছে যাও টাটাতে, তোমার মধ্যে জানার ইচ্ছেটা আছে সুমন! ব্রাভো!”
সুমন একটু লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলল, “কী যে বল জেঠু”
ঘনাদা একটু প্রশ্রয়ের হাসি দিয়ে বললেন, “ঠিকই বলছি আমি। সঠিক প্রশ্ন করবার ক্ষমতাটাই তো শিক্ষা এবং আবিষ্কারের প্রথম ধাপ! তাহলে তোমাকেই জিজ্ঞেস করি – একটা জিনিস যদি সহজে বোঝা না যায় যে সেটা কীভাবে কাজ করে, তখন তু্মি কী করবে? একটু ভেবে বল দেখি!”
সুমন মনে হল এবারে একটু বিপদেই পড়ল। একদিকে ঘনাদার প্রশংসায় সে খুবই খুশি। কিন্তু কী উত্তর দেবে? একটা মার্চেন্ট অফিসের ছাপোষা কেরানি সে – ৭২ নম্বরের মেসে থাকে – গত দু-মাসের ভাড়া এখনও দেওয়া বাকি, ছেলে-বউকে রেখে আসতে হয়েছে বহরমপুরে – সে এইসব বাঘা বাঘা বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে কী মতামত দেবে? পাগল নাকি?
কিন্তু সবাই তখন তার দিকেই তাকিয়ে আছে, আর ঘনাদার মুখে মৃদু মৃদু হাসি। সুমন তো ঘামতেই শুরু করে দিল! শেষ পর্যন্ত একটু তোতলাতে তোতলাতে উত্তর দিল, “আমি ঠিক কী করে বলি জেঠু, আমার তো তেমন লেখাপড়া নেই। তবে এইবারে বড়োপিসির বাড়ি গিয়ে একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। পিসির নাতির জন্য একটা খেলনা নিয়ে গিয়েছিলাম তো – চাবি দেওয়া একটা বড়ো ‘লেডি বাগ’। চাবি দিয়ে মাটিতে ছেড়ে দিলেই সে দিব্বি চোঁ চোঁ আওয়াজ করে এদিক ওদিক চলে। নাতিটির পাঁচ বছর বয়স। তা ওকে একটু খেপাবার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, ‘এই, এটা কী করে চলে বল্ত? এটা তো জ্যান্ত নয়!’ সে মুখ বেঁকিয়ে বলল, ‘এটা জ্যান্ত নয় আমি জ্জানি! এটাকে চাবি দেওয়া হয়েছে বলে এটা চলে, বুঝলে’? আমি আবার মজা করে বললাম, ‘সে তো আমিও জানি। কিন্তু চাবি দিলেই বা কী হয় টোকো? কী করে চলে?’ টোকো কিন্তু আর কিছু বলল না, বরঞ্চ একটু রাগ দেখিয়ে উঠে চলে গেল। আমিও আর কিছু বলিনি। ভুলেই গিয়েছিলাম সেই ব্যাপারটা। হঠাৎ প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে একটা হাতুড়ি আর তোবড়ানো খেলনাটা হাতে নিয়ে টোকো আমার কাছে এসে ঘাড় গোঁজ করে বলল, ‘আমি জানি কী করে চলে এটা। আমি ভেঙে ভেতরে দেখেছি, এই দ্যাখ!’ বলেই সে আমাকে ভাঙা স্প্রিংটা দেখিয়ে বলল, এই লোহাটা চাবি দিলে গুটিয়ে যায়। কিন্তু ছেড়ে দিলে লোহাটা আবার খুলতে থাকে। তখন চাকা চলে…”
ঘনাদা এতক্ষণ বেশ মন দিয়ে সুমনের কথাগুলো শুনছিলেন। কিন্তু এই পর্যন্ত শুনেই তিনি উচ্ছসিত হয়ে বলে উঠলেন, “আহা, তুমি ব্রিলিয়ান্ট সুমন, আর তোমার পিসির নাতিও ব্রিলিয়ান্ট! যদি কোনো কিছুর কর্মপদ্ধতি বাহ্যতভাবে জানার কোনো উপায় না থাকে, তবে তো সেটাকে ভেঙে ফেলে দেখা যেতেই পারে যে সেটা কীভাবে কাজ করছে… একেবারে ব্রিলিয়ান্ট!”
আমরা সবাই অবাক হয়ে একে অপরের দিকে তাকিয়ে কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু ঘনাদার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি বলেই চললেন, “তা এই যে হেড্রন কোলাইডার, যেখানে তোমার আগের মাস্টার মশাই কাজ করেন, সেটা তো আর কিছুই নয়, একটা ইলেকট্রনিক হাতুড়ি!”
“হাতুড়ি?” শিশিরের আর বিস্ময় ধরে না!
“হ্যাঁ, হাতুড়ি নয়তো আবার কী? হেড্রন বলতে বোঝায় ওই পারমাণবিক জগতের প্রাথমিক কণাগুলো। সেগুলোকে কোলাইডারের ভেতরে হাই ভোল্টেজ দিয়ে একে অপরের সঙ্গে খুব জোরে জোরে ধাক্কা লাগিয়ে তাদের ভেঙে ফেলা হয় বলে ওই রিসার্চ সেন্টারের নাম দেওয়া হয়েছে হেড্রন কোলাইডার।”
“তাই নাকি?” আমিও আমার বিস্ময় প্রকাশ করলাম।
ঘনাদা শুধু বললেন, ‘সবুজ’!
সুমন বলল, “কিন্তু আঠা, জেঠু, আঠা?”
ঘনাদা মুচকি হেসে বললেন, “ভোলোনি দেখছি!”
শিশির বলল, “সে ভবী ভুলবার নয় ঘনাদা!”
“তাই তো দেখছি” ঘনাদা ঘাড় নাড়লেন “বলছি। বলব যখন বলেছি, তখন বলব। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক শক্তির দালাল যেমন ‘ফোটন’ বা ‘আলোর কণা’, আর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দালাল যেমন ‘গ্র্যাভিটন’, তেমনি স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্সের দালালের নাম হল “গ্লুয়ন” তাকেই আমি নাম দিয়েছি আঠা! বিভিন্ন হেড্রনগুলোকে এঁটেসেঁটে পরমাণুগুলোর মধ্যে ভালো করে ধরে রাখবার কাজটা ওই আঠারই! ওই আঠা না থাকলে পদার্থগুলো তৈরি হত কী করে? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই বা তৈরি হত কী করে? সব বস্তু কালীঘাটের গামছার মতন ফ্যাড়ফেড়ে হয়ে যেত – মানে আসলে ‘বস্তু’ বলে কিছু হয়ে দাঁড়াতই না! কাজেই ধরা ছোঁওয়ার মধ্যে যে বিশ্বে আমরা বাস করি, সেসব কোনো কিছুই তৈরি হত না!”
“সুমন বলেও কিছু থাকত না – সে ভূত হয়ে চারিদিক ভেসে ভেসে বেড়াত…” শিশির হেসে একটু টিপ্পনী কাটে।”
“কাকু তোমরাও!” সুমনও ছেড়ে দেবার পাত্র নয়।
কিন্তু ঘনাদাই কি কম যাবার পাত্র নাকি? তিনি মন্তব্য করলেন, “বুঝতেই পারছ যে সেই আঠা কত গুরুত্বপূর্ণ! আঠা না থাকলে এই ‘ভৌতিক’, মানে ফিজিকাল ব্রহ্মাণ্ড তৈরিই হত না, আর আমরা সবাই ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াতাম।” সবাই হো হো করে হেসে উঠল।
“কিন্তু সিরিয়াসলি বলি জেঠু, লেপচুন না কি একটা বললে তখন, তা সেটাকে ভাঙলেই বা কী? সেখানে এই আঠাকে খুঁজে পাওয়া যাবে কী করে?” সুমন প্রশ্ন করে।
ঘনাদা কিছুক্ষণ সুমনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আবারও একটা লাখো টাকার প্রশ্ন করলে সুমন! কোয়ার্ক আর লেপটন্সগুলোকে তো শুধু ভাঙলেই হল না, ভেঙে যা খুঁজে পেতে চাই সেগুলো যে আসলে কী, তা বুঝব কী করে”
“হ্যাঁ, একটু বুঝিয়েই বলুন ঘনাদা,” গৌর ধীরভাবে বলল।
“বলছি,” ঘনাদা উত্তর দিলেন, “এখানেই তো মেদিনার কৃতিত্ব। তোমাদের বোস-আইনস্টাইন স্টাটিসটিকসের কথা তো একটু আগে বললাম—যাঁদের সম্মানে ‘বোসন’ গোত্রের কণাগুলির নামকরণ করা হয়েছে। পরমাণুর মধ্যে এই ধরনের কণার উপস্থিতি অধ্যাপক বোস আর আইনস্টাইনেরা যখন ঘোষণা করলেন তখন তো একেবারে হইচই শুরু হয়ে গেল। কারণ সেই কণা সঙ্গে সঙ্গে পদার্থের ‘তৎকালীন ব্যাখ্যাতীত’ অনেক কিছু বৈশিষ্ট্যকেই ব্যাখ্যা করে দিতে পারল। কিন্তু তবু প্রশ্ন রইল, প্রমাণ কই? এই ধরনের কণাগুলি এতই ঠুনকো বা ‘অস্থির’ যে তাদের সহজে খুঁজে পাওয়া খুবই মুশকিল। তাই বিশ্লেষণ করে দেখতে হয় যে কণার উপস্থিতি থাকলে, তার ভগ্নাংশ কী হতে পারে। সেই ভগ্নাংশ-কেও তো এমন হতে হবে যে তাকে ল্যাবরেটরিতে খুঁজে পাওয়া যাবে! তাই বিজ্ঞানীরা অনেক বছর ধরে হিসেব করে করে এমন সব ভগ্নাংশের কথা ঘোষণা করলেন যাদের উপস্থিতি ‘বোসন’-এর অস্তিত্ব প্রমাণ করে দেবে। তখন থেকে সেই ভগ্নাংশের সন্ধান শুরু হল সারা পৃথিবী জুড়ে। এর নাম দেওয়া হল ‘বোস-আইনস্টাইন কনডেনশেসন’ বা বি.ই.সি।”
“তা সেই বিইসি কি কোনোদিন খুঁজে পাওয়া গেল?” শিশিরের প্রশ্ন।
“আলবৎ গেল!” সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন ঘনাদা, “১৯৯৫ সালে আমেরিকার বোল্ডার, কলোরাডো শহরের একটা ল্যাবরেটরিতে এরিক কর্নেল ও আরও দুজন সহকারী মিলে বিইসি-র অস্তিত্ব প্রমাণ করে দিল, আর সেই সঙ্গে বোসনেরও। কিন্তু ততদিনে সত্যেন বোস মারা গিয়েছেন, আর মৃত ব্যক্তিদের তো আর নোবেল দেওয়া হয় না। তাই বাঙালিরা আরও একটি নোবেল থেকে বঞ্চিত হল। তবে ২০০১ সালে এরিক আর তার সহযোগীরা সেই কাজের জন্য নোবেল পেল।”
“জেঠু, তুমি তো এমন তুচ্ছ করে ‘এরিক আর তার সহযোগীরা পেল’ বললে যে তাতে মনে হচ্ছে যে তাঁরা যেন তোমার ‘ইয়ার’ ছিলেন” সুমন একটু অনুযোগ করল।
কিন্তু ঘনাদা মিষ্টি হেসে বললেন, “তা ছিল বৈকি! ১৯৮০-র দশকে আমাকে যখন বোল্ডারে নিয়ে যাওয়া হয় ওই ল্যাবরেটরিতেই – ভগ্নাংশটির কিছু কিছু গাণিতিক হিসেবের উপদেষ্টা হিসেবে, তখন আমি ওখানেই ছ-মাস থেকে যাই। সেই সময়ে আমি এরিকের সঙ্গে কাজ করছিলাম। সে ছিল ব্রিজ খেলবার পোকা। প্রতি সপ্তাহে ডুপ্লিকেট ব্রিজ খেলার ক্লাবে আমাকে নিয়ে যেত ওর পার্টনার হিসেবে। তখনই বেশ পরস্পরের বেশ ইয়ার হয়ে পড়েছিলাম আমরা”
“তাই নাকি?” এবারে একটু সমীহ করে বলল সুমন।
“হ্যাঁ, তাই। আর সেভাবেই তো হিগ্স সাহেবের সঙ্গে আলাপ হল আমার।”
“হিগ্স সাহেব আবার কে?” শিশির প্রশ্ন করল।
“ও, হিগ্স। উনি তো ব্রিটিশ সাহেব, বোল্ডারে ওই ল্যাবরেটরিতে এসেছিলেন একটা লেকচার দিতে। ওঁর নাম আমি আগেই শুনেছিলাম। তাঁর জন্মের কয়েক বছর পরেই, মানে ১৯৩২ সালে ‘নিউট্রন’-এর আবিষ্কার হল। নিউট্রন হল ‘প্রোটন’-এর মতোই আরেকটি কণা, কিন্তু তার একটু পায়াভারী, মানে তার ওজনটা একটু বেশি। পরে দেখা গেল যে কণাটিকে যদি নিউক্লিয়াস থেকে বার করে ফেলা যায় তবে মিনিট দশেকের মধ্যেই সেটা তার অতিরিক্ত ওজনটা হারিয়ে ফেলে। তখন সে একটা প্রোটন আর একটা ইলেকট্রনে পরিণত হয়। রহস্য হল, অতিরিক্ত ওজনটা যায় কোথায়, আর আসেই বা কোত্থেকে? তাই ১৯৬০-এর দশকে হিগ্স সাহেব তরুণ বিজ্ঞানী হিসেবে এই নতুন রহস্যটা নিয়ে কাজ করতে শুরু করলেন। সেই কাজ নিয়ে ১৯৬৪ আর ১৯৬৬ সালের মধ্যে তিনি কিছু বৈজ্ঞানিক পেপার লিখে ফেললেন। তাতে বললেন যে এই ওজনের তারতম্যটা আসছে একটা নতুন ধরনের শক্তির ফিল্ড থেকে, যা সারা দুনিয়া জুড়ে ব্যাপ্ত। তবে ইলেকট্রন-প্রোটনের মতো তাকে সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই নতুন শক্তির ফিল্ডের নাম দেওয়া হল ‘হিগ্স ফিল্ড’। কিন্তু সেই শক্তিকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেবার জন্য তো আবার দরকার শক্তির দালালকে, যেমন আগে তোমাদের বলেছি। তখন সেই শক্তির দালালকে বলা হল ‘হিগ্স বোসন’ বা ‘হিগস পার্টিকল’। তারপর থেকে হিগ্স পার্টিকল মেনে নিয়ে হিসেব করলে ফিজিক্সের ‘স্টান্ডার্ড মডেল’-এ আর কোনো গরমিল থাকে না। অতএব হিগ্স পার্টিকলের অস্তিত্ব যে সত্যি, তাতে কারুর সন্দেহ রইল না। কিন্তু, প্রমাণ কই? প্রমাণ না পেলে কি বিজ্ঞানে কিছু গৃহীত হয়?”
“উফ্, আবার সেই ‘প্রমাণ কর’, প্রমাণ কর’!” শিবুর বোধহয় ছোটোবেলার পরীক্ষাগুলোর সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে গেল।
শিশির তার সঙ্গে একটু চুটকি কেটে দিল, “প্রমাণ কর ‘ইহা’ ‘উহার’ চাইতে লম্বা – বাপ্রে সে কী বিভীষিকা! প্রমাণ না দিতে পারিলে সপ্তম শ্রেনিতে যাইবার ছাড়পত্র পাওয়া যাইবে না।”
ঘনাদা একটু হেসে বললেন, “বিজ্ঞানে প্রমাণই তো সব। ১৯৮০-র দশকে আমি যখন প্রথম ড. হিগ্সকে মিট করলাম, তখনও পর্যন্ত তাঁর হিগ্স পার্টিকলের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। সেই কারণে তিনি একটু বিষণ্ণ ছিলেন বলে আমার মনে হয়েছিল। ওঁকে অতিথি করে ব্রিজ খেলতে এনেছিল আমার পার্টনার, ভবিষ্যত-নোবেল জয়ী বৈজ্ঞানিক এরিক কর্নেল, যাঁর কথা তোমাদের একটু আগে বললাম। ব্রীজের টেবিলে আমাকে দেখেই হিগ্স বললেন, ‘ও ভারতীয় তুমি! তা সত্যেন বোস-এর নাম শুনেছ নাকি?’
কিন্তু আমি শুধু যে ওঁকে চিনতামই তা নয়, আমার সঙ্গে যে তাঁর একটা ব্যক্তিগত যোগাযোগও ছিল – আর আমি যে এইসব বিশ্লেষণের কাজের জন্য ওঁর কাছে মাঝেমাঝেই যেতাম, সেসব ওঁকে বলাতে তিনি একটু চুপসে গেলেন বলে মনে হল। সেই সুযোগে ওঁর বিরুদ্ধে পরপর তিনটে ‘গ্রান্ড স্ল্যাম’ করে ফেললাম। কিন্তু ব্রিজ-এ হেরে গেলেও, আমার সঙ্গে কিন্তু ওঁর বেশ দোস্তি হয়ে গেল তারপরে। স্কটল্যান্ড ফিরে যাবার আগে আমাকে বললেন, “ডাস্, তোমার অঙ্কের মাথাটা বড়ো পরিষ্কার। আমাদের কলেজে এসে পড়াতে শুরু করো না কেন? আমার অনেক গ্র্যান্টের টাকা আছে, ভালো মাইনে দেব…”
“তাই নাকি?” সুমন খুব সমীহ করে জিজ্ঞেস করে, “গেলে না শেষ পর্যন্ত?”
ঘনাদা উদাস হয়ে বললেন, “আরে দূর, সেসব কী আর আমার দ্বারা হয়? আমার এই মেসই ভালো, বুঝলে না! আমি বড়ো হয়েছি পুঁটি মাছ খেয়ে, আমার কী আর ওই দূর দেশে গিয়ে থাকা চলে? মাঝে মাঝে যাই যখন অল্প কিছুদিনের জন্য কেউ ডাকে। এর বেশি আর পোষায় না আমার! ওই ৫০০ কেজি করে করে, বড়ো বড়ো মোষের মতো গোরু, তাদের মাংস বেশিদিন ধরে ঠিক খেতে পারি না। রামভুজের হাতের পুঁটি মাছের ঝোল তার চেয়ে ঢের ভালো, বুঝলে তো!”
গৌর তাড়াতাড়ি বলল, “বেশি জোরে বলবেন না ঘনাদা, রামভুজের কানে ঢুকলে তো তার মাইনে বাড়িয়ে দিতে হবে শেষে!”
শিশির হো হো করে হেসে ফেলল, “ঠিক বলেছিস একদম।”
ঘনাদা কিন্তু বলেই চললেন, “এই হিগ্সের কল্যাণেই কিন্তু আমার মেদিনার সঙ্গে আলাপ হল শেষ পর্যন্ত।”
“তাই নাকি?” সবাই একটু অবাক হয়ে ঘনাদার দিকে তাকাল “হিগ্স সাহেবই আপনার সঙ্গে মেদিনার আলাপ করিয়ে দিলেন?”
“হ্যাঁ, তাই তো।” ঘনাদা বললেন “১৯৯০ দশকের শেষের দিকে হিগ্সের বয়স প্রায় সত্তর। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বিখ্যাত কাজ, ‘হিগ্স পার্টিকল’-এর ৩৬ বছর বয়স হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তখনও পর্যন্ত কিছুতেই তার অস্তিত্বের প্রমাণ দাখিল করা যায়নি। তাই তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে তাঁর জীবনকালে আর সেই প্রমাণ পাওয়া যাবে না, আর তিনি কোনোদিন নোবেলও পাবেন না। হয়তো সেই বিষণ্ণতার জন্যেই আমাকে চিঠিপত্রও আর বেশি লিখতেন না। কিন্তু ইউ.কে.-র উত্তরাঞ্চলে ডারহ্যাম বলে যে একটা বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি আছে, তারা সেসময়ে হিগ্সকে ডেকে কয়েকটা সেমিনার দেবার কনট্র্যাক্ট দিল। তখন হিগ্স আমাকে সেখানে আসতে ডাকলেন, ওঁর সহকারী হিসেবে। সামান্যই – মাত্র হপ্তা দুয়েকের কাজ, কিন্তু বেশ মোটা মাইনে। তাই আর কী করি, রাজি হয়ে গেলাম।”
“গেলে সেখানে?” সুমন একটু অবাক হয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল “আমি কী তখনও আসিনি?”
শিবু তাড়াতাড়ি বলল, “না না, তুই আসবার আগে ছিল এটা।”
“ও, আচ্ছা,” সুমন মেনে নিল।
ঘনাদা বললেন, “হ্যাঁ তুমি আসবার আগেই হবে। যাই হোক, সেখানে তখন একটি চিনে ছাত্রী ছিল, যার নাম মেদিনা অ্যাবলাইকিম। সেখানে তখন ফিজিক্সে পিএইচডি করছিল সে। হিগ্সের সেই সেমিনারে ও যোগ দেয়। কিন্তু কিছু কিছু সূত্রের ব্যাপারে তার একটু অসুবিধে হচ্ছিল – চিনেরা খুব মেধাবী হলেও, ইংরিজি ভাষা নিয়ে তাদের একটু অসুবিধে হয়। তাই হিগ্স আমাকে বললেন, ‘ডাস্, তুমি যদি মেয়েটাকে একটু সাহায্য করতে পারো তাহলে খুব ভালো হয়। এইসব ভগ্ন কণা সনাক্ত করবার অঙ্কগুলো এমনিতেই অনেকের কাছে একটু শক্ত মনে হয়। তার ওপরে আবার ভাষার সমস্যা। একটু তালিম দিতে পারবে ওকে?”
“তাহলে তালিম দিলে তাকে?” সুমন জিজ্ঞেস করল।
“দিলাম বইকি!” ঘনাদা উত্তর দিলেন “প্রায় ছয় সপ্তাহ কাটালাম ওকে প্রাইভেট টিউশনি দিতে দিতে। তারপরে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। পিএইচডি শেষ করে যখন সে বেজিং ইউনিভার্সিটিতে হাই এনার্জি ফিজিক্সের গবেষণায় যোগ দিতে গেল তখন আমাকেও বলল ওর সঙ্গে যেতে। বলল, ‘আমরা তো বছর দশেক আগেই ওখানে একটা কোলাইডার বানিয়েছি – জেনিভার মতন। ভবিষ্যতে আরও অনেক বড়ো করা হবে সেটাকে। ওখানে তুমি বেশ দায়িত্বশীল কাজ পাবে নিঃসন্দেহে। আসবে আমার সঙ্গে?”
“এবারেও গেলেন না অত বড়ো সুযোগ পেয়েও?” সুমন আবার প্রশ্ন করে।
কিন্তু ঘনাদার আগে গৌরই উত্তর দিয়ে দেয়, “আরে শুনলি না একটু আগে? অত বড়ো বড়ো গোরুর মাংস খাবেন না বলে তো ইউরোপেই গেলেন না ঘনাদা, আর তুই ভাবছিস বেজিং যাবেন? জানিস না, চিনেরা সাপ-ব্যাং কীসব যেন খায়!”
সুমন বলল, “মেদিনা তাহলে নোবেল পাচ্ছে কী আবিষ্কার করে?”
ঘনাদা বললেন, “বলছি। তার আগে একটা সুখবর দিই। শেষ পর্যন্ত জেনিভায় সার্ন হেড্রন কোলাইডারে, ২০১২ সালের জুলাই মাসে একটা বিশাল বড়ো এক্সপেরিমেন্ট করে ‘হিগ্স বোসন’-এর অস্তিত্ব প্রমাণ করা গেল। সৌভাগ্যবশত, হিগস তখনও বেঁচে ছিলেন। তাই সার্ন-এর অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে তাঁকেও ফিজিক্সে নোবেল দেওয়া হল ২০১৩ সালে।”
“বাঃ, কী ভালো কথা!” সুমন বলে ওঠে, “কিন্তু মেদিনা কী কাজ করেছে?”
“আঠা, আঠা…” ঘনাদা প্রত্যুত্তর দিলেন “সে একটা বিশাল বড়ো আন্তর্জাতিক টিম নিয়ে, এই বছরেই, মানে ২০২৪ সালেই, একটা পেপার লিখে ঘোষণা করেছে যে বেজিং কোলাইডারের সাহায্যে তারা গ্লু বল্ এর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পেরেছে। এটা নিয়ে অবশ্য আরও কিছু কাজ বাকি এখনও, কারণ কিছুদিনের পরে বোঝা যাবে যে ওরা সত্যিই গ্ল, বল্ খুঁজে পেয়েছে, নাকি অন্য কিছু। কিন্তু যদি ঠিক প্রমাণ হয়, তবে তো বলব মেয়েটা অসাধ্য সাধন করে ফেলেছে শেষ পর্যন্ত। এমন একটা কাজের পুরস্কার? নোবেল অবধারিত।”
“তা সে নোবেল পেলে আপনাকে খাওয়াবে তো?” শিবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করে।
“আলবৎ খাওয়াবে। কেন খাওয়াবে না” ঘনাদা গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন। কথাটা বললেন কিন্তু আরাম কেদারাটা থেকে উঠে নিজের শয়ন কক্ষের দিকে চলে যেতে যেতে। বোধহয় বিশ্রামের সময় হয়ে এসেছিল তাঁর।
বহুদিন পরে বেশ মন ভরে একটা বড়ো কাহিনি শুনতে পেয়ে সবাই বেশ খুশি। কিন্তু শিশির হঠাৎ ডুকরে উঠল, “আরে, পুরো সিগারেটের টিনটা নিয়ে চলে গেলেন? টিনটা খোলাও হয়নি এখনও…”
Tags: অমিতাভ রক্ষিত, নবম বর্ষ প্রথম সংখ্যা