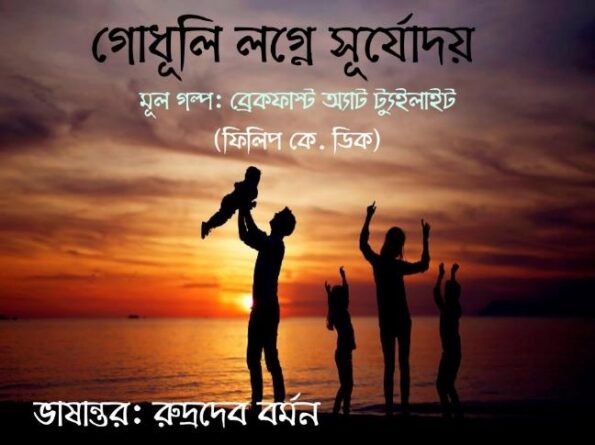গোধূলি লগ্নে সূর্যোদয়
লেখক: রুদ্র দেব বর্মন
শিল্পী: সৌরভ ঘোষ
অরিন তাড়াতাড়ি করে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসে। তখনও গামছা দিয়ে মাথা মুছে চলেছে। টপ টপ করে জলের ফোঁটা মাথা থেকে ঘাড় বেয়ে পিঠে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু তর সয় না অরিনের। বাবাকে ডাইনিং টেবিলে চা খেতে দেখেই বলে ওঠে, “বাবা, আজ আমাদের স্কুলে পৌঁছে দেবে?”
তীর্থঙ্কর তখন সবেমাত্র পট থেকে কাপে দ্বিতীয় বারের জন্য চা ঢালছে। ঘুম থেকে উঠে সকালে পরপর অন্তত দু’কাপ চা না হলে ওর চলে না। আজ একদিকে একটু সকাল সকাল অফিসে পৌঁছোনর দরকার আর অন্যদিকে গাড়িটাও ঝামেলা করছে বলেই এত তাড়াতাড়ি ও প্রস্তুতি নিচ্ছে। নইলে অন্য দিনগুলোতে ও সাধারণত বাচ্চারা স্কুলে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই বিছানা ছাড়ে। অনেক দিন পর আজ অন্যরকমভাবে সকালটা শুরু করেছে। চা-টা ঢালতে ঢালতেই একবার মুখ তুলে ও ছেলের দিকে তাকায়। অরিন তখনও মাথা মুছে চলেছে। তাকিয়ে আছে বাবার দিকে। ওকে নিরাশ করতে খারাপ লাগলেও তীর্থঙ্করের আজ উপায় নেই। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলে, “উঁহু, আজ নয় অরিন। আজ তুমি দিদিদের সঙ্গে হেঁটেই চলে যাও। অন্যরকম মজা হবে, কেমন? গাড়িটা তো গ্যারাজে দেওয়া হয়েছে না!”
মেজ মেয়ে জিনি মুখ বাঁকায়। “কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে যে!”
“কই না তো!,” বিদিশা বোনকে থামিয়ে দৌড়ে গিয়ে জানলার পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি মেরে বলে, “ও মা! বৃষ্টি কোথায়? এ তো কুয়াশায় পুরো ভরে আছে চারদিক। তবে বৃষ্টি কিন্তু নেই।”
“দাঁড়া একটু। আমি দেখছি,” মহিমা সিঙ্কে বাসন ধুচ্ছিল। এবার তোয়ালেটা টেনে নিয়ে হাত মুছতে মুছতে এগিয়ে গিয়ে জানলার বাইরে নজর দেয়। “কি জঘন্য একটা দিন রে বাবা! এটা কি ধরনের কুয়াশা? এ তো মনে হচ্ছে ঘন ধোঁয়ায় ঢাকা চারদিক। একটা কিছুও দেখা যাচ্ছে না কোনও দিকেই। জিনি মা, টিভিটা একটু চালাও তো। দ্যাখো তো ওয়েদার রিপোর্ট কী বলছে?”
অরিন জামাটা কোমরে গুঁজতে গুঁজতে বলে, “টিভি তো চলছে না মা। আমি সকালে চালিয়ে ছিলাম। স্ক্রিন পুরোটা নীল হয়ে খড়খড় করছে খালি!”
তীর্থঙ্কর তড়াক করে উঠে দাঁড়ায়। মাথা গরম হয়ে ওঠে ওর। বলে, “এই টিভিটা আবার খারাপ হয়ে গেল? এই তো সেদিন ঠিক করালাম!” এগিয়ে গিয়ে টিভিটার সমস্যা বোঝার চেষ্টা করে তীর্থঙ্কর। টিভির সুইচ অন ক’রে রিমোটটা টেপাটেপি করে খানিক। ফায়ার স্টিকটা দেখে নেয় কয়েক বার। সেট-টপের পেছনের কানেকশনটা খোলে আর লাগায় বারদুয়েক। তবুও টিভিতে কোনও ছবি ভেসে ওঠে না। গাঢ় নীল স্ক্রিনে কয়েকটা সাদা লম্বা দাগ মাঝে মধ্যে ভেসে ওঠে। এ ছাড়া আর কিছু হয় না। ঘড়ঘড়ে একটা স্ট্যাটিক আওয়াজ ছাড়া। বাচ্চারা ওদিকে স্কুলের জন্য তৈরি হতে হতে কয়েকবার উঁকি মেরে যায়। বাবাকে ব্যস্ত দেখে ফিরে যায় আবার। তীর্থঙ্কর কিছু বুঝে উঠতে পারে না টিভিটা কেন হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। কালই তো রাতে ওরা ফোর্টিন্থ ইন্ডিয়ান আইডল-এর সেমিফাইনাল দেখে ঘুমোতে গেছিল। ও বলে ওঠে, “আশ্চর্য!”
অরিন টাইটা ঠিক করতে করতে এক হাতে ব্যাগটা পিঠে ওঠায় আর লীভিং রুমের দরজা খুলে বলে, “মা, আমি এলাম।”
কিচেন থেকে মহিমা বলে ওঠে, “দাঁড়াও। দিদিদের সঙ্গে একসঙ্গে বেরোবে।”
বিদিশা পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে মায়ের সামনে গিয়ে বলে, “আমি তৈরি। আমাকে ঠিক লাগছে তো মা?”
চিবুকে হাত দিয়ে মেয়েকে কাছে টেনে মহিমা কপালে একটা চুমু দিয়ে বলে, “তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে সোনা মা।”
তীর্থঙ্কর ওদিকে এবার হাল ছেড়ে দিয়ে রিমোটটা সোফায় ছুড়ে ফেলে বেরিয়ে আসতে আসতে বলে, “ঠিক আছে, আমি অফিসে গিয়ে ওখান থেকেই সার্ভিসিং এজেন্সিকে ফোন করে…”, আর এরপরেই তীর্থঙ্কর হঠাৎই থেমে যায়। ওর চোখ ততক্ষণে বাইরের লিভিংরুমের দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে থাকা অরিনের ওপর। অরিন দাঁড়িয়ে আছে ওখানে, ওর মুখচোখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, চোখ বড় বড় করে ভয়ার্ত ভাবে তাকিয়ে আছে।
“কী হয়েছে?”
“আমি— আমি যাবো না।”
“কী হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ লাগছে?”
“আমি স্কুলে যেতে পারব না।”
সবাই অরিনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তীর্থঙ্কর অরিনের কাছে এগিয়ে গিয়ে ওর হাতটা ধরে জিজ্ঞেস করে, “কী হয়েছে? কেন তুমি স্কুলে যেতে পারবে না?”
“ওরা— ওরা আমাকে যেতে দেবে না।”
“কারা?”
“ওই সৈন্যগুলো।”
অরিনের মুখ থেকে এবার আগ্নেয়গিরির লাভার মতো শব্দের স্রোত উছলে বেরিয়ে আসে। “ওরা চারদিক থেকে আসছে। একদম ঘিরে নিয়েছে চারদিক থেকে। সৈন্য আর অস্ত্র গিজগিজ করছে সব জায়গাতেই। আর… আর ওরা সব আসছে এদিকে।”
তীর্থঙ্কর ভারী অবাক হয়। ওর মুখ থেকে প্রতিধ্বনির মতো বেরিয়ে আসে, “সৈন্য! আসছে? এদিকে আসছে?”
“হ্যাঁ। ওরা সব এদিকেই আসছে আর ওরা আমাদের—” থেমে যায় অরিন, মুখে ভয়ের ছাপ আরও ঘন হয়ে ফুটে ওঠে। ততক্ষণে সামনের বাগানের মোরাম বিছানো পথে ভারী বুটের শব্দ জেগে ওঠে। আর তারপরেই একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ, যেন কাঠের কিছু একটা ভাঙল। সঙ্গে কর্কশ গলার কিছু আওয়াজও যেন ভেসে আসে বাইরে থেকে।
“হে ভগবান,” মহিমা চাপা গলায় আর্তনাদ করে ওঠে। “তীর্থ, এ সব কী হচ্ছে?”
তীর্থঙ্কর অরিনকে ভেতরে ঠেলে দিয়ে বাইরের ঘরের দিকে এগোয়। ভারী বুটের পদক্ষেপের শব্দ আর তারপরেই আবার কাঠ ভাঙার আওয়াজে ওর ভেতরটা ধকধক করে ওঠে। বুকে যেন একটা ব্যথা অনুভব করে তীর্থঙ্কর। কিন্তু তারপর বাইরের ঘরে পৌঁছে যখন দেখল সামনের ভাঙা দরজার ভেতরে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে, তখন সব ব্যথা-বেদনা এক লহমায় মুছে গিয়ে বুকের ভেতরে যেন একটা শূন্যতা জেগে উঠল। জলপাই-সবুজ রং-এর পুরোদস্তুর উর্দীপরা তিনজন সৈন্য ওদের ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর ওদের ঠিক পেছনে দরজার ভাঙা পাল্লাটা একদিকে লটকে ঝুলে রয়েছে।
(২)
তিনজন সৈন্য! দরজা ভেঙে ঘরের ভেতর ঢুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই মুহূর্তে। এই সকালবেলা। তীর্থঙ্কর হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। জলপাই-সবুজ রং-এর পুরোদস্তুর উর্দীপরা প্রত্যেকটা সৈন্য সম্পূর্ণ সশস্ত্র। বন্দুক আর বিভিন্ন জটিল অস্ত্রশস্ত্র দু-হাতে ধরা আর শরীরের বিভিন্ন অংশে আরও কিছু সংযুক্ত যা তীর্থঙ্কর আগে কোনওদিন দেখা তো দূরের কথা এমনকি কোথাও পড়েওনি বা শোনেওনি। অচেনা অজানা অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও প্রত্যেকের শরীর জড়িয়ে বিভিন্ন নল আর পাইপ। বেশ কিছু মিটারের ডায়াল এখানে ওখানে ঝুলছে। মাথায় হেলমেট আর তার সঙ্গে জুড়ে থাকা গ্যাস-মাস্ক যেটা এখন ঝুলছে কাঁধের পেছনে। পড়নের উর্দীতে বিভিন্ন জায়গায় কিছু চৌকো চৌকো চকচকে বর্গাকার বাক্স মতো কিছু, যেগুলো থেকে আবার কিছু পরিবাহী তার গিয়ে যুক্ত হয়ে রয়েছে হেলমেটের ওপরে বেরিয়ে থাকা অ্যান্টেনার মতো কিছু একটার সঙ্গে। হেলমেটের সামনের স্বচ্ছ আবরণী পেরিয়ে তীর্থঙ্করের দৃষ্টি এ সমস্ত জটিল যন্ত্রপাতি ছাড়িয়ে সব শেষে গিয়ে পড়ে ওদের মুখের ওপর। তীর্থঙ্কর দেখতে পায় ওদের ক্লান্ত রুক্ষ কুঁচকে যাওয়া মুখে নিদ্রাহীন লালচে চোখের তীক্ষ্ণ অথচ নৃশংস এবং উদাসীন দৃষ্টি যেন তাঁকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিচ্ছে।
তিনজনের মধ্যে একজন সেই মুহূর্তে ঝাঁকি মেরে হাতের বেখাপ্পা পাতলা সরু বন্দুকটা সোজা তুলে ধরে তীর্থঙ্করের বুক বরাবর। ও বোধহীনভাবে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে উদ্যত বন্দুকটার দিকে। এটা কী ধরনের বন্দুক? লম্বাটে আর সরু। প্রায় ছুঁচের মতোই সরু, বড়জোর বস্তা সেলাই করার ছুঁচের থেকে একটু মোটা বলা যেতে পারে এটাকে। পেছনের যেদিকে বন্দুকের কুঁদোটা থাকে সেখানে একই রকম পাতলা সরু নলের প্যাচানো একটা কুণ্ডলী।
“মানে… আপনারা… কি… ,” বলে সবে তীর্থঙ্কর শুরু করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই সামনের বন্দুক বা ওই জাতীয় বস্তুটা উঁচোনো সৈনিকটি তাঁকে থামিয়ে দিয়ে কঠোর কর্কশ গলায় বলে ওঠে, “কে তুই? এখানে কি করছিস তুই?”
বলতে বলতে মুখের সামনের স্বচ্ছ মুখাবরণীটা এবার সরায় সৈন্যটা। ওর গোটা মুখটা এবার পরিষ্কার দেখা যায়। নোংরা হয়ে আছে মুখটা। বেশ কিছুদিন স্নান না করে বাইরের আবহাওয়ায় ঘুরে বেড়ালে যেমন হয় আর কি। চামড়ায় বেশ কিছু কাটা দাগ-ও রয়েছে। কয়েকটা যেন প্রায় তাজা। যেন ভালো করে দেখলে এখনও শুকনো রক্তের চিহ্ন পাওয়া যাবে। এর বেশ কয়েকটা দাঁত দেখা যাচ্ছে ভাঙা আর নিশ্চিহ্ন।
পাশ থেকে দ্বিতীয় সৈনিকটি তীর্থঙ্করকে তখনও চুপ করে থাকতে দেখে দাবড়ে ওঠে, “কী হল? বল্ কী করছিস তুই এখানে?”
তীর্থঙ্কর এই সক্কালবেলা নিজের বাড়ির লিভিং রুমে দাঁড়িয়ে অনাহুত এই তিনজন সৈনিকের প্রশ্নে হতবাক হয়ে যায়। উত্তর খুঁজে পায় না। তৃতীয় সৈনিকটি এবার এক পা এগিয়ে আসে তীর্থঙ্করের সামনে। বন্দুকটা বাঁ হাতে ঝুলিয়ে রেখে ডান হাতটা বাড়ায় তীর্থঙ্করের দিকে। “দেখি তোর আধার কার্ড বা নীল কার্ড। তোর ঠিকানা যাচাই করতে হবে…”. বলতে বলতে ওর চোখে পড়ে ভেতরের ডাইনিং-এর দরজায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকা মহিমা আর বাচ্চাগুলোর দিকে। ও-র মুখটা হা হয়ে ঝুলে পড়ে।
“একজন মহিলা!”
সৈনিক তিনজনেই হতবাক হয়ে যায় এই অবিশ্বাস্য ঘটনার সম্ভবতায়।
প্রথম সৈনিকটি এবার তীর্থঙ্করকে আবার জিজ্ঞেস করে, “এ সব কী হচ্ছে? এই মহিলা এখানে কতক্ষণ ধরে রয়েছে?”
তীর্থঙ্কর এতক্ষণে একটু দম ফিরে পায়। বলে, “উনি আমার স্ত্রী। এ সব কি হচ্ছে মানে? আপনারা কোথা থেকে—”
“আপনার স্ত্রী?”, এতক্ষণে সৈনিকদের প্রশ্নের সম্বোধন সূচক শব্দের পরিবর্তন হয়। পেছনে ‘স্ত্রী’ দাঁড়িয়ে থাকায় তীর্থঙ্কর এবার ‘তুই’ থেকে সোজা ‘আপনি’-তে পদোন্নতি পায়।
“হ্যাঁ। ইনি আমার স্ত্রী আর ওরা তিনজন আমাদের সন্তান। এবার দয়া করে আপনারা—”
“আপনার নিজের স্ত্রী! আপনার সন্তান! আর আপনি এদেরকে এখানে নিয়ে এসেছেন? আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে!”
আরেকজন বলে ওঠে, “এই লোকটার নিশ্চয়ই ভষ্মরোগ হয়েছে। নইলে…,” বলতে বলতে হাতের বন্দুকটা নামিয়ে ধরে তীর্থঙ্করকে পাশ কাটিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে লিভিং রুম পার করে ডাইনিং-এর সামনে মহিমার কাছে গিয়ে পৌঁছোয়।
“আপনি তৈরি হয়ে নিন দিদি। আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।”
শেষ বাক্যটা যেন বজ্রপাতের মতো নেমে এল তীর্থঙ্করের উপর। এতক্ষণ ও যেন কোনও ম্যাজিক শো দেখছিল। হঠাৎ করে দরজা ভেঙে উদয় হওয়া তিনজন অস্ত্রশস্ত্রধারী সৈনিক তাকে খানিকটা হতবাক করেও দিয়েছিল। ও যেন এতক্ষণ কোনও অ্যানাস্থেশিয়ার ঘোরে চলে গিয়েছিল। যে মুহূর্তে তৃতীয় সৈন্যটা মহিমার দিকে হাত বাড়িয়ে ওদের সঙ্গে যাওয়ার আদেশ দিল, তীর্থঙ্করের সামনে থাকা অদৃশ্য ঘোরের পর্দাটা যেন ছিঁড়ে গিয়ে ওকে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে আনল।
ও যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকেই লাফিয়ে পড়ল।
কিন্তু ওর ক্ষমতা ততটা ছিল না। ওকে লাফিয়ে পড়তে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তিনজন সৈনিকই একসঙ্গে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটা ভয়ংকর শক্তির ঝড় যেন তীর্থঙ্করকে ধাক্কা মারল। মহিমা আর বাচ্চা তিনটের চোখের সামনে যেন এক সেকেন্ডের জন্য একটা ঘূর্নীঝড় বয়ে গেল। তারপর তীর্থঙ্কর হাত-পা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিটকে পড়ল। অন্ধকারের একটা মেঘ যেন তার চারদিকে ঘুরে চলেছে। তার কান ভনভন করতে লাগল। মাথা ভার। কাজ করছে না। চারদিক ধোঁয়া ধোঁয়া। তারপর আস্তে আস্তে সব কিছু কমতে লাগল। একটু পরে, তীর্থঙ্কর ওর আশপাশের চলমান অবয়বগুলো সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। কিছু আবছা আওয়াজ কানে আসতে থাকে। তার নিজের বাড়ি। পরিচিত লিভিং রুম। তীর্থঙ্কর নিজেকে ধীরে ধীরে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করে চলল। কিন্তু এক মুহূর্ত পরেই আবার ওর চোখের সামনে অন্ধকারের পর্দা নেমে এল।
(৩)
এদিকে একজন সৈনিক ততক্ষণে বাচ্চা তিনটেকে একদিকে জড়ো করেছে। ওরা এক জায়গায় নিজেদেরকে আঁকড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মহিমার একটা হাত ধরে আরেকজন সৈন্য টানছে। টানের চোটে মহিমার পোষাকের একটা অংশ কাঁধের ওখান থেকে ছিঁড়ে ঝুলছে। সৈন্যটা খ্যাক খ্যাক করে এক সঙ্গীর উদ্দেশে বলে ওঠে, “হেই, অবস্থা বোঝো! লোকটা এই মহিলাকে কেন যে এখানে এনেছে দেখে কিছু কি বুঝতে পারছ?”
“বাইরে নিয়ে যাও। এখানে ছেড়ে যাওয়া যাবে না।”
“জি, ক্যাপ্টেন।” মহিমাকে টেনে সৈন্যটা বাইরের দরজার দিকে নিয়ে যেতে যেতে আবার বলে, “আমরা এঁর জন্য যতদূর যা যা করার নিশ্চই করার চেষ্টা করব।”
“হেই, ওই বাচ্চাগুলোকে নিয়ে যাও তুমি”, ক্যাপ্টেন তৃতীয় সৈন্যটার উদ্দেশে আদেশ জারি করে। “ওদেরকেও সঙ্গে নিয়ে নাও। আমি এদিকটা একটু সরেজমিনে দেখে নিই।”
মাস্কটা খুলে হাতে নিয়ে হালকা পায়ে বাড়িটার এদিকে ওদিকে নজর দেয় ক্যাপ্টেন। ওর মাথায় ঢোকে না এখানে এই পুরুষটি একজন মহিলা আর তিনটে বাচ্চা নিয়ে কী করছে! একটা মাস্ক নেই কারও! পরিচয়পত্র দেখাতে পারছে না! না আছে আধার কার্ড না নীল কার্ড! সবথেকে বড় কথা এই বাড়িটা গোটা এখনও এভাবে কী করে দাঁড়িয়ে আছে? একটুও আঘাতগ্রস্ত না হয়ে কি করে বেঁচে রইল এই বাড়িটা! কাল রাতে যে হারে এদিকের এলাকায় ‘রম’ পড়েছে তাতে বাকিগুলোর মতো এটারও তো গুঁড়িয়ে যাওয়া উচিত ছিল। অথচ এটা তো দেখা যাচ্ছে যেমনকার তেমনিই গোটা দাঁড়িয়ে রয়েছে! যেন গতরাতে ‘রম’-বর্ষণ শেষ হওয়ার পর এই বাড়িটাকে অন্য কোথাও থেকে তুলে এনে এখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে!
ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেনের নজরে আসে তীর্থঙ্কর কোনওভাবে কাতরাতে কাতরাতে উঠে দাঁড়িয়েছে। যদিও তখনও নিজের পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। মুখটা রক্তাক্ত। নাক আর দাঁতের কষের পাশ থেকে এখনও রক্ত ঝড়ছে। চোখেও আবছা দেখছে সব কিছু। কোনওভাবে দেওয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছে। শ্বাসের গতি অনিয়মিত। ওই অবস্থাতেই ক্যাপ্টেনের উদ্দেশে গোঙায় তীর্থঙ্কর, “দেখুন, আমরা… এখানেই… ভগবানের… দিব্যি…”
ক্যাপ্টেন তীর্থঙ্করকে খেয়ালও করে না। করা সম্ভবও ছিল না তার। ক্যাপ্টেনের নজর ততক্ষণে গিয়ে পড়েছে রান্নাঘরের দিকে। তাকিয়ে আছে সরাসরি ডাইনিং টেবিলের দিকে। “ওগুলো কী? খাবার? আরে! এগুলো কি খাবার নাকি? ক্যাপ্টেন এবার এক-পা দু-পা করে এগিয়ে যায় ডাইনিং টেবিলটা দিকে। বলে, “ওয়াও! হেই, এদিকে এস। দেখো এদিকে সব।”
সৈন্য দুজনেই মহিমা আর বাচ্চা তিনটেকে দরজার সামনে ছেড়ে দিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো দৌড়ে আসে। ক্যাপ্টেনকে ডাইনিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হুড়মুড় করে সোজা ওখানে পৌঁছে হাঁ করে টেবিলের দিকে তাকিয়ে থাকে। তিনজনেই বিস্মিত এবং হতবাক।
একজন শেষে বলে ওঠে, “কি আশ্চর্য!”
আরেকজন বলে, “এদিকে দেখো। এই দ্যাখো চা!” বলেই হাত বাড়িয়ে তুলে নেয় চায়ের পট-টা। সোজা পট থেকেই ঢালতে শুরু করে গলায় লোভীর মতো। এবং আটকায় গলায়। একটা কাশির দমক বেরিয়ে আসে। চায়ের ধারা গড়িয়ে নামে চিবুক থেকে সোজা উর্দীতে। উফ্ উফ্ করে বলে ওঠে, “বাপরে! ভয়ানক গরম!”
ইতিমধ্যে অন্যজন খুলে ফেলেছে ফ্রিজের দরজার পাল্লা। “এই দ্যাখো, এখানে দুধ, ক্রীম, ডিম, মাখন, মাংস…পুরো ভরতি খাবার রে বাবা!”
ক্যাপ্টেন ডাইনিং থেকে এগিয়ে স্টোর রুমে অদৃশ্য হয়। মুহূর্ত পরেই আবার দৃশ্যমান হয় ডাইনিং-এ। ওর হাতে এখন জমানো মটরশুটির একটা প্যাকেট। প্যাকেটটা ওদের দুজনকে দেখিয়ে বল, “যা যা খাবার-দাবার দেখছ সব তুলে নাও। সব। সমস্ত তুলে নাও আমাদের অহিবাহনে।”
মটরশুটির প্যাকেটটা থপ্ করে ডাইনিং টেবিলটা উপর ফেলে দেয় ক্যাপ্টেন। তারপর ঘুরে তাকায় তীর্থঙ্করের দিকে। হাত দিয়ে চাপড়ে চাপড়ে নোংরা হয়ে যাওয়া পোষাকের এ পকেটে ও পকেটে খোঁজে সিগারেটের প্যাকেটটা। খুঁজে পেয়ে একটা বের করে ধরায় ধীরে সুস্থে। সারাক্ষণ চোখ রাখে তীর্থঙ্করের উপর। স্থির নজরে যেন মাপছে, এমন ভাবে তাকিয়ে থেকেই লম্বা লম্বা তিন চারটা দীর্ঘ টান দিয়ে সিগারেটের প্রায় অর্ধেকটা ছাই করে দিয়ে তারপর তীর্থঙ্করকে বলে, “ঠিক আছে, এবার আপনার কি বলার আছে সেটা বলুন, আমি শুনছি।”
তীর্থঙ্কর মুখ খোলে, ঠোঁট দুটো খুলে গিয়ে আবার বন্ধ হয়ে যায়। কোনও আওয়াজ বেরোয় না। মাথা পুরো খালি। ভোঁতা একটা বোধহীন অনুভূতি ছাড়া তীর্থঙ্কর আর কিছু টের পায় না। কিছু ভাবতেও পারছে না তীর্থঙ্কর।
ক্যাপ্টেন নজর করল ব্যাপারটা। কথা ঘোরানোর জন্য ডাইনিং টেবিলটা দেখিয়ে বলল, “এই যে এই সমস্ত খাবারদাবার, এগুলো কোথায় পেয়েছেন?”
তীর্থঙ্কর এখনও চুপ। শুধু একবার বোধহয় মনে হল ঠোঁট দুটো যেন নড়ল। কিন্তু কোনও আওয়াজ বেরোল না।
ক্যাপ্টেন আবার প্রশ্ন ছুড়ে দিল। এবার হাতটাকে একবার সমস্ত বাড়িটার দিকে তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরিয়ে বলল, “এই সমস্ত বাসনপত্র, আসবাব, এত কিছু এখানে কীভাবে জোগাড় করলেন? এই বাড়িটাই বা কীভাবে গোটা রয়ে গেল? কাল রাত্রিরের আক্রমণের থেকেই বা আপনারা কীভাবে নিজেদের বাঁচালেন?”
“আ-আমি…,” তীর্থঙ্করের মুখ থেকে এতক্ষণে একটু আওয়াজ বেরোল। হাঁফাচ্ছে তীর্থঙ্কর। আবার চুপ। শুধু বড় বড় শ্বাস ফেলার আওয়াজ। তবে ওর নিষ্পলক চোখের দৃষ্টি কিন্তু ক্যাপ্টেনের উপর থেকে সরল না।
ক্যাপ্টেন পুরো একটা মিনিট নির্বাক তাকিয়ে রইল তীর্থঙ্করের দিকে। তারপরেও তীর্থঙ্করকে নিস্তব্ধ দেখে লম্বা পদক্ষেপ ফেলে এগিয়ে এল ওর দিকে। চোখে মুখে একটা ক্রুঢ় দৃষ্টি। “একজন মহিলা। তিনটে বাচ্চা। মোটমাট পাঁচজন। যেন একটা পরিবার। আপনারা সবাই মিলে এখানে কী করছেন?” তাঁর কণ্ঠস্বরের কাঠিন্য তীর্থঙ্করকে স্পর্শ করল কি না বোঝা গেল না। একটু থেমে ক্যাপ্টেন আবার শুরু করে, “মশাই, আপনি কিন্তু পুরো ব্যাপারটা ভালো করে ব্যাখ্যা করলে ভালো করবেন। আপনি এখানে কী করছেন তা, আমার মনে হয়, আপনি আরও ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন— নয়তো আমাদের হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং সেটা আপনার পছন্দ না ও হতে পারে।”
(৪)
তীর্থঙ্করকে ডাইনিং টেবিলের একটা চেয়ারে বসানো হয়েছে। ও কোনও বাধা দেয়নি। নিজেকে পুরো ছেড়ে দিয়েছিল ক্যাপ্টেন আর তার দলের হাতে। ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও। অন্য কিছু করার কোনও ক্ষমতাও ওর ছিল না।
এখন চেয়ারে বসে শরীরের ভার কনুইয়ের সাহায্যে টেবিলে ছেড়ে দিয়ে ক্রমাগত বড় বড় শ্বাস নিয়ে নিজেকে স্থিতিশীল করার চেষ্টা করে চলেছে। একই সঙ্গে নিজের চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতাও ফিরে পেতে চাইছে। যদিও এই মুহূর্তে ওর মাথা এখনও পুরোপুরি ফাঁকা। সমস্ত শরীরে ও ব্যথা টের পাচ্ছে। জিভ দিয়ে ঠোঁটের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়া রক্ত অনুভব করে তীর্থঙ্কর। বাঁ হাতের পেছনটা দিয়ে রগড়ে সেটা মুছে নিলো। টের পায় ওর মাড়ির একটা দাঁত-ও ভেঙে গিয়েছে। আরও দু-তিনটে দাঁত-ও যেন নড়ছে মনে হচ্ছে। পকেট থেকে রুমালটা বার করে থু থু করে ভেঙে যাওয়া দাঁতের টুকরোটা ও ফেলে। ও টের পায় এখনও ওর হাত কাঁপছে।
এবার ওর কানে আসে ক্যাপ্টেনের গলা, “ঠিক আছে। একটু নিজেকে স্থির করুন। সব ঠিক হয়ে যাবে।”
মাথা তুলে রুমালটা পকেটে রাখতে রাখতে দেখে মহিমা আর বাচ্চারা ইতিমধ্যে ঘরের ভিতরে ফিরে এসেছে। জিনির কান্নার শব্দ কানে আসে। তাকিয়ে দেখে বিদিশা ফ্যাকাশে ভয়ার্ত মুখে দাঁড়িয়ে। আর অরিন ভয় পাওয়া বড় বড় চোখে সৈন্যগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে।
“তীর্থ”, মহিমা ওর কাঁধে আলতো করে নিজের হাতটা রাখে। “তুমি ঠিক আছো তো?”
তীর্থঙ্কর মাথা নাড়ায়। বলে, “হু। ঠিক আছি”, ও চায় না ওর গোটা পরিবার এই মুহূর্তে আর বেশি টেনশন করুক। মহিমাও সেটা বুঝতে পারে। ও হাত বাড়িয়ে তীর্থঙ্করকে হালকা করে কাছে টেনে নিজের মাথা স্বামীর কাধে রেখে সান্ত্বনা দেয়, “তুমি বেশি ভেব না। এরা এরকম করে পালাতে পারবে না। এক্ষুনি কেউ না কেউ আসবে। সব্জিওয়ালা বা পিয়ন কিংবা সামনের বাড়ির গুরুং দিদি… এরা পালাবে কোথায়…”
“চুপ করুন”, ক্যাপ্টেন দাবড়ে ওঠে, “সব্জিওয়ালা! পিয়ন! প্রতিবেশী! কী বলছেন কী আপনারা? কোথায় পাচ্ছেন এসব! হ্যাঁ?” তারপর হাত বাড়ায় মহিমার দিকে। বলে, “দেখি দিদি আপনাদের ইউসিএস কার্ডটা দেখান দিকি।”
“ইউসিএস কার্ড?” মহিমার মুখ হা হয়ে যায়।
“ইউসিএস— মানে ইউনিভার্সাল সিটিজেনশীপ কার্ড। আছে? নেই তো! না আধার কার্ড না নীল কার্ড না ইউসিএস কার্ড। কিছুই নেই! এমনকি কোনও গ্যাস মাস্কও নেই আপনাদের কাছে!” ক্যাপ্টেন নিজের চিবুকে জেগে ওঠা খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলো চুলকোয়। যেন নিজের মনেই ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করতে চাইছে।
একজন সৈন্য এগিয়ে এসে ক্যাপ্টেনের কানের কাছে নীচু স্বরে বলে, “ক্যাপ্টেন, আমার মনে হচ্ছে এরা পাকিস্তানি।”
অন্যমনস্ক ক্যাপ্টেন বলে, “হতেই পারে। আবার না ও হতে পারে।”
সৈন্যটি কিন্তু স্থির নিশ্চিন্ত। আবার বলে, “ক্যাপ্টেন, এরা নিশ্চয়ই পাকিস্তানি বা বাংলাদেশি। বরং এদের সব ক-টাকেই উড়িয়ে দেওয়া হোক। আমরা কোনও ফাঁক ছাড়তে পারি না। তাই না, ক্যাপ্টেন?”
“এখানে একটা কিছু গোলমেলে ব্যাপার আছে। অবশ্যই আছে,” বলতে বলতে ক্যাপ্টেন উর্দীর গলার কাছ দিয়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে বার করে আনে একটা চৌকো মতোন ছোট্ট তার লাগানো বাক্স। সেটার তারের একটা প্রান্ত চেপে ঢুকিয়ে দেয় হেলমেটের অ্যান্টেনার একটা জায়গায়। বলে “আমি বরং র-কে খবর দিয়ে দিই।”
‘র’-শব্দটা যেন শিহরণ জাগিয়ে তোলে বাকি সৈনিক দুজনের মধ্যেই। ‘র’ মানেই ‘রাপু’, আর ‘রাপু’ মানেই বাহাত্তর ঘা। একশো বছর আগে বাঘে ছুলে আঠারো ঘা-এর কথা শোনা যেত। পঞ্চাশ বছর আগে পুলিশের ছোঁয়ায় ছত্রিশ ঘা-এর কথা শোনা যেতো। সেগুলো সবই সাধারণ মানুষের কথা। এখন ‘র’-এর ‘রাপু’- মানে রাজনৈতিক পুলিশের কথায় সৈনিকদের পর্যন্ত শরীর শিউরে ওঠে। একজন সৈন্য ক্যাপ্টেনকে বোঝাতে চেষ্টা করে, “ক্যাপ্টেন, একটু শুনুন। এই ব্যাপারটা বরং আমরাই সাল্টে নিই। ফালতু এই ছোট ব্যাপারে ‘র’-কে খবর দেওয়ার কোনও মানে হয় না। কে জানে ‘রাপু’-গুলো হয়তো আমাদেরকেই ৪-নম্বর লাগিয়ে দেবে আর আমরা ফেঁসে যাবো। তার চেয়ে…”
ক্যাপ্টেন কর্নপাত করে না। চৌকো বাক্সটাতে ততক্ষণে বলতে শুরু করে দিয়েছে, “হ্যালো, আমি শিক-৬ নম্বর বাহিনীর ক্যাপ্টেন। শিলিগুড়ি করিডর। সুকনা থেকে বলছি। আমাকে ওয়েব-বি তে যোগাযোগ করান।”
তীর্থঙ্কর মহিমার দিকে তাকিয়ে কোনওরকম বলে, “মহিমা, শোনো, আমি…”, কিন্তু শেষ করতে পারে না। তার আগেই একজন সৈন্য প্রায় লাফিয়ে আসে, “চোপ! কোনও কথা নয়।”
তীর্থঙ্কর চুপ করে যায়। মহিমা তীব্র চোখে সৈন্যটার দিকে তাকিয়ে থাকে।
ক্যাপ্টেনের হাতের চৌকো বাক্সটা আওয়াজ করে ওঠে, “ওয়েব বি সেন্ট্রাল কলিং।”
ক্যাপ্টেন বলে, “ওয়েব বি সেন্ট্রাল, এটা শিক-৬ ক্যাপ্টেন, শিলিগুড়ি করিডর, সুকনা থেকে বলছি। আপনারা কি একটা ফরওয়ার্ড রাপু দল এখানে পাঠাতে পারবেন? আসলে এখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে দেখতে পাচ্ছি। পাঁচজনের একটা দলকে এখানে একটা বাড়িতে পাওয়া গেছে। বাড়িটা সম্পূর্ণ গোটা। কোথাও কোনও ভাঙার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। একজন লোক আর একজন মহিলা, সঙ্গে তিনটে বাচ্চা। এদের সঙ্গে কোনও গ্যাস-মাস্ক নেই, কোনও ইউসিএস বা আধার কার্ড, এমনকি কোনও নীল কার্ড-ও নেই। মহিলার শরীরে কোনও অত্যাচারের চিহ্ন-ও নেই। একত্রে বসবাস করছে যদিও! আবার সব রকমের আসবাব রেখেছে বাড়িতে। আরেকটা আশ্চর্য ব্যাপার হল বাড়িতে প্রচুর খাবার জমা করা রয়েছে। অন্তত শ’খানেক কেজি খাবার-দাবার তো হবেই। ওভার।”
অপরপ্রান্ত খানিক চুপচাপ। সম্ভবত ওদিকে কিছু আলোচনা চলছে। রাপু মানে রাজনৈতিক পুলিশের দলকে এই মুহূর্তে সুকনায় পাঠানোর সম্ভাবনার বিচার বিবেচনা করছে বোধহয়। ক্যাপ্টেন ধৈর্য ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আবার চৌকো বাক্স থেকে আওয়াজ আসে, “ওয়েব বি সেন্ট্রাল কলিং। শিক-৬ দলকে আদেশ করা হচ্ছে সুকনাতে থাকতে। একটা রাপুর দল সুকনায় রওনা হয়ে গেছে। লক্ষ রাখুন পাঁচজনের দলটা যেন পালাতে না পারে। ওভার।”
“শিক-৬ ক্যাপ্টেন বলছি। আদেশ গৃহীত হল। আমরা এখানেই থাকছি। পালাবার কোনও সুযোগ দেওয়া হবে না। ওভার এন্ড আউট।”
যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ক্যাপ্টেন চৌকো বাক্সটা আবার উর্দীর নির্দিষ্ট জায়গায় ঢুকিয়ে রাখে। তারপর নিজের দলটার দিকে তাকিয়ে বলে, “রাপুরা আসছে। এখানেই থাকো। দ্যাখো যেন কেউ পালাতে না পারে। আর হ্যাঁ, রাপুরা পৌঁছোনর আগেই খাবারদাবার যা যা ওঠানোর সব অহীবাহনে তুলে নাও। রাপুরা এলেই আমরা বেরিয়ে যাবো।”
কথা শেষ হতে না হতেই বাইরে থেকে একটা ভয়ংকর গভীর বিস্ফোরণের গর্জন ভেসে এল। সেই আওয়াজে গোটা ঘরটাই ঝনঝন করে কেঁপে উঠল যেন। জানলাগুলোর কাচের পাল্লা আর আলমারিতে থাকা বাসন-কোসনগুলো সব একসঙ্গে ঝনঝন করে উঠল।
“বাপরে!” একজন সৈনিক বলল। “এটা তো মনে হচ্ছে খুব কাছাকাছি কোথাও পড়েছে। আমাদের স্ক্রিন-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল না কি!”
“না না। আমি তো আশা রাখি যে আমাদের স্ক্রিন-ব্যবস্থা আজ রাত অবধি অন্তত ঠিক থাকবে। আর তার আগেই আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে,” বলে ক্যাপ্টেন জমানো মটরশুটির যে প্যাকেটটা ডাইনিং টেবিলে ফেলে দিয়ে ছিলেন সেটা এক হাতে তুলে নিলেন। তারপর তীর্থঙ্কর আর মহিমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “এদিকের অবস্থা নিশ্চই বুঝতে পারছেন। এখন একটু বিশ্রাম নিন। রাপুর দল আসছে।”
জমানো মটরশুটির প্যাকেটটা হাতে নিয়েই ডাইনিং রুমের বাইরে যেতে যেতে দরজার কাছ থেকে ঘুরে সৈনিক দুজনকে আদেশ করলেন, “লেগে পড়ো। আমি চাই যেন রাপুরা আসার আগেই খাবারগুলো অহীবাহনে বোঝাই করে নেওয়া যায়।”
সৈনিক দুজন এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হওয়ায় বোধহয় একটু নিরাশ হয়ে পড়েছিল। এবার মনের মতো পছন্দের আদেশ ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে পাওয়া মাত্র দ্রুত গতিতে জড়ো করা সমস্ত খাবারগুলো একটার উপর আরেকটা সাজিয়ে নিয়ে দু-হাতে তুলে ক্যাপ্টেনের পেছন পেছন বেরিয়ে পড়তে বেশি সময় নিল না। একটু পরেই তীর্থঙ্করদের চোখের সামনে দিয়ে সৈনিক দুজন সামনের ভাঙা দরজার পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। তীর্থঙ্কর আর মহিমা ওদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে ভয়ার্ত এবং নির্বাকভাবে সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে রইল। সৈনিকদের নিজেদের মধ্যে বলা কথাবার্তার আওয়াজ আস্তে আস্তে সামনের মোরাম বেছানো পথে ভারী বুটের মস্ মস্ শব্দের সঙ্গে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।
(৫)
তীর্থঙ্কর ডাইনিং টেবিলে মাথাটা কাত করে হাত দুটো দু-পাশে ছড়িয়ে রেখে বসেছিল। সৈনিকদের বুটের আওয়াজ সামনের বাগানের মোরাম বিছানো পথে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাওয়ার পরও মিনিট খানেক অপেক্ষা করলো। তারপর টেবিলের ভর রেখে উঠে দাঁড়িয়ে একটু দম নিয়ে দেখে নিল হাঁটতে পারবে কিনা। নিশ্চিন্ত হয়ে নিয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ব্যথার কাতরানি আটকে রেখে বলল, “তোমরা এখানেই থাকো। আমি দেখে আসছি।”
মহিমা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে তীর্থঙ্করকে ধরে। ভয়ার্ত স্বরে জিজ্ঞেস করে, “কী করতে চাইছ তুমি?”
“দেখি। বাইরে যেতে পারি কিনা!” বলে তীর্থঙ্কর প্রায় ছুটে খিড়কি দরজার কাছে পৌঁছোয়। প্রায় কথাটা এই অর্থে যে তীর্থঙ্কর ওটাকে ছুটে যাওয়া বলে ভাবলেও তা প্রকৃত অর্থে পা টেনে টেনে ছুটে যাওয়ার একটা চেষ্টা বই অন্য কিছু নয়। খিড়কি দরজাটা বন্ধই আছে আর গতকালের মতো একইরকম আছে। দরজার ল্যাচটা খোলার সময় ও বুঝতে পারে ওর হাত কাঁপছে। শ্রান্তি না ভয়? পাল্লাটা টেনে দরজাটা হাট করে খোলে তীর্থঙ্কর। বাইরে বেরিয়ে পেছনের উঠোনে নামে। টের পায় পেছনে মহিমা ততক্ষণে এসে খিড়কি দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। তীর্থঙ্কর চারদিকে তাকিয়ে অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করে। “ওদের কাউকে এদিক থেকে দেখা যাচ্ছে না। যদি আমরা এদিক দিয়ে বেরিয়ে যাই…”
তারপরেই তীর্থঙ্কর চুপ করে যায়। একটা ঢোক গেলে।
এই মুহূর্তে, এই পেছন উঠোন পেরিয়ে চারদিকে আর কিছুই তো নেই! না। একটু ভুল হচ্ছে ওর। আছে। তবে কাল রাত্রিতে ঘুমোতে যাওয়ার আগেও শেষ সিগারেটটা খাওয়ার সময় এখানে পায়চারী করতে করতে যা যা দেখে ছিল বা না দেখলেও জানতো যেগুলো ছিল, সেগুলো এখন কিছুই নেই। ওর চারদিকে এখন যতদূর নজর যায় শুধুই ধূসর কালচে ধোঁয়ার মেঘ যেন আকাশ থেকে নেমে এসে মাটির সঙ্গে ছোটাছুটি করে খেলে বেড়াচ্ছে। তার মধ্যে দিয়ে কিছু আবছা আকার আকৃতি নজরে আসে। ভাঙাচোরা কিছু আকার চুপচাপ এই ধূসর পটভূমিকায় স্থির হয়ে রয়েছে।
ধ্বংসাবশেষ!
সমস্ত বাড়ি ঘরের ধ্বংসাবশেষ। একটার পর একটা ধ্বংসস্তূপ। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে ভেঙে পড়া সমস্ত কিছু। সর্বত্র ধ্বংসাবশেষ। পিছনের উঠোনের পাশের দিক দিয়ে ধীর ধীরেকয়েক পা হাঁটল তীর্থঙ্কর। কংক্রিটের বানানো পথটা, যেটা ওর বাড়ির উঠোনটাকে গোল করে চারদিকে ঘিরে বানিয়ে ছিল রাতের ডিনারের পর একটু হাঁটাহাঁটি করার জন্য, যে পথটাতে কাল রাতেও সিগারেটের সুখটান দিতে দিতে হেঁটেছিলো তীর্থঙ্কর, সেটা হঠাৎই একটু এগিয়ে শেষ হয়েছে গিয়েছে। আর তার ওপারে, উঠোনের বাইরে, তাদের এই বাড়িটা বাদ দিয়ে আর কিছু নেই। এর বাইরে, শুধুই ভেঙে পড়ে থাকা কংক্রিটের চাঙড় আর ধসে পড়া টুকরো-টাকরা জিনিসপত্রের স্তূপ। আর কিছু না। যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত আর কিছু নেই। কিছুই নাই।
গোটা একটা শহর ‘নেই’ হয়ে গেছে। বাড়ি ঘর স্কুল অফিস সব ধ্বংস হয়ে গেছে। কিছুই নেই। একটাও মানুষ নেই। প্রাণহীন। জেগে আছে শুধু কিছু ভেঙে পড়া দেয়াল, একের পর এক। মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়ে দিয়ে। তীর্থঙ্করের চোখে পড়ে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কয়েকটা আগাছা বেড়ে উঠেছে। তীর্থঙ্কর নীচু হয়ে, একটি আগাছা হাত দিয়ে স্পর্শ করে। রুক্ষ, মোটা ডাঁটা এবং তারপরেই তার হাত ছোঁয় স্ল্যাগের মতো কঠিন কর্কশ কিছু। কঠিন হয়ে যাওয়া গলিত ধাতু। চমকে হাত সরিয়ে নেয় তীর্থঙ্কর। সে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়তে চায়। কিন্তু তার আগেই—
“ভিতরে ফিরে আসুন,” একটা ফ্যাসফ্যাসে গলার আওয়াজ তীর্থঙ্করকে চমকে দিল।
সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পেছন ঘুরেই তীর্থঙ্কর স্তম্ভিত হয়ে গেল। একজন লোক তাদের বারান্দায় খিড়কি দরজার কাছে কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। একজন ছোটখাটো মানুষ, চাপা চোয়াল, গাল দুটো বসা। চোখ দুটি কালো কয়লার টুকরোর মতো খুদে খুদে কিন্তু ঝকঝক করছে। এর উর্দীর রং আর রকমসকম সৈন্যদের থেকে আলাদা। মাথার উপরের শিরস্ত্রান আর মুখের উপর লাগানো গ্যাস-মাস্কটাও অন্যরকম। আর এর সেগুলো খুলে পাশে আর পেছনে আলগোছে ঝুলছে। এতদূর থেকেও তীর্থঙ্কর বুঝতে পারে এই লোকটার গায়ের রং হলদেটে আর কেমন যেন অদ্ভুতভাবে চকচক করছে, আর সেই সঙ্গে গালের হাড়গুলোও কেমন যেন উঠে আছে। দেখে মনে হচ্ছে একটি অসুস্থ মানুষের মুখ, সম্ভবত জ্বর হয়েছে অথবা অবসন্নতায় বিধ্বস্ত। অথচ দাঁড়ানোর বা কথাবার্তার ভঙ্গিতে যথেষ্ট চনমনে আর করিৎকর্মা বলে মনে হচ্ছে।
তীর্থঙ্কর নড়ে না। ওখান থেকেই প্রশ্ন ছুড়ে দেয়, “আপনি কে?”
লোকটা মুখের সামনে থেকে মাছি তাড়ানো মতো হাত দিয়ে একটা ভঙ্গি করে। বলে, “দোরজি। রাপু কমিশনার পেমা দোরজি।”
“আপনি— আপনি রাজনৈতিক পুলিশ? কমিশনার দোরজি!” তীর্থঙ্কর বলে ওঠে। একটু আগে সৈনিকদের কথাবার্তায় রাপুদের সম্বন্ধে যেটুকু শুনেছে তাতে ওর ভেতরে একটা ঠান্ডা হিমেল স্রোত বয়ে যায়।
“হ্যাঁ। একদম ঠিক। এবার আপনি ভেতরে আসুন। মহিলা এবং বাচ্চাদের আমি ভেতরে বসিয়েছি। আপনি এলে আমি আপনাদের কাছে কিছু ব্যাখ্যা চাইব। আমার বেশ কিছু জিনিস বোঝার আছে।”
(৬)
কমিশনার দোরজি ড্রয়িং রুমটা বেছে নিলেন বসবার জন্য। এটা ডাইনিংটার থেকে বড় আর আলো-বাতাস বেশি। যা বোঝা গেলো কমিশনার দোরজি সময়ের খুবই হিসেবী। সবাই বসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম প্রশ্ন ছুড়লেন।
“আমি সবার আগে জানতে চাই যে এই বাড়িটি কীভাবে ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেল?”
তীর্থঙ্কর, মহিমা আর বাচ্চারা তিনজন একসঙ্গে বসেছিল একটা লম্বা সোফায়।
কমিশনার দোরজির প্রথম প্রশ্নের পরেও ওরা প্রত্যেকেই চুপচাপ বোকার মতো বসে রইল। তাদের বাড়িটা কেনই বা ধ্বংস হবে আর না হলে কেন সেটা হল না তাই নিয়ে এই সেনা-পুলিশের এত মাথা ব্যাথাই বা কেন হবে, সেটা বুঝে ওঠা ওদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না।
মিনিটখানেক তীর্থঙ্করদের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন কমিশনার। তার দৃষ্টি একের পর একজনের উপর ঘুরতে থাকল। বারতিনেক সবাইকে দেখে নিয়ে তারপর আবার বললেন, এবার গলার স্বর যেন আরেকটু নরম আর তাতে অনুরোধের সুর মেশানো, “কী হল? আপনাদের উত্তরটা দিন।”
তীর্থঙ্কর এবার এতক্ষণে তার কণ্ঠস্বর খুঁজে পায়। কমিশনার লোকটার ব্যবহারে কিংবা গলাযর স্বরে আগের ক্যাপ্টেনের মতো সেই হিংস্রতা না থাকায় বা সারাদিনের ঘটনার ঘনঘটায় পরিশ্রান্ত এবার ও মুখ খোলে। “দেখুন কমিশনার,” ও বলে, “আমি জানি না। আমি বা আমরা এই ব্যাপারে সত্যিই কিছু জানি না”, একবার ঘাড় ঘুরিয়ে মহিমার দিকে তাকিয়ে নেয়। মহিমা মাথা নেড়ে চোখের ইশারায় সায় দেয়। তীর্থঙ্কর আবার শুরু করে, “আজ সকালে আমরা রোজকার মতোই ঘুম থেকে উঠেছি। যেমন প্রত্যেকদিন আমরা সকালে জলখাবার খাই তেমনি খেয়েছি। রোজকার মতোই স্কুলের জন্য, অফিসের জন্য—”
“তবে আজ সকালে ভয়ানক কুয়াশা ছিল,” বিদিশা বলে ওঠে, “আমরা দেখেছি। বাইরে ছিল ভয়ানক কুয়াশা। কুয়াশার জন্য কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।”
অরিন অনেকক্ষণ থেকে সুযোগ খুঁজছিল কিছু একটা ওর বক্তব্য রাখার। এবার দিদিকে বলতে দেখে আর সময় নষ্ট করল না। “আর টিভিটাও চলছিল না। আমি আবহাওয়ায় খবরের জন্য চালালাম। শুধু ঘড়ঘড় করছিল। বাবা, তুমি তো চালাবার অনেক চেষ্টা করলে তাই না?”
“টিভি? আপনাদের টিভি চলছে? এখনও?”
মহিমা উত্তর দেয়। “না, আজ চলেনি। তবে গতকাল রাতেও আমরা ইন্ডিয়ান আইডল-এর সেমিফাইনাল দেখে শুতে গিয়েছিলাম।”
”ইন্ডিয়ান আইডল?” কমিশনার দোরজি তাঁর পাতলা ঠোঁট দুটো বেঁকিয়ে যেন একটু হাসলেন। তারপর বললেন, “পাঁচ বছর আগেই সরকারিভাবে সমস্ত রিয়ালিটি শো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া এখানে এই গোটা এলাকায় গত বেশ কিছু মাস ধরেই কোনও নেটওয়ার্ক নেই। মালদহের এদিক থেকে ওদিকে সিকিম পর্যন্ত গোটা এলাকায় নেটওয়ার্ক জ্যাম করা আছে। শুধু কিছু স্পেশাল সরকারি কম্পাঙ্কে মিলিটারি যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু আছে।”
উর্দীর বুকপকেট থেকে একটা ট্যাব বের করে স্টাইলাস দিয়ে কিছু করলেন কমিশনার। তারপর চারদিকে একবার পুরো তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘাড় ঘুরিয়ে কিছু দেখলেন। নিজের মনেই মাথা নাড়লেন বারদুয়েক। তারপর তীর্থঙ্করের দিকে তাকিয়ে যেন নিজেকেই বলছেন এমন ভাবে শুরু করলেন, “এই বাড়িটা। এই আপনারা সবাই। আমি বুঝতে পারছি না… এক আপনারা যদি ইসাই বা পিলিআ হোন তো—”
“ইসাই বা পিলিআ? এগুলো আবার কী?” মহিমা বিড়বিড় করে বলে।
কমিশনার দোরজি অপলক চোখে তীর্থঙ্করদের প্রত্যেকের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছিলেন। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মহিমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “ইসাই হচ্ছে পাকিস্তানের আইএসআই আর পিলিআ হচ্ছে চীনের পিপল লিবারেশন আর্মি। দু-হাজার আঠাশের ভারত পাকিস্তানের বালুচ যুদ্ধের পর পাকিস্তান আর চীনের মধ্যে যে বেইজিং চুক্তি দু-হাজার তিরিশে হয় তারপর থেকে এই ইসাই আর পিলিআ একসঙ্গে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে গোপন কার্যক্রম শুরু করে।”
“এ সব তো সবাই জানে। এই সবার জানা কথাগুলো বলে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন?” তীর্থঙ্কর কমিশনার দোরজির ইতিহাস ভূগোল নিয়ে বক্তব্য শুনে ধৈর্য রাখতে পারে না, “এগুলো তো আমাদের বাচ্চারা জানে। শুধু আপনি যে ইসাই-এর কথা বলছেন আমরা সেটা আইএসআই বলি আর ওই পিলিআ না কি? ওটা গোটাগুটি পিপলস্ লিবারেশন আর্মি বলেই জানি।”
“জানেন? আপনারা জানেন?“ কমিশনার দোরজির গলায় একটা ব্যঙ্গের আভাস আর সেটা উনি রীতিমতো ওঁর শারীরিক ভঙ্গিতেও প্রকাশ করতে লজ্জিত নন তা বোঝা গেল।
“হ্যাঁ। জানি। দেখুন কমিশনার, মাত্র দু-বছর আগের কথা মনে না থাকার কোনও কারণ তো নেই। বিশেষ করে এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে হলে।“
“এক মিনিট। এক মিনিট,” হাত বাড়িয়ে তীর্থঙ্করকে থামায় কমিশনার দোরজি। “কী বললেন? দু-বছর আগে? তাই বললেন তো?”
তীর্থঙ্কর অবাক হয়। “হ্যাঁ। কেন?”
কমিশনার দোরজি উত্তর দিতে গিয়ে চুপ করে যান। পুরো এক মিনিট তীর্থঙ্করদের প্রত্যেককে দেখতে থাকেন। কপালে চিন্তার ভাঁজ। মহিমা তীর্থঙ্করের দিকে অবাক চোখে তাকায়। অরিন, জিনিয়া আর বিদিশাও অবাক। এ ওর দিকে তাকিয়ে যেন বোঝার চেষ্টা করে। কমিশনার দোরজি গোটা পরিবারের প্রতিক্রিয়া চুপচাপ লক্ষ করেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পুরো ড্রইং রুমটার চারদিকে ধীরে সুস্থ পায়চারি শুরু করেন। নজর একের পর এক ঘরটার সমস্ত আসবাবপত্র, সাজসজ্জা, দেওয়ালে টাঙানো ফোটো, শো পিস— সব কিছুর উপর ঘুরে বেড়ায়। তারপর এসে তীর্থঙ্করের সামনে দাঁড়ান। একটু নীচু হয়ে জিজ্ঞেস করেন, “আচ্ছা এখানে আপনারা কতদিন ধরে আছেন?”
“দেখুন আমি জানি না আপনি কেন এ ধরনের প্রশ্ন করছেন। তবে আমরা এই সুকনাতে আসি দু-হাজার কুড়িতে। ওই যে বছর করোনা ভাইরাসের জন্য প্রায় গোটা বছরটাই লকডাউনের মধ্যে পার হয়ে ছিল। আর আমাদের ছোট ছেলে অরিনের জন্ম এখানেই সদর হাসপাতালে দু-হাজার বাইশে। এখন ওর বয়স দশ।“
“ও”, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কমিশনার অরিনের দিকে তাকান। অরিন বড়দি বিদিশার আরেকটু কাছে ঘেঁষে বসে।
আবার সামনের ছোট সোফাটায় গিয়ে বসেন কমিশনার দোরজি। পকেট থেকে নোটবুকটা বার করে কিছু লেখেন। তারপর স্টাইলাসটা দিয়ে নিজের কপালে যেন কয়েকটা দাগ কাটেন খসখস করে। তাকে চিন্তিত মনে হয় এবার। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে যেন হঠাৎই কোনও সিদ্ধান্ত নিলেন। তারপর তীর্থঙ্করদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “দেখুন যদিও আপনাদের দেখে আমার তেমন ভয়ংকর কিছু মনে হচ্ছে না। কিন্তু আপনাদের এখানে এই জায়গায় উপস্থিতিটা আজকের এই সময়ে বেশ মারাত্মক রকমের বিস্ময়কর এবং সন্দেহজনক। কেন জানেন?”
“না। আমরা সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না,” তীর্থঙ্কর স্বীকার করে। মহিমা মাথা নেড়ে সায় দেয়।
কমিশনার দোরজি একবার হাতের নোটবুকটা দেখে নিয়ে আবার শুরু করেন, “এই মুহূর্তে আমরা এখন যেখানে বসে আছি, শিলিগুড়ির এই অঞ্চলটাকে ভূ-রাজনৈতিকভাবে মুরগির গলা বা চিকেন নেক বলে। এই জায়গাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভারতের গোটা উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ভৌগলিক ক্ষেত্রে দখল বজায় রাখার জন্য। আর এমনিতেই এটা এখন হচ্ছে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি। চীন আর পাকিস্তান দু-পক্ষই চাইছে যেভাবে হোক এই জায়গাটা দখল করতে। কাজেই এই এলাকায় অচেনা মানুষ মাত্রই শত্রুপক্ষের গুপ্তচর হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। আপনারা যে তা নন তা আপনাদেরকেই প্রমাণ করতে হবে।”
“তার মানে যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে?”
“শুরু হয়েছে? দু-বছর আগে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। দু-হাজার সাঁইত্রিশে।”
তীর্থঙ্কর হতভম্ব হয়ে যায়। বিড়বিড় করে বলে, “দু-বছর আগে! ২০৩৭ সালে। মানে এটা হচ্ছে ২০৩৯!”
তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ওয়ালেটটা বার করে আনে। এগিয়ে দেয় কমিশনার দোরজির দিকে। বলে, “এগুলো দেখুন।”
কমিশনার হাত বাড়িয়ে ওয়ালেটটা নেন। খুলে ওটার ভেতরে সাবধানতার সঙ্গে নজর দেন। “কেন?”
“দেখে নিন। গ্যাসের রিসিপ্ট, এটিম রিসিপ্ট, মুদিখানার রসিদ। তারিখগুলো দেখে নিন,” তীর্থঙ্কর এবার মহিমার দিকে তাকায়। ওর চোখে মুখে এতক্ষণ পরে উজ্জ্বলতা ফিরে এসেছে। ও মহিমাকে বলে, “এবার আমি বুঝতে পারছি। বাইরের ধ্বংসস্তূপগুলো দেখে আমার খানিকটা আন্দাজ হচ্ছিল। এবার ঠিক ধরতে পেরেছি।”
অরিন এতক্ষণ দিদিদের কাছ ঘেঁষে বসেছিল। যুদ্ধের কথায় এখন ও খানিকটা উত্তেজনায় চেগে উঠেছে। একটু ফাঁক পেয়েই কমিশনারকে জিজ্ঞেস করে, “আমরা কি জিতছি?”
কমিশনার দোরজি অরিনের প্রশ্নের উত্তর দেন না। বরং নিজের নোটপ্যাড আর তীর্থঙ্করের দেওয়া রসিদগুলোর দিকে তাকিয়ে কিছু যেন মিলিয়ে নেন। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়ান। মনোযোগ দিয়ে দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারগুলো দেখেন। তারপর বলেন, “বেশ আশ্চর্যজনক ব্যাপার। প্রত্যেকটাই পুরোনো। খুবই পুরোনো। কোনওটা সাত বছরের আর কোনওটা আট বছরের পুরোনো,” আবার ফিরে এসে সোফায় বসেন। তীর্থঙ্করের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, “আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন? যে আপনি এসেছেন অতীত থেকে? আমাকে মানতে হবে যে আপনারা সময়ভ্রমণকারী?”
তীর্থঙ্কর কিছু বলার আগেই সৈনিক দলের সেই ক্যাপ্টেন এসে ঢোকে ড্রইংরুমে। “স্যার, আমরা প্রস্তুত। অহীবাহনে মালপত্র তোলা হয়ে গিয়েছে,” বলে কমিশনারের আদেশের অপেক্ষা করে।
কমিশনার মাথা নাড়েন। তারপর একটু কী যেন চিন্তা করে নিয়ে ক্যাপ্টেনকে বলেন, “ঠিক আছে। আপনি আপনার টহলদারি বাহিনী নিয়ে এগিয়ে যান। আমি পরে আসছি।”
ক্যাপ্টেন ইতস্তত করে। তীর্থঙ্করদের দিকে তাকায়। কমিশনারকে একা রেখে এগিয়ে যেতে অনিচ্ছুক মনে হয় তাকে। বলে, “আপনি কি একা…”
কমিশনার দোরজি থামিয়ে দেন। “ঠিক আছে। আমি এই ব্যাপারটা দেখছি। আপনারা এগোন এবার।”
ক্যাপ্টেন মিলিটারি কায়দায় স্যালুট জানান কমিশনারকে। “ইয়েস, স্যার”, তারপর ঘুরে বেরিয়ে যান ঘরটা থেকে। বাইরে বেরিয়ে দ্রুতগতিতে ক্যাপ্টেন আর তার দল তাদের অহীবাহনে, যেটা একটা লম্বাটে গড়নের ট্রাক হলেও দেখলে মনে হচ্ছে যেন সেটা একটা চাকার ওপরে বসানো লম্বা একটা নল, সেটায় সদলবলে চেপে বসেন। পরমুহূর্তে একটা হালকা গুনগুন আওয়াজ করে অহীবাহন চলতে শুরু করল।
একটু পরেই দৃশ্যপটে শুধু কালচে ধূসর মেঘ আর আবছা হয়ে আসা ধ্বসে পড়া বাড়িঘরের প্রান্তরেখাটুকু ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।
এদিকে ঘরের মধ্যে তীর্থঙ্করদের গোটা পরিবার দেখতে পায় কমিশনার দোরজি তাদের সারা বাড়িতে দ্রুতগতিতে একবার এদিকে একবার ওদিকে করে পায়চারি করছেন। কখনও দেওয়ালে সাজানো জিনিস দেখছেন, কখনও আসবাবপত্র পরীক্ষা করছেন। এক একবার টেবিলে বা শোকেসে সাজানো বইপত্র বা পত্রিকা তুলে নিয়ে দ্রুত পাতা উলটোচ্ছেন। এবার হাতে গোটা কয়েক পত্রিকা নিয়ে এসে তীর্থঙ্কররের সামনে সোফাটায় বাঁ পায়ের উপর ডান পা তুলে বসে সোফায় হেলান দিলেন। একটু হাসলেন কি? বাকি পত্রিকাগুলো সামনের সেন্টার টেবিলে রেখে দিয়ে একটার কয়েকটা পাতা ফরফর করে উলটে গেলেন। তারপর বললেন, “সবই পুরোনো। যদিও খুব বেশি পুরোনো নয়।”
“সাত বছর।” তীর্থঙ্কর এখন অনেক আত্মবিশ্বাসী।
“এরকম কি হতে পারে?” কমিশনার দোরজি যেন নিজেকেই প্রশ্ন করেন। একটু থেমে আবার নিজেই উত্তর দেন, “সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু আপনাদের ভাগ্য ভালো যে আমি ছোটবেলায় এইচ জি ওয়েলস পড়েছি। কাজেই বিশ্বাস করছি কম করে হলেও সম্ভাবনা আছে। এদিকে গত কয়েকমাস ধরে ভারতবর্ষে অনেক কিছু ঘটেছে। তো এবার সময় ভ্রমণ! অতীত থেকে ভবিষ্যতে।”
থামলেন কমিশনার। শ্যেন চোখে তীর্থঙ্করদের প্রত্যেক সদস্যকে আলাদা আলাদা করে নজর করলেন। মহিমার মনে হল যেন বলিউডি হিন্দি সোপ অপেরা সিরিয়ালের সুটিং হচ্ছে। তারপর কমিশনার একটু যেন ব্যঙ্গের মুচকি হাসি দিয়ে তীর্থঙ্করকে বললেন, “ভালো। কিন্তু আপনার এই সময় আর স্থান নির্বাচন ঠিক হয়নি। আপনার আরও দূর অতীত থেকে কিংবা অন্য জায়গায় নিজেদের রেখে তারপর এই গল্পটা লিখতে হত।”
“কমিশনার, আমি কোনও গল্প বানাচ্ছি না। কাজেই কোনও সময় বা স্থান নির্বাচন করেছি তা-ও নয়। এই ব্যাপারটা কী বা কীভাবে হয়েছে, সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই। শুধু দেখতে পাচ্ছি এরকম হয়েছে। এর সঙ্গে সময় ভ্রমণের কোনও সম্পর্ক আছে কি না জানি না, তবে স্থান-কালের কিছু একটা ব্যাপার আছে বলে আমার মনে হচ্ছে,” তীর্থঙ্কর কিন্তু আর আত্মবিশ্বাস হারাচ্ছে না। তা সে যতই এই কমিশনার লোকটা ব্যঙ্গের হাসি হাসুক বা যা খুশি বলুক। তাঁদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া এই ব্যাপারটা এখন তার কাছে অনেকটাই স্পষ্ট।
“সেক্ষেত্রে আপনি নিশ্চয়ই বিশেষ কিছু করেছিলেন ওই সাত বছর আগের দিনটিতে? কি করেছিলেন— কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানীরিক্ষা?”
তীর্থঙ্কর মাথা নাড়ে। “না। কিছুই না। আমরা ঘুম থেকে উঠলাম। আর… আর আমরা এখানে, এই সময়ে।”
(৭)
কমিশনার দোরজি গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। চুপ করে বসে রইলেন। তীর্থঙ্করের বক্তব্য তাঁর কাছে সময় পরিভ্রমণের কল্পবিজ্ঞান বলে মনে হচ্ছে। বাস্তবিকতার দিক দিয়ে আপাত-অসম্ভব। এই দু-হাজার উনচল্লিশেও যার কোনও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ নেই। আবার যা কিছু বাস্তব নিদর্শন এবং প্রমাণ তিনি নিজের চোখে এখানে দেখছেন তা সবই সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? যদি না…
একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিলেন কমিশনার। তারপর বললেন, “শুনুন। আপনার কথা অনুযায়ী এখানে আপনারা সাত বছর ভবিষ্যতে এগিয়ে এসেছেন। তাই তো? সময়ের মধ্যে দিয়ে ভ্রমণ করেছেন। স্থান একই আছে— সময়টা শুধু এগিয়ে এসেছে। যদিও আমরা কিন্তু এখনও এই সময় পরিভ্রমণের ব্যাপারে সঠিক কিছু জানি না। এই নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা কোনও কাজ এখনও পর্যন্ত করেননি। এমনকি আমাদের সামরিক বিভাগেও এই নিয়ে কোনও তথ্য বা এর সম্ভাবনার বিষয়ে কোনও রিপোর্ট নেই।”
“আচ্ছা, কীভাবে যুদ্ধ শুরু হল?” মহিমা মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন।
“শুরু? এটা নতুন করে কিছু শুরু হয়নি। আপনাদের মনে নেই? যুদ্ধ তো সাত কেন তারও কয়েক বছর আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল,” কমিশনার দোরজি মহিমাকে বলেন।
তীর্থঙ্কর বলে, “সেগুলো নয়। ওসব তো ছুটছাট ব্যাপার ছিল। এই যে আসল যুদ্ধ, এটা কবে শুরু হয়েছে?”
“আসলে এই যুদ্ধের শুরুর কোনও প্রকৃত শুরুয়াতি-বিন্দু নেই। টুকরো টুকরো আঘাত-প্রত্যাঘাত. আতঙ্কবাদী হামলা, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক বা নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম চলছিলই।“ হঠাৎই প্রসঙ্গ পালটে তীর্থঙ্করকে জিজ্ঞেস করেন, “আচ্ছা ২০১৯ সালে আপনারা কোথায় ছিলেন?”
তীর্থঙ্কর মহিমার দিকে তাকায়। তারপর দোরজির উদ্দেশ্য বলে, “সে সময় আমরা ছিলাম কলকাতায়। জিনিয়া সেই বছরেই জন্মায়।”
“তো আপনাদের নিশ্চই পুলোয়ামা অ্যাটাক আর তারপর হওয়া সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের কথা মনে আছে? আর তারপর তো ওই বছরের শেষে হল চীনের সঙ্গে ডোকালাম সংঘর্ষ আর পরের বছর ২০২০ সালে আবার চীনের সঙ্গে গালোয়ান সংঘর্ষ। তারপর কিছুদিন বাদ দিয়ে ২০২৪ সালে একই সময়ে আর একই সঙ্গে শুরু হয় পূর্বপ্রান্তে অরুণাচলের দিক দিয়ে চীনের আক্রমণ আর পশ্চিম প্রান্তে পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিতীয় কার্গিলের যুদ্ধ। এই দুটো মিটে যেতেই ২০২৮ সালের বালুচিস্তানের যুদ্ধ। যেটা ১৯৭১-এর বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা মনে করিয়ে দিয়ে স্বাধীন বালুচ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। আর ঠিক তারপরে থেকেই চীনের সঙ্গে শুরু হয়ে যায় ক্রমাগত আজ এখানে কাল ওখানের রোজকার খটাখটি। যা ২০৩২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউএনও আর ইউএস-এর মধ্যস্থতার মাধ্যমে হওয়া বেইজিং শান্তি চুক্তির মধ্যে দিয়ে আপাতভাবে থামে।”
তীর্থঙ্কর বলে, “এই তো মাসছয়েক আগেই সেটা হল। এর মধ্যে আবার কখন যুদ্ধ শুরু হল?”
কমিশনার দোরজি তীর্থঙ্করের কথায় চুপ করে গিয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর নোটপ্যাডটা খুলে কিছুক্ষণ আঙুল চালালেন তার উপর। তারপর কিছু একটা তাতে পেয়ে গিয়ে মনোযোগ দিয়ে সেটা দেখলেন। তারপর যেন নিজের মনেই হেসে উঠলেন। নোটপ্যাডটা বন্ধ করে পকেটে রেখে দিয়ে তীর্থঙ্করকে বললেন, “হ্যাঁ। এবার বুঝলাম। আপনি যা বলতে চাইছেন সেই হিসেবে আজ থেকে সাত বছর আগে ওই ২০৩২ সালে, গতকালকের তারিখেই ভারতের এই পূর্বাঞ্চলে চীন হঠাৎ করেই মিসাইল দিয়ে আক্রমণ শুরু করে। আর সেইদিন থেকে বলা যেতে পারে নিয়মিত যুদ্ধ চলছে। আর আজ এই সাত বছরে তো গোটা পৃথিবী দুটো ভাগে ভাগ হয়ে লড়াই করে চলেছে। এটা এখন নিউজ এজেন্সিগুলোর ভাষায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তো সে যা হোক, সাত বছর আগের গতকালের এই দিনটাতেই হয়েছিল এই এলাকায় প্রথম বোমা বর্ষণ। একের পর এক মিসাইলের আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এই এলাকাটা। আর এর প্রধান লক্ষ্যই ছিল এই এলাকাটা। যেটাকে ভারতের মানচিত্রে চিকেন নেক বা মুরগির গলা বলা হয়। ভৌগলিক দিক দিয়ে এটা যদি চীন দখল করতে পারত সেইদিন, তো পুরো পূর্বাঞ্চলের উপর বাকি ভারতের আর কোনও যোগাযোগ বা নিয়ন্ত্রণ থাকত না। আর ওই আক্রমণ হয়েই ছিল সেই লক্ষ্যে। তাই বলা যায় যুদ্ধটা আসলে ওই দিন থেকে বিস্তৃত হতে লাগল। যুদ্ধটা ওই দিন থেকে শুরু হয়নি, যুদ্ধ আসলে চলছিলই।” বলেই আচমকা নোটপ্যাডটা বন্ধ করে পকেটে ঢুকিয়ে নিলেন কমিশনার দোরজি। তারপর ঝুঁকে বসে একটু এগিয়ে এলেন তীর্থঙ্করের দিকে।
“কিন্তু, আমি যদি আমার রিপোর্টে কর্তৃপক্ষকে জানাই যে আপনারা ২০৩২-এর বোম পড়ার এক রাতে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন আর তারপর ঘুম থেকে উঠে সোজা চলে এলেন এই ২০৩৯-এ, তো কর্তৃপক্ষ সেই রিপোর্টটা সন্দেহজনক বলে দাগিয়ে তো দেবেই, সেই সঙ্গে ভাববে আমারও নিশ্চই ভষ্মরোগ হয়েছে। কাজেই…”
বিদিশা মাঝপথে প্রশ্ন করে ওঠে, “সেটা আবার কী রোগ?”
বিদিশার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন কমিশনার। তারপর যেন বোঝাচ্ছেন এমন ভাবে বললেন, “ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে এখন এই গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গ আর বিহারের পুরো উত্তর দিকের গোটা এলাকা চীনা মিসাইলের আঘাতে আঘাতে প্রায় ধ্বংসস্তূপ। তার ফলে এখানকার আবহাওয়ায় একধরনের বিকিরণ ছড়িয়ে পড়েছে, কোনও আনবিক বোমা ব্যবহৃত না হওয়া সত্ত্বেও। আর তাই চারদিকের এই বিকিরণের আবহাওয়ায়, এদিকে যারা থাকছে, কাজ করছে, তাদের প্রত্যেকের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে রেডিয়ো অ্যাক্টিভ কণা। সারাক্ষণ মাস্ক পড়ে থাকা সত্ত্বেও। আর সেগুলো ব্রেনে গিয়ে মানুষকে মানসিক রোগগ্রস্ত করে তুলছে। এটাকেই এখন ভষ্মরোগ বলছে।”
“আমি… আমি জানতে চাই কে জিতছে?” কমিশনারের বলার স্বরে অরিন এবার আবার সাহস করতে পেরে তার নিজস্ব প্রশ্নের উত্তর পেতে চায়। আবার তার সঙ্গে যোগ করে, “তা ছাড়া বাইরে ওটা কি ছিল? ওই ট্রাকের মতো? ওটা কি রকেটের সাহায্যে চলে?”
“ওই অহীবাহন? না, না। ওটা টারবাইনের সাহায্যে চলে। ওর টারবাইনের সামনেটা বোরিং মেশিনের মতো যেটা সামনে যা আসুক সেটাকে কেটে বেরিয়ে যেতে পারে। এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চলার উপযুক্ত।“
“সাত-সাতটা বছর!”, মহিমা বলেন, “এর মধ্যে দুনিয়াটা কতটা পালটে গেছে! বিশ্বাস করাই কঠিন। অসম্ভব মনে হচ্ছে।”
কমিশনার দোরজি কাঁধ ঝাঁকান। “অনেক। অনেক পালটে গেছে। আমার নিজেরও তাই মনে হয়। আমার মনে আছে মাত্র সাত বছর আগে আমি কী করতাম। আমি তখন সবে কিছুদিন হল কলেজ ছেড়েছি। তখনও পড়াশোনা করছি। ওই চাকরিবাকরির পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। আমাদের একটা ফ্ল্যাট ছিল। একটা গাড়িও। রোজ ক্লাবে নাচতে যেতাম। স্বপ্ন ছিল প্রভু দেবার বা টাইগার শ্রফ হব। টিভিতে নেটফ্লিক্স কানেকশন নিয়েছিলাম। বলিউড হলিউডের যত নাচের সিনেমা আর প্রোগ্রাম, সে সব দেখে দিন কাটছিল। স্বপ্নের মতো। কিন্তু স্বপ্নের দিন ফুরিয়ে গিয়ে হঠাৎই সন্ধ্যা নেমে এল। আসলে আসছিলই। ধীরে, কিন্তু নিশ্চিন্তে। শুধু আমি জানতাম না। আমরা কেউই জানতাম না। কিন্তু সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সবরকম লক্ষণ ছিল। এখন পেছনে তাকিয়ে দেখতে পাই। শুধু তখন যদি সবাই মিলে দেখার চেষ্টা করতাম! হয়তো সন্ধ্যার গোধূলি লগ্ন এত তাড়াতাড়ি নেমে আসত না।”
“আপনি কি রাজনৈতিক পুলিশ বিভাগে কাজ করেন? এটা কী ধরনের পুলিশ?” তীর্থঙ্কর প্রশ্ন করে। একজন সেনাপুলিশের কাছ থেকে এমন কাব্যময় কথাবার্তা তীর্থঙ্করকে কৌতুহলী করে তোলে।
“আমি সৈন্যবাহিনীর তত্ত্বাবধান করি বলতে পারেন। সৈনিকদের রাজনৈতিক বিচ্যুতির দিকে নজর রাখি। জনগনের রাজনৈতিক বিচ্যুতির দিকে নজর রাখি। একটা সর্বাত্মক যুদ্ধে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন নজরদারি রাখতে হয়। নিজেদের লোকেদের উপরে, দেশের লোকেদের উপরে, এমনকি শত্রু দেশের উপরেও। বিশেষত আমাদের এখন যুদ্ধ চলছে চীন আর পাকিস্তানের সঙ্গে। একসঙ্গে। একটা উগ্রপন্থী অধ্যুষিত দেশ তো অন্যটা এক কম্যুনিজমের নামে ভেকধারী এক স্বৈরতন্ত্রী পুঁজির দেশ। এক দল আমাদের দেশের এক শ্রেনীর মানুষকে ধর্মের নামে তো আরেক দল টাকা ছড়িয়ে দেশের আরেক শ্রেনীর মানুষের মন বিষাক্ত করে তাদের দেশদ্রোহী করে তুলছে। এই যুদ্ধের সময়ে একজন দেশদ্রোহী যদি আমাদের সিস্টেমের মধ্যে ঢুকে পড়ে তো আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাই আমরা কোনও সুযোগ দিতে চাই না।”
তীর্থঙ্কর অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। কমিশনারের শেষের দিকের কথাগুলো একটাও তার কানে ঢোকে না। ও তাকিয়ে আছে কমিশনারের দিকে। কিন্তু দেখছে না। কমিশনারের কথাগুলো তার কানের পর্দায় শুধু গুনগুন করে গুঞ্জন তুলে থেমে যায়। অর্থময় কোনও ছবি তাঁর মাথার ভেতরে তৈরি হয় না। সে যেন ডুবে গেছে এক গভীর ভাবনায়। তারপর কমিশনার থামতেই বিড় বিড় করে বলে ওঠে, “হ্যাঁ। এগুলোর সবই ছিল আমাদের সামনে। এই দিনের আলো মিলিয়ে আসার সব ধরনের চিহ্ন সবরকমভাবেই বর্তমান ছিল। আমরাই শুধু তা দেখছিলাম না। সন্ধ্যা যে নেমে আসছে, গোধূলি লগ্ন যে বয়ে যাচ্ছে আর কালরাত্রির নেমে আসা যে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে তা আমারা কেউই বুঝতে পারিনি।”
ততক্ষণে কমিশনার দোরজি উঠে পড়েছিলেন। তীর্থঙ্করের বইয়ের আলমারি কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বইগুলো দেখেছিলেন। “আমি এখান থেকে কয়েকটা নিয়ে যাব। অনেকদিন কোনও বই পড়িনি। এখন আর এদিকে পাওয়াও যায় না। সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সেই ২০৩২-৩৩শে।”
তীর্থঙ্করও উঠে এসে কমিশনারের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে। এবার আলমারির কাচের স্লাইডিং দরজাটা খুলে দেয়। বলে, “পুড়ে গিয়েছে? সব?”
কমিশনার দোরজি হাত বাড়িয়ে কয়েকটা বই বার করেন। “রবীন্দ্রনাথ, প্রেমচন্দ, আর কে নারায়ণ। ভি এস নইপল। আমি এই পুরোনো ক্ল্যাসিকালগুলো নেব। এগুলো নিরাপদ। ওই তারাশঙ্কর আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা এই নবারুন ভট্টাচার্য নেওয়ার ইচ্ছে থাকলেও নেওয়া উচিত হবে না। এতে আমার মতো পোড়খাওয়া রাপু কমিশনারও ঝামেলায় পড়ে যেতে পারে। বুঝলেন?” বলে তীর্থঙ্করের মুখোমুখি হলেন, বললেন, “আর আপনারা যদি এখানে থাকতে চান তো এই বইগুলো সরিয়ে ফেলুন।”
তীর্থঙ্কর দেখে কমিশনার তাঁকে কার্ল মার্ক্সের ‘দাস ক্যাপিটাল’ বইটা আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন।
“যদি আমরা থাকতে চাই! আমাদের আর অন্য কিছু করার উপায় আছে কি?”
“আপনারা থেকে যেতে চান?”
“না”, মহিমা শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বলে ওঠে।
(৮)
কমিশনার দোরজি ঘুরে মহিমার দিকে তাকালেন। “ঠিক। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় না আপনাদের এখানে থেকে যাওয়াটা ঠিক হবে। প্রথম কথা এখানে থেকে গেলে আপনাদেরকে আলাদা করে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় কথা, আপনাদের সময় ভ্রমণের ব্যাপারটা র-এর হাই সেন্ট্রালকে বোঝানো যাবে না। আর তাই আমার রিপোর্টে আপনাদের অজ্ঞাত পরিচয় হিসেবে দেখাতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনাদের আলাদা শুধু নয়, হয়তো শাস্তি ভোগ-ও করতে হতে পারে।”
“আলাদা করে দেওয়ার মানে কীরকম?” মহিমা জানতে চায়।
“যদি কোনও বড় শাস্তি আপনাদের উপর লাগু না হয় তো আপনাদের প্রথমেই প্রত্যেকের থেকে প্রত্যেককে আলাদা করে দেওয়া হবে। যেমন, বাচ্চাদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে তামিলনাড়ুর পূনর্বাসন কেন্দ্রে, আপনাকে পাঠানো হবে মাটির তলার মহিলা শ্রমিক শিবিরে আর তীর্থঙ্করবাবুকে পুরুষ হিসেবে অবশ্যই সামরিক বিভাগে।“
তীর্থঙ্কর বলে ওঠে, “ওই যে তিনজন সৈনিক একটু আগে এখান থেকে গেল, ওই রকম?”
কমিশনার বলেন, “হ্যাঁ। একমাত্র যদি আপনি আইডিটি ডিপার্টমেন্টের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হন তো অন্য কথা।”
“সেটা কি?”
“ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনিং এন্ড টেকনোলজি। আপনার কি বিশেষ কোনও ট্রেনিং নেওয়া আছে? ভালো হবে যদি বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির কোনও শাখায় করা থাকে।”
“উঁহু। আমি বাণিজ্য শাখার লোক। হিসাবরক্ষক।”
কাঁধ ঝাকালেন কমিশনার দোরজি। বললেন, “সেক্ষেত্রেও আপনার আর একটা সুযোগ অবশ্য থাকবে। আপনাকে একটা ইউপিএসসি রাপু নিয়োগ পরীক্ষা দিতে দেওয়া হবে। যদি আপনার আইকিউ যথেষ্ট বেশি পাওয়া যায় তো আপনাকে রাজনৈতিক পুলিশের কাজ দেওয়া হবে। এখানে প্রচুর লোকের দরকার পড়ে,” বলতে বলতে চুপ করে যান তিনি। দু-হাতে বইগুলো ধরে রেখে কিছু চিন্তা করেন খানিক। তারপর আবার বলেন, “তীর্থঙ্করবাবু, আপনাদের ফিরে যাওয়াই ভালো। এখানে মানিয়ে নিতে আপনাদের অসুবিধা হবে। আমিও পারলে ফিরে যেতাম। যদি সেটা সম্ভব হত। কিন্তু সেটা আর হবে না।”
মহিমা বলে, “ফিরেই তো যেতে চাই। নিশ্চই যাবো। কিন্তু কী ভাবে?”
“যেভাবে আপনারা এসেছেন।”
“আমরা তো এমনিই চলে এসেছি। মানে, ঘুমের মধ্যে চলে এসেছি।”
কমিশনার দোরজি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। “কাল রাতে ইদানিং কালের মধ্যে সবথেকে ভয়ংকর ‘রম’ আক্রমণ হয়েছিল। চীনারা এদিকের গোটা এলাকায় একসঙ্গে আক্রমণ করেছিল।”
“রম?”
“রম— আরওএম। রোবট অপারেটেড মিসাইল। চাইনিজরা পরিকল্পনা মাফিক ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এলাকাগুলো ধ্বংস করতে চাইছে। কিলোমিটারের পর কিলোমিটার এলাকা একসঙ্গে আক্রমণ করে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। এই রম মিসাইলগুলো এই কাজে সেরা। সস্তাও। ওরা কোটি কোটি বানাচ্ছে আর ছুড়ছে। পুরো পদ্ধতিটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালাচ্ছে। রোবট নিয়ন্ত্রিত কারখানায় তৈরি করে ওই রোবট দিয়েই ছুড়ছে আমাদের উপর। কাল রাতে তো সবথেকে ভয়ংকর করেছে। এই এলাকার প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে বোধহয় একটা করে ফাটিয়েছে। সেজন্যই আজ সকালে টহলদারি দলটাকে এদিকে পাঠানো হয়েছিল, যদিও ওরা কোথাও কিছু পায়নি। না জীবিত, না মৃত। একমাত্র আপনাদের ছাড়া।”
তীর্থঙ্কর মাথা নাড়ে, “হুম, এতক্ষণে বোঝা যাচ্ছে।”
“সম্ভবত একসঙ্গে এতটাই শক্তি গতরাতে এখানে রম বিস্ফোরণে মুক্ত হয়েছিল যে তা কোনওভাবে স্থান-কালের বিন্যাসে একটা সময়-বিচ্যুতির সৃষ্টি করতে পেরেছিল। ভূমিকম্পের মতোই সময় বা কাল-কম্পন… ব্যাপারটা রীতিমতো আশ্চর্যের। আমরা ভূমিকম্প বলে যেটা জানি সেটা যেমন পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠের নীচের প্লেটগুলোর সংঘর্ষের ফলে তৈরি হওয়া ঘনীভূত শক্তিপুঞ্জর বেরিয়ে আসার ফলে ভূপৃষ্ঠের উপরের স্তরের কম্পন তেমনি ভয়ংকর বিস্ফোরণে পুঞ্জিভূত শক্তি কোনও কারণে ঘনীভূত হয়ে সহসা নির্গমনের মুহূর্তে কালের প্রবাহের একটা বিচ্যুতি বিন্দু হয়তো তৈরি করে ফেলে। কোনওভাবে। জানি না কেমন করে। তবে আমার মনে হচ্ছে এরকম কিছু একটা হয়ে থাকতে পারে। সেই বিশেষ মুহূর্তে যখন বস্তুর ধ্বংসের কারণে ঘনীভূত শক্তি বিভিন্ন তরঙ্গে নির্গত হচ্ছিল তখন কোনও ভাবে আপনাদের সহ আপনাদের বাড়িটা এক বিশেষ তরঙ্গের সঙ্গে মিলে গিয়ে অনুরণিত হয়ে টেনে নিয়ে আসে ভবিষ্যতে। টেনে এগিয়ে নিয়ে আসে সাত বছর পরের আজকের দিনটায়। এই রাস্তাটা, এই পাড়াটা, এখানের সব কিছুই, আসলে বিস্ফোরণে প্রচণ্ড শক্তির প্রকোপে বাতাসে মিশে গেছে। আর সেই শক্তিই সময়-বিচ্যুতির ফুটো দিয়ে টেনে আপনাদের বাড়িটাকে সাত বছর এগিয়ে নিয়ে এসে আজকের দিনে বসিয়ে দিয়েছে।”
তীর্থঙ্কর আর মহিমা অবাক হয়ে কমিশনার দোরজির ব্যাখ্যা শুনছিল। মহিমার দিকে একবার তাকিয়ে তারপর তীর্থঙ্কর বলে, “আমাদের টেনে ভবিষ্যতে নিয়ে এল! গতকাল রাতে! যখন আমরা ঘুমিয়েছিলাম!” একটু চুপ করে থেকে তীর্থঙ্কর আবার বলে, “কীভাবে সেটা সম্ভব? মানে, এইভাবে ভর বা বস্তুর থেকে যখন শক্তি বেরিয়ে আসে তখন কি কোনও ওয়ার্মহোল তৈরি হতে পারে?”
কোলের উপর তুলে রাখা বইগুলো নাড়াচাড়া করছিলেন কমিশনার দোরজি। তীর্থঙ্করের দিকে তাকিয়ে খানিক চুপ করে রইলেন। উত্তর দেওয়ার আগে যেন নিজের চিন্তাভাবনা গুছিয়ে নিতে চাইলেন। তারপর একটু বিষন্ন হেসে বললেন, “দেখুন, আমি বৈজ্ঞানিক নই। স্কুল কলেজের পর ফিজিক্স বই আর ছুঁয়ে দেখিনি। তবে বিভিন্ন বইপত্র ইত্যাদিতে যা পড়েছি সেই হিসেবে একটা আন্দাজ শুধু দিতে পারি। আপনি যে ওয়ার্মহোলের কথা বলছেন সেটা সাধারণত স্থান ভিত্তিক হয়। কাল ভিত্তিক নয়। যেন একটা পোকা একটা আপেলের একদিক থেকে খেতে খেতে সরাসরি অন্যদিকে বেরিয়ে এল। এবার ধরুন একটা পিঁপড়ে যদি এখন ওই আপেলটায় উঠে পড়ে তো ওটার সামনে আপেলটার একদিক থেকে বিপরীত অন্য দিকে পৌঁছোনর জন্য দুটো রাস্তা থাকছে। যদি পোকায় খাওয়া ফুটোটা খুঁজে না পায় তো গোটা আপেলটার উপর দিয়ে চলে অন্যদিকে নামবে— মানে গোলোক এর পৃষ্ঠতল বরাবর পিঁপড়েটাকে হাঁটতে হচ্ছে। আর ফুটোটা খুঁজে পেলে সরাসরি এপাশ থেকে ওপাশে ব্যাস বরাবর হাঁটলেই পৌঁছে যাবে অন্য পাশে। এবার ধরুন, ওটা আপেল বা গোলাকার কিছু নয়— মানে এবার ওটাকে চ্যাপটা কিছু ভাবুন। ধরুন বিস্কিট— এই ক্ষেত্রে পৃষ্ঠতল বরাবর একদিক থেকে অন্যদিকে যাওয়া আর সরাসরি কোনও ফুটো দিয়ে অন্যদিকে যাওয়া— দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনেক কম সময়ে অনেকটা বেশি পথ পেরোতে পারবে। তো, এই মহাবিশ্বে, যেখানে দূরত্ব আলোকবর্ষে মাপা হয় সেখানে এই ওয়ার্মহোল খুঁজে পেলে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়া অনেক সহজ হয়ে যায়। কিন্তু এটা সাধারণত স্থানিক-মাত্রার ব্যাপার। তবে আপনাদের ব্যাপারটা কিন্তু অন্যরকম। আপনারা অন্য কোথাও যাননি বা পৌঁছোননি। একই জায়গায় রয়েছেন। শুধু সময়টা এগিয়ে এসেছে। মানে এটা সময়-মাত্রার কিছু ব্যাপার হয়েছে। বলে যে সময়ের গতি একমুখী— গতকাল থেকে আজ হয়ে আগামীকাল। উলটোটার এখনও পর্যন্ত কোনও তাত্ত্বিক প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি। যেন একটা তির-ধনুকের জ্যা-থেকে বেরিয়ে সোজা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তিরটার মতোই সময়-ও একমুখী সোজা ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলে। এবার ধরুন কোনওভাবে, সেটা হঠাৎ করে একরাশ শক্তির কোনও একটি বিন্দুতে পুঞ্জিভূত হয়ে গিয়ে তারপর সহসা ছড়িয়ে পরার কারণে বা অন্য কিছু কারণে-ও হতে পারে, সেই সময়ের তিরটাকে বেঁকিয়ে বা ভাঁজ করে ফেলল। আর আপনাদের এই বাড়ির স্থানটা যদি সময়ের একটা ভাঁজ থেকে অন্য ভাঁজে কোনওভাবে পৌঁছে যেতে পারে তো সেটা সময়-লম্ফনের মতোই একটা ব্যাপার হতে পারে। আর আমার মনে হচ্ছে যে গতরাত্রের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে এরকম কিছু একটা হয়ে থাকতে পারে।”
কমিশনার দোরজি অনেকটা এক নাগাড়ে বলে দম নেওয়ার জন্য থামলেন। খানিকক্ষণ চুপ করে তীর্থঙ্করদের দেখলেন। কিছু ভাবছিলেন। “আজ রাতে”, একটু থেমে তিনি আবার বললেন, “যা খবর আছে সেই হিসেবে আজ রাতেও আবার আক্রমণ হবে। উপগ্রহ চিত্রের বিশ্লেষণ বলছে প্রচুর রম রোবট মিসাইল তৈরি হয়েছে এই দিকের উদ্দেশে। যা কিছু বাকি আছে এই এলাকায় আজ রাতে সে সমস্ত ধুলিস্যাৎ করবার পরিকল্পনা করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। চীন সম্ভবত এই মুরগির গলার অংশটা আগামী কালের মধ্যে দখল করতে চাইছে।” ঘড়িতে সময় দেখবার জন্য থামলেন কমিশনার। দেখে নিয়ে বললেন, “এখন বিকেল চারটে বাজে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আক্রমণ শুরু হবে। আপনাদের সে সময় মাটির নিচে থাকাই ভালো। ওপরের কোনও কিছুই আর গোটা থাকবে না। আমি আপনাদের আমার সঙ্গে নীচে নিয়ে যেতে পারি। যদি আপনারা চান। আর যদি আপনারা একটা সুযোগ নিয়ে দেখতে চান তো… যদি আপনারা এখানেই থাকতে চান…” থেমে গেলেন কমিশনার দোরজি।
“আপনার কি মনে হয় আজ রাতের বিস্ফোরণে সময়ের উলটোযাত্রা হতে পারে?”
“হয়তো। আমি জানি না। এটা একটা জুয়ো খেলা। হয়তো তা আপনাদের উলটো পথে ফেরত নিয়ে গিয়ে আপনাদের সময়ে পৌঁছে দেবে। অথবা দেবে না।”
তীর্থঙ্কর বলে, “আর যদি দেয়-ও, তো সেক্ষেত্রে আমরা কীভাবে নিজেদের সময়ে ফিরব? অন্য কোনও সময়েও তো চলে যেতে পারি? আরও ভবিষ্যতে কিংবা আরও অতীতের দিকে?”
এবার হেসে ফেললেন কমিশনার দোরজি। তারপর বললেন, “হতেই পারে। দেখুন পুরোটাই সম্ভাবনার খেলা। আপনাদের সপক্ষে একটাই ব্যাপার যে এই মুহূর্তে এই স্থান শক্তির অসাম্যের কারণে সময়ের তীরের ভাঁজ বরাবর এগিয়ে এসেছে। এবার যদি কোনওভাবে আবার সেই একত্রিত জমাট বাঁধা শক্তির নির্গমনের কারণে সেই সাম্য ফেরত আসে তো সেই অহং মুহূর্তে সময়ের তীরের ভাঁজ খুলে গিয়ে সময়ের তিরটা আবার সোজা হয়ে যাবে। আর একই সঙ্গে আপনাদের এই স্থানটা তখন তার প্রকৃত সময়-বিন্দুতে পৌঁছে যেতেই পারে। সম্ভাবনার বিচারে এটা হওয়ার সুযোগ বেশি হলেও আপনি যেমন ভাবছেন তেমনটাও হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে যে সময়ের যে ভাঁজের কারণে আজকে আপনারা এখানে, সেই ভাঁজ আর সোজা হলই না। সেক্ষেত্রে আপনাদের কোথাওই পৌঁছে দেবে না। আর যদি না দেয় তো—”
“যদি না দেয় তো… আমাদের বাঁচবারও কোন সুযোগ থাকবে না, তাই তো?”
কমিশনার দোরজি উত্তর দেন না। যদিও দেওয়ার মতো কোনও উত্তর-ও ওঁর কাছে নেই। উনি পকেট থেকে নোটবুকটা বের করে মাঝখান থেকে ভাঁজ খুলে টেনে ছড়িয়ে টেবিলের উপর রাখলেন। আঙুলের দ্রুত চলনে নোটপ্যাডটা অন করে একটা লাইভ ম্যাপ খুলে জুম করে বাড়িটার এলাকা দৃশ্যমান করলেন। তারপর নির্দেশ করলেন বাড়িটা থেকে সাতশো-আটশো মিটার দূরের একটা বিন্দু। তীর্থঙ্করকে দেখিয়ে বললেন, “এর কাছাকাছি জায়গায় একটা টহলদারি দলের গাড়ি থাকবে আরও আধঘণ্টার মতো। যদি আপনারা আমাদের সঙ্গে মাটির নিচের বাঙ্কারে আশ্রয় নিতে চান তবে এই রাস্তাটা ধরে চলে আসবেন।” আঙুল দিয়ে টেনে একটা লাল রং-এর রেখা বানিয়ে ম্যাপে বাড়িটাকে আটশো মিটার দূরের একটা বিন্দুতে জুড়লেন। বললেন, “এই ফাঁকা মাঠের মতো জায়গাটায় একটা অহীবাহন দেখতে পাবেন। এটায় রাপুর একটা দল আরও আধঘণ্টা থাকবে। ওরা আপনাদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেবে। মনে হয় আপনি এই ফাঁকা মাঠটা খুঁজে নিতে পারবেন। পারবেন না?”
“মনে হয় পারব” তীর্থঙ্কর নোটপ্যাডে পথের মানচিত্রটা ভালো করে দেখে মাথায় তুলে নেয়। দেখতে গিয়ে ও-র একটা কেমন খটকা লাগে। তারপর হঠাৎই ও বুঝতে পারে। ঠোঁটের কোণে একটা হালকা হাসি জেগে ওঠে। বলে, “কমিশনার, ওখানে না পৌঁছোনর কোনও কারণ নেই। ওই ফাঁকা মাঠের জায়গাতেই আমাদের বাচ্চাদের স্কুলটা ছিল। সুকনা রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল। আজ সকালেও ওরা ওখানেই যাচ্ছিল যখন আপনাদের ওই টহলদার বাহিনী ওদের আটকায়। এই তো কিছু সময় আগেই।”
“উঁহু। সেই স্কুলটা ছিল সাত বছর আগে,” কমিশনার দোরজি তীর্থঙ্করের ভুলটা শুধরে দেন। নোটপ্যাডটা বন্ধ করে আবার ভাঁজ করে নিয়ে পকেটে ঢোকান। তারপর পেছনে ঝুলিয়ে রাখা মাস্কটা পড়ে নিয়ে হেলমেটটা তার ওপরে বসিয়ে নেন। দু-হাতে পছন্দ করে রাখা বইগুলো তুলে নিয়ে বাইরের দিকে এগিয়ে গেলেন। ভাঙা দরজা পেরিয়ে সামনের লনে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়ালেন একবার। বললেন, “হয়তো আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। হয়তো হবে না। আপনাদের সিদ্ধান্তের উপর ওটা নির্ভর করছে। আপনাদের কোনও একটা পথ ঠিক করে নিতে হবে— এদিকে না ওদিকে। যেদিকেই যান প্রার্থনা করি আপনাদের ভালো হোক। বাচ্চারা মানুষের মতো মানুষ হোক। যাই হোক, ভালো থাকুন। চলি।”
পেছন ঘুরে সামনের দিকে দ্রুত গতিতে হাঁটতে হাঁটতে ক্রমশ বাড়িটাকে পেছনে ফেলে দূরের ধ্বংসস্তূপের ওপাশে হারিয়ে গেলেন কমিশনার দোরজি।
(৯)
বাড়িটা এখন ফাঁকা। শুধু ওরা পাঁচ জন। যেমন সকালে ঘুম থেকে উঠে ওরা ছিল। না ঠিক তেমন নয়। এখন সামনের দরজাটা ভাঙা পড়ে আছে। আর ওরা এখন জানে যে ওদের গতকালের রাতটা পড়ে আছে সাত বছর পেছনে।
পাঁচ জনেই রয়েছে ড্রইং রুমে। প্রথম সুযোগেই অরিন প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বাবার উপর। “বাবা… বাবা, তুমি সৈন্যবাহিনীতে ঢুকবে? ওই রকম বন্দুক নিয়ে লড়াই করবে?” ওর চোখ দুটো উত্তেজনায় চকচকে করে। “তুমিও ওই রকম একটা সাপের মতো অহীবাহন চালাবে?”
তীর্থঙ্কর নীচু হয়ে ছেলেকে কাছে টেনে নিলেন। আদর করে কপালের উপর পড়ে থাকা চুলগুলো আঙুল দিয়ে পেছনের দিকে ঠেলে দিয়ে গালটা একটু টিপে দিলেন। বললেন, “তুমি তাই চাও? তুমি এখানে থেকে যেতে চাও? যদি ওইরকম মুখোস পড়ে ওরকম বন্দুক হাতে নিয়ে আমাকে লড়াই করতে হয় তো আমাদের ফিরে যাওয়া চলবে না।”
অরিনকে চিন্তিত মনে হয়, “আমরা ক-দিন পরে যেতে পারি না?”
তীর্থঙ্কর মাথা নাড়েন। “না, অরিন। সেটা মনে হয় না করা যাবে। আমাদের এক্ষুনি ঠিক করতে হবে যে আমরা ফিরে যাবো না কি এখানেই থেকে যাবো।”
বিদিশা হতাশার সুরে বলে, “ওই কমিশনার তো বলে গেলেন যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আবার সেই আক্রমণ শুরু হবে।”
তীর্থঙ্কর উঠে পড়ে। ঘরটার মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করে। ওকে চিন্তামগ্ন এবং উদ্বিগ্ন দেখায়। মহিমা নিশ্চুপে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকে। অরিন, জিনিয়া আর বিদিশা মা-বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে।
তীর্থঙ্কর পায়চারি করতে করতে যেন নিজেকেই বলে চলে, “যদি আমরা আধঘণ্টার মধ্যে বেরিয়ে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় জোগাড় না করে এখানে এই ঘরটায় থেকে যাই তো কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হয়তো এই বাড়িটার সঙ্গে আমরাও মিসাইলের বিস্ফোরণে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাব। ধরা যাক আমরা এই রাস্তাই নিলাম। সেক্ষেত্রে খুব হালকা হলেও একটা সম্ভাবনা আছে যে হয়তো কোনওভাবে বিস্ফোরণের শক্তি আবার জমা হয়ে সময়-বিচ্যুতি তৈরি করে আমাদের আবার সাত বছর পেছনে পৌঁছে দেবে। কিন্তু এটা একটা খুবই হালকা সম্ভাবনা। কোটিতে এক। কিংবা তারও কম। সেক্ষেত্রে আমাদের কি এই সম্ভাবনার অপেক্ষা করাটা ঠিক হবে? আমরা কি এখানে বসে থেকে দেখতে চাইব যে বাড়িটা আমাদের চারদিকে ভেঙে পড়ছে, এটা জেনেও যে— যে কোনও মুহূর্তে আমাদের শেষ সময় ঘনিয়ে আসতে পারে— অপেক্ষা করব একটু একটু করে সেই শেষ মুহূর্তের জন্য— বেসমেন্টের মেঝেতে শুয়ে থেকে কান পেতে সেই শেষ মুহূর্তের এগিয়ে আসার পায়ের আওয়াজ শোনার চেষ্টা করব—”
“তুমি কি সত্যিই ফিরে যেতে চাও?” মহিমা জিজ্ঞেস করে।
“অবশ্যই। তবে ফেরার ঝুঁকি কিন্তু মারাত্মক, মানে—”
“আমি তোমার কাছে ঝুঁকির পরিমাণ জানতে চাইনি। আমি জানতে চাইছি যে তুমি কি সত্যিই ফিরে যেতে চাও, না চাও-না? হয়তো তুমি এখানেই থেকে যেতে চাও। হয়তো অরিনের কথাটা গুরুত্বপূর্ণ। উর্দীপরা তুমি, মাথায় হেলমেট আর মুখে মুখোস নিয়ে, হাতে ওইরকম সূচের মতো বন্দুক নিয়ে, ওইরকম একটা সাপের মতো গাড়ি চালাতে চাইছ।”
“আর তুমি মাটির নীচের পাতাল শহরের কারখানায় কাজ করছ আর শ্রমিক শিবিরের আশ্রয়ে দিনযাপন করছ। বাচ্চারা সবাই সরকারি পুনর্বাসন কেন্দ্রে ওই দক্ষিণ ভারতের কোথাও ভবিষ্যতের সৈনিক কিংবা শ্রমিক হওয়ার শিক্ষানবিসী করছে! তোমার এগুলো কেমন হবে বলে মনে হচ্ছে? আমাদের তো যা হওয়ার হল। বাচ্চাদের ওখানে ওরা কী শেখাবে? তোমার কী মনে হয়? ওই শিক্ষায় ওরা বড় হয়ে কী হবে? আমার বিশ্বাস—”
“হয়তো ওদের ওখানে কোনও কাজের জিনিসই শেখাবে। যা ওদের ভবিষ্যতে কাজে লাগবে বেঁচে থাকার জন্য।”
“কাজের জিনিস? কাদের কাজের? ওদের জন্য? মানুষ জাতির জন্য? না যুদ্ধের কাজের জন্য?”
“ওরা বেঁচে থাকবে। অন্তত,” মহিমা বলে, “ওরা নিরাপদে থাকবে। আর যদি আমরা এই ঘরটায় বসে থাকি, অপেক্ষা করি আক্রমণ শুরু হওয়ার আর বিস্ফোরণের শক্তি জমা হওয়ার—”
“নিশ্চয়ই”, তীর্থঙ্কর রেগে ওঠে, দাঁতে দাঁত চেপে বলে, “বেঁচে ওরা থাকবে। সম্ভবত বেশ ভালোভাবেই। ভালো খাবার এবং পোষাক আর নিরাপত্তা। এগুলোও থাকবে।” ওর চোখ এখন ছেলেমেয়ের দিকে। মুখ চোখ কঠিন। নজর সরায় না তীর্থঙ্কর। বলে, “ওরা নিজেরা ভালোভাবেই বেঁচে থাকবে। ব্যাস, এই পর্যন্তই। ওরা বেঁচে থেকে বড় হয়ে উঠবে। প্রাপ্তবয়স্ক হবে একদিন। কিন্তু কেমন মানুষ হবে? তুমি তো শুনলে যে কমিশনার দোরজি কি বললেন! ২০৩২-শে বইপত্র পুড়িয়ে দিয়েছে। তো ওরা কী শিখবে? কীভাবে শিখবে? ওই ২০৩২-এর পর মানুষের জন্যে কি আদর্শ বেঁচে আছে? একটা সরকারি পূনর্বাসন কেন্দ্রের আবহাওয়ায় বড় হয়ে উঠে ওদের কি ধরনের মানসিকতা তৈরি হতে পারে বলে তোমার ধারণা? কী ধরনের মূল্যবোধ নিয়ে ওদের জীবন তৈরি হবে?ওরা সবাই কোনওভাবে কারখানার শ্রমিক বা বন্দুকধারী সৈনিক হয়েই জীবনযাপন করবে।”
“কেন? আইডিটিতে মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনিং এন্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টে কাজ করবে। তাহলে হবে তো?” মহিমা যুক্তি দেয়।
“ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনিং এন্ড টেকনোলজি। সবচেয়ে সেরাদের জন্য। যাদের আইকিউ বেশি— যাদের কল্পনাশক্তি প্রবল। সেই তারা। এরা সারাদিন ব্যস্ত থাকবে ল্যাপটপ নিয়ে বা সুপারকম্পিউটারের সামনে। যুদ্ধের পরিকল্পনা করবে নয় তো নতুন নতুন অস্ত্রের নকশা তৈরি করবে। যাই করুক তা করবে মানুষ মারার জন্য। একবার ভাবো জিনিয়া আর বিদিশা তাই করছে। ওরা নতুন নতুন অস্ত্রের নকশা বানাচ্ছে আর অরিন হয়তো রাপুতে কমিশনার বা জেনারেল। ওই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রের কী কী ভাবে ব্যবহার করা হবে তার পরিকল্পনা করছে। যদি কোনও সৈন্যদের মধ্যে দ্বিধা দেখা যায়— অস্ত্র চালাতে না চায় তো অরিন সেটা তদন্ত করে ওপরতলায় ওর প্রতিবেদন পাঠাবে যাতে ওই দলটাকে জেলে ভরা যায় বা বন্দুকের মুখে উড়িয়ে দেওয়া যায়। একটাই উদ্দেশ্য জীবনের— যুদ্ধটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এমন একটা পৃথিবীতে— যেখানে বুদ্ধিমানরা অস্ত্রের নকশা বানায় আর নির্বোধরা সেগুলো চালায়।”
মহিমা আবার বলে, “কিন্তু ওরা বেঁচে থাকবে।”
থমকে যায় তীর্থঙ্কর। মহিমাকে দেখে বোঝার চেষ্টা করে। কিছু বুঝতে পারে না। বলে, “বেঁচে থাকার অর্থ সমন্ধে তোমার চিন্তাভাবনা একটু অদ্ভুত মনে হচ্ছে আমার! তুমি ওটাকে বেঁচে থাকা বলে মনে করো? হয়তো সেটাই ঠিক!” তীর্থঙ্কর আবার একটু চুপ করে থেকে মাথা ঝাঁকিয়ে অদ্ভুতভাবে বলে, “হয়তো তুমিই ঠিক। সেক্ষেত্রে আমাদের কমিশনার দোরজির সঙ্গে মাটির তলার আশ্রয়ে চলে যাওয়াই উচিত। এই দুনিয়ায় টিকে থাকার জন্য। বেঁচে থাকার জন্য।”
মহিমা উঠে এসে তীর্থঙ্করের পাশে বসে। তীর্থঙ্করের কাঁধের কাছে আলতো করে হাত রেখে মৃদু স্বরে বলেন, “তীর্থ, আমি কখনওই সেটা বলিনি। আমি আসলে বুঝে নিতে চাইছিলাম যে ঠিক করে সমস্ত দিকগুলো তুমি ভেবেছ কি না। কেন আমাদের এই বাড়িতে থেকে যাওয়াটাই দরকার আর সেটা তোমার কাছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার কি না। যেখানে আমাদের পুরোনো সময়ে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। আবার এখানে থেকে যাওয়ার মানে হয়তো আজই আমাদের সবার শেষ দিন।”
তীর্থঙ্কর ভ্রু কুঁচকে মহিমাকে দেখে। “তো তুমি সম্ভাবনা কম হলেও সেই সুযোগটা নিতে চাও!”
“অবশ্যই। সুযোগ আমাদের নিতেই হবে। আমাদের বাচ্চাদের শুধু ঘৃণা, হত্যা আর ধ্বংসের কারিগর হয়ে ওঠার জন্য সরকারি পূনর্বাসন কেন্দ্রে আমরা পাঠাতে পারি না,” বলে হেসে ফেলে মহিমা। তারপর বলে, “যদিও ওরা যে রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে যেত সেটা এখন এখানে, এই ২০৩৯-এর পৃথিবীতে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটা খোলা মাঠ মাত্র।”
মা-বাবার কথাবার্তার সুরে বাচ্চারা এতক্ষণ একটু শিটিয়ে ছিল। তাদের ভবিষ্যৎ নিয়েই যে তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে তা না বোঝার মতো ছোটও আর ওরা নয়। অন্তত জিনিয়া আর বিদিশা তো নয়ই। এবার এতক্ষণ পরে মাকে হেসে উঠতে দেখে ওদের চেপে রাখা নিশ্বাস ঝেড়ে ফেলে শান্তি পায়। জিনিয়া এতক্ষণ বাবার জামার হাতাটা টেনে ধরে বসেছিল। এবার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, “আমরা কি ফিরে যাচ্ছি বাবা? আজকেই?”
তীর্থঙ্কর জিনিয়ার হাতটা জামার থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের হাতে নেয়। বলে “যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সোনা।”
সিদ্ধান্তটা নিয়ে নেওয়াতে এবার অনিশ্চয়তা দূর হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে এখন এতক্ষণে একটু শান্তির বাতাস বইছে। সকালে ওই বাচ্চারা স্কুলে বেরোতে যাওয়ার মুহূর্তের পর থেকে যা এই প্রথম।
মহিমা উঠে পড়ে। রান্নাঘরের দেওয়ালে বসানো কাবোর্ডের পাল্লা খুলে খুবই অবাক হয়ে যায়। “আরে, সবই তো রয়েছে। ওরা তাহলে কি নিয়ে গেল?”
“ফ্রোজেন মটরশুটির প্যাকেটের গোটা বাক্সটা আর রেফ্রিজারেটরে যা কিছু ছিল নিয়ে গিয়েছে। আর শুধু ভেঙেছে সামনের দরজাটা।”
অরিন দৌড়ে এসে ব্যাপারটা দেখে উত্তেজনায় বলে ওঠে, “ইয়া! আমরা ওদের হারিয়ে দিয়েছি। হিপ হিপ হুররে!” বলেই আবার দৌড়ে চলে যায় জানলার কাছে। জানলার পর্দা সরিয়ে উঁকি মারে বাইরে। কিন্তু বাইরের ছড়িয়ে থাকা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আর কিছু দেখতে না পেয়ে চুপ করে যায়। যতদূর চোখ যায় মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে পড়ে আছে ভেঙে পড়া শহরের ধ্বংসস্তূপ। চোখের সামনে শুধুই উড়ে বেড়ানো ধূলো আর ছাই। মিইয়ে যায় অরিন। খানিক চুপ করে থেকে বলে, “আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।” বাবাকে জিজ্ঞেস করে, “বাবা, এখানটা কি সবসময়ই এরকম ছিল?”
তীর্থঙ্কর উত্তর দেন, “হ্যাঁ।”
মুখ শুকিয়ে যায় অরিনের। বলে, “শুধুই ধূলো আর ছাইয়ের কুয়াশা? সূর্য কি আর কখনও উঠবে না, বাবা?”
অরিনের এ প্রশ্নের উত্তর দিতে একটু ইতস্তত করে তীর্থঙ্কর। তাকে বাঁচিয়ে দেয় মহিমা। মহিমা রান্নাঘরের থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করে, “একটু চা বানাবো না কি?”
“হ্যাঁ। বানাও”, বলে তীর্থঙ্কর বাথরুমে ঢোকে। আয়নায় নিজেকে দেখে। মুখের এখানে ওখানে বেশ কয়েকটা কাটা দাগ। রক্ত শুকিয়ে গিয়ে লেগে আছে এখনও। ওর মাথা ঘুরতে শুরু করে। পেটের ভেতর থেকে একটা ব্যথা উঠে আসে। সকাল থেকে যে উত্তেজনা, ভয় শরীরে ঘিরে ছিল সেটা এখন খানিক থিতিয়ে যাওয়ার ফলে এতক্ষণ চাপা পড়ে থাকা ব্যথা বেদনা যেন এবার চাগিয়ে উঠতে চাইছে। নিজেকে জোর করে শান্ত করে তীর্থঙ্কর। এখন অনেক কাজ বাকি। সময়ের এই চক্র থেকে ওকে ওর পরিবারকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা শেষ চেষ্টা করতেই হবে। বেসিনের নল খুলে তীর্থঙ্কর মুখ চোখ পরিষ্কার করতে শুরু করে।
রান্নাঘরের দরজার পাশে একটা ছোট টেবিলে ওরা সবাই চা খেতে বসে এবার। এই টেবিলটা ওরা সাধারণত তাড়াহুড়োয় কিছু খেয়ে নেওয়ার দরকারে ব্যবহার করে। আজ এ বাড়িতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়ার ফলে ওদের এই মুহূর্তে কোনও তাড়া নেই। তবুও ওরা ওখনেই বসে পড়ে।
চা খেতে খেতে জিনিয়া বারবার জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়। অরিন পর্দাটা আর টেনে দেয়নি বলে ওই জানলাটা দিয়ে বাইরের অনেকটা নজরে আসছে। জিনিয়া বলে ওঠে, “ওই লোকটা কি আবার আসবে মা? কেমন না লোকটা? ছোটখাটো আর যেন একটু বোকা বোকা! কেমন আমাদের বইগুলো নিয়ে চলে গেল! উনি কি আবার ঘুরে আসবেন? হ্যাঁ?”
তীর্থঙ্কর বা মহিমা কেউই জিনিয়ার প্রশ্নের উত্তর দেয় না। বিদিশা আর আর অরিন এখন নিঃশব্দে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে।
তীর্থঙ্কর হাতের ঘড়িটার দিকে তাকায়। দশটা বেজে বন্ধ হয়ে রয়ে গিয়েছে। মোবাইলটা জেগে রয়েছে, কিন্তু কোনও নেটওয়ার্ক নেই। মোবাইলে সময়টা দেখে নিয়ে ঘড়িটার কাটা ঘুরিয়ে চারটে পনেরো করে তীর্থঙ্কর। বলে, “কমিশনার দোরজি তো বললেন যে সন্ধে হতেই আক্রমণ শুরু হবে। তার মানে খুব বেশি আর সময় আমাদের হাতে নেই।”
(১০)
চা-পর্ব তখন শেষ পর্যায়ে। পট থেকে বাকি চা-টা তীর্থ আর নিজের কাপে ঢেলে নিয়ে পটটা খালি করে পাশে সরিয়ে রাখে মহিমা।
চুমুক দিয়ে তীর্থঙ্করের দিকে তাকিয়ে বলে, “তো আমরা সত্যিই এই বাড়িতে থেকে ভাগ্য পরীক্ষা করছি। তাই তো?”
“ঠিক তাই।”
“ফেরত যাওয়ার সম্ভাবনা যদিও খুবই কম। তবুও?”
“যদিও ফেরত যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তবুও। তুমি খুশি তো মহিমা?”
“আমি যথেষ্ট খুশি”, মহিমা চা শেষ করে কাপটা নামিয়ে রেখে বলে, “এটাই আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত তীর্থ। তুমিও ভালোই জানো। যত কম সুযোগই থাকুক সেটুকুই আমাদের নেওয়া উচিত। ফিরে যাওয়ার জন্য। ফিরে গিয়ে কিছু করার জন্য। যাতে সাত বছর পর আমাদের কারোরই এমন অবস্থায় পৌঁছোতে না হয়। সাত বছর পরেও যাতে আমাদের পরিবার একসঙ্গে থাকতে পারে। আমাদের সবার পরিবার… আমরা আলাদা হতে চাই না। আমরা কেউ চাই না।”
তীর্থঙ্কর চা শেষ করে কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে পর্দা সরানো জানলাটা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দিনের আলোর ফুরিয়ে আসা দেখছিল। ওদিকে তাকিয়ে থেকেই অনির্দিষ্ট ভঙ্গিতে বলে ওঠে, “আলো কমে আসছে। আমাদের গুছিয়ে নিতে হবে। আর ঘণ্টাদুয়েকের মতো সময় পাওয়া যাবে। তার মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে এমনকি আমরা এই গোধূলির আনন্দও খানিকটা উপভোগ করতে পারি।”
ধীরে ধীরে দিনের আলো বাইরে ফুরিয়ে আসে। গোধূলির স্বর্ণাভা ছড়িয়ে পড়ে দিগন্তে। তারপর ক্রমশ নিভে যায় দিবাকর। কালচে ধূসর অন্ধকার ঘনিয়ে আসে চারিদিকে। বাড়িটার মধ্যে।
তীর্থঙ্করদের প্রস্তুতি পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল।
ঠিক সাড়ে ছ-টার সময় প্রথম রম-টা বিস্ফোরিত হল। ধাক্কাটা বাড়ির মধ্যেও এসে পৌঁছোল, একটা তরঙ্গ প্রবাহের মতো এসে বিস্ফোরণের ঘাতটা বাড়িটাকে যেন জড়িয়ে ধরল।
ডাইনিং রুমের থেকে জিনিয়া দৌড়ে এল, মুখটা ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। “বাবা! এটা কী হচ্ছে?”
“কিছু না, জিনি মা। তুমি ভয় পেয়ো না। কিছু হবে না।”
ডাইনিং থেকে বিদিশার অধৈর্য আওয়াজ আসে, “চলে আয় জিনিয়া। তোর দান এবার।” ওরা ডাইনিং-এ লুডো খেলতে বসেছে।
অরিন লাফিয়ে উঠে পড়ল। “আমি দেখে আসি কী হচ্ছে।” উত্তেজনায় দৌড়ে যায় জানলার দিকে, পর্দার ফাঁক দিয়ে তাকায় অন্ধকারে ঢেকে যাওয়া বাইরেটায়, “আমি… আমি দেখতে পাচ্ছি কোথায় পড়েছে ওটা!”
তীর্থঙ্কর উঠে গিয়ে অরিনের পাশে দাঁড়িয়ে পর্দাটা পুরো সরিয়ে দেয়। বহুদূরে, প্রায় দিগন্তের কাছে একটা সাদা উজ্জ্বল আলোর আগুন যেন ঝলকে উঠে জ্বলছে। ধোঁয়ার একটা লম্বা পাকানো স্তম্ভ ওই আলোর আগুন থেকে বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে উঠে যাচ্ছে ওপরে। অরিনকে টেনে নিয়ে পর্দাটা পুরো টেনে দিলেন তীর্থঙ্কর। তারপর টেবিলে বসে থাকা বিদিশা আর মহিমার দিকে তাকিয়ে বলে, “এক কাজ করি। চলো, আমরা নীচে চলে যাই।“
“কোথায়?”
“নিচে। বেসমেন্টে। চলো চলো। আর দেরি করা ঠিক হবে না।“
সবাই উঠে পড়ে। তীর্থঙ্কর বেসমেন্টে নামার সিঁড়ি ঘরের দরজার তালাটা চাবি দিয়ে খোলে। বাড়িটা যিনি বানিয়েছিলেন তিনি ছিলেন একজন জিওলজিস্ট। ওএনজিসিতে চাকরি করতেন। রিটায়ারমেন্টের পর পছন্দের এই পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে থাকার জন্যে এই বাড়িটা বানানোর সময় ভূমিকম্প-প্রবণ এলাকা বলে নিচে একটা বেসমেন্টও বানিয়ে ছিলেন। দু-হাজার কুড়িতে বদলি হয়ে এসে থাকার জন্য বাড়ি খুঁজতে গিয়ে এটা সস্তায় পেয়ে যায় তীর্থঙ্কর। ভূতত্ববিদ ভদ্রলোক তখন মারা গেছেন। গ্রীন কার্ড পেয়ে যাওয়া একমাত্র ছেলে সবকিছু বেচে দিয়ে মাকে নিয়ে ইউএসএ-তে চলে যায়। আজ সেই বেসমেন্টটাই তীর্থঙ্করের কাজে লাগবে।
মহিমা দাঁড়িয়ে পড়ে। “আরে, খাবারগুলো! ওগুলো নিয়ে নিই চলো।”
“ঠিক বলেছো। বিদিশা, তুমি বোন আর ভাইকে নিয়ে নিচে যাও। আমরা খাবারগুলো নিয়ে আসছি।”
অরিন দাঁড়িয়ে পড়ে। “আমিও কিছু নিয়ে নিতে পারি।”
ইতিমধ্যে চার নম্বর বিস্ফোরণের আওয়াজ আর তার সঙ্গের তরঙ্গাঘাতে বাড়িটা আবার কেঁপে ওঠে। মনে হল রমগুলো ওরা ক্রমাগত আরও কাছে ফেলা শুরু করেছে। তীর্থঙ্কর জোর করে অরিনকে সিঁড়ির দিকে ঠেলে দিয়ে বলে, “উঁহু, নিচে যাও আর দিদিদের সঙ্গে থাকবে। এদিক ওদিক লাফ-ঝাঁপ করবে না একদম। আর বেসমেন্টটার ভেন্টিলেটরে একদম উঁকি মারতে যাবে না। ঠিক আছে?”
অরিন অনিচ্ছুকভাবে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়েও আবার বলে, “আমি আমার ওই ট্রেনটা আর ওই প্লাই-উডের টুকরোটা নিয়ে নিই বাবা? প্লাইউডটা দিয়ে বেসমেন্টের ভেন্টিলেটরটা ঢাকা দেওয়া যাবে!”
“আচ্ছা, বাবা। নিয়ে নাও আর নিচে যাও” মহিমা বলে ওঠে।
পঞ্চম বিস্ফোরণের আওয়াজ আর তরঙ্গাঘাত এসে আঘাত করে। এটা মনে হল আরও কাছে কোথাও পড়ল।
দ্রুতগতিতে অরিন ওর খেলনা ট্রেন আর প্লাইউডের টুকরোটা নিয়ে নিচে চলে যায়। ভয় ক্রমশ জড়িয়ে ধরছে সবাইকে। মহিমা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে। “খাবার দাবার, জল আর কিছু প্লেট নিলাম। এগুলো ধরো। আর কিছু?”
“বই।” মহিমার স্নায়ুচাপ বেড়ে গেছে এতক্ষণে। এদিক ওদিক তাকিয়ে আবার দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে। আরও কিছু খাবার নিয়ে আসার ইচ্ছে।
তীর্থঙ্কর কিছু বলে না। বাঁ হাতে টেবিলের ওপর থেকে কমিশনার দোরজির নামিয়ে রাখা বইগুলোর মধ্যে থেকে কয়েকটা বই তুলে নিয়ে স্ত্রীর পেছনে পেছনে যখন রান্নাঘরে ও ঢুকছে দেখা গেল ওর হাতে ধরা সবচেয়ে ওপরের বইটায় দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোকের ছবি দেখা যাচ্ছে।
তখনও ওরা দুজন রান্নাঘরেই, ভয়ংকর শব্দের সঙ্গে গোটা বাড়িটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠল। রান্নাঘরের জানলার কাচগুলো ঝরঝর করে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল ওদের ওপরে। ওপরের তাকে থাকা প্লেট-ডিশগুলো সেই কম্পনের চোটে নিচে পড়ে আওয়াজ করে ভেঙে পড়ল। সিঙ্কে থাকা কাল রাতের ব্যবহৃত বাসনগুলোও ভেঙে চুরচুর হয়ে গেল। তীর্থঙ্কর হাতের সমস্ত কিছু কিচেন টেবিলে নামিয়ে দিয়ে মহিমার হাত ধরে টান দিয়ে নীচু হয়ে কিচেন-টেবিলের নিচেটায় আড়াল নিল।
ভেঙে পড়া জানলার মধ্যে দিয়ে কালচে ধূসর ধোঁয়ার স্রোত রান্নাঘরের ভেতরে ঢুকে পড়লো। সন্ধের হাওয়াতে এক তীব্র কষাটে পচা গন্ধ ঘরটায় ছড়িয়ে গিয়েছে। চোখমুখ জ্বালা করে ওঠে। তীর্থঙ্কর কেঁপে ওঠে।
মহিমাকে বলে, “থাক খাবারদাবার। চলো নিচে যাই।”
“কিন্তু—”
“ছাড়ো তো!” একটানে মহিমাকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়োয় বেসমেন্টের সিঁড়ির দিকে। দরজার কাছে পৌঁছোতে না পৌঁছোতেই দেওয়ালের একটা চাঙড় ওদের সামনে ভেঙে পড়ল। সিঁড়িতে হোঁচট খেতে খেতে মহিমাকে ভেতরে ঠেলে দিয়ে কোনওরকমে নিজেও ঢুকে তীর্থঙ্কর সবেমাত্র ভেতর থেকে বেসমেন্টের দরজা বন্ধ করছে, আরেকটা বিস্ফোরণ হল। সম্ভবত এটা বাড়িটা থেকে একটু দূরে।
বিদিশা এসে মাকে তুলে ধরে। জিজ্ঞেস করে, “ও মা, খাবারগুলো কোথায়?”
তীর্থঙ্কর হাত দিয়ে মুখ মাথা থেকে ধূলোবালি পরিষ্কার করছিলো। বলল, “ও আনা গেল না, মা। ছেড়ে দাও। দেখো, ও সবের কোনও দরকার পড়বেই না।”
অরিন ভেন্টিলেটরে ফোকরে প্লাইউডের টুকরোটা লাগাচ্ছিল। কিছুতেই পারছিল না। হাঁফাতে হাঁফাতে ওখান থেকে বলল, “ও বাবা, একটু ধরো না এদিকে।”
তীর্থঙ্কর উঠে গিয়ে প্লাইউডের টুকরোটা ঠেলে ভেন্টিলেটরে ফোকরে গুঁজে দিল। অরিন নেমে মায়ের পাশে গিয়ে বসে পড়েছিল। বেসমেন্টটা বেশ ঠান্ডা আর নিস্তব্ধ হলেও সিমেন্টের মেঝেটা বহুদিনের অব্যবহারে খরখরে আর স্যাঁতসেঁতে।
এবারের রমটা এসে পড়ল বাড়িটার দক্ষিণ দিকের ঘরের উপর। মনে হল এবার একসঙ্গে দুটো রম পড়েছে। তীর্থঙ্কর ঝাঁপিয়ে পড়ে সবাইকে টেনে নিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ল। তাড়াহুড়োয় কংক্রিটের মেঝেতে ওর মাথাটা ঠুকে গেল। উঁহু করে একবার কাতরেও উঠল ও। এক মুহূর্তের জন্য যেন চোখে অন্ধকার নেমে এল। খানিক পরে বিস্ফোরণের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই আবার উঠে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসে জিজ্ঞেস করল, “সবাই ঠিক আছো তো?”
“আমি ঠিক আছি। অরিন, অরিন কোথায়? মহিমা জানতে চাইল। জিনিয়া ফোঁপাচ্ছিল। অরিন দেখা গেল উলটোদিকের দেওয়ালের ওখান থেকে হামাগুড়ি দিয়ে মায়ের কাছে আসছে। কখন ওদিকে চলে গেছিল কেউ মনে করতে পারল না। বিদিশা উঠে বসে বলল, “মনে হয় আমি ঠিকই আছি।”
হঠাৎ আলোটা দপদপ করে উঠেই আস্তে আস্তে নিভে গিয়ে পুরো ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেল। কালো পিচের মতো অন্ধকারে ঢাকা পড়ল বেসমেন্টটা।
তীর্থঙ্কর বললেন, “যাঃ, গেল ইনভার্টারটা!”
অরিন বলল, “আমার কাছে একটা টর্চ আছে,” পকেট থেকে একটা ছোট্ট টর্চ বার করে জ্বালায় অরিন। “কেমন এটা?”
তীর্থঙ্কর অরিনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে “খুব ভালো। সোনা ছেলে।”
আরও রম পড়ল। আরও। এবার একের পর এক। কোনওটা কাছেই কোথাও, আবার কোনওটা মনে হল একটু দূরে কোথাও। ওদের নীচের মেঝে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকল। দেওয়াল থরথর করে কাঁপছে। বিস্ফোরণের তরঙ্গাঘাত গোটা বাড়িটাকে যেন রোলার-কোস্টারে উঠিয়ে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে।
মহিমা বলে, “মনে হয় আমাদের শুয়ে পড়াই উচিত।”
“হ্যাঁ, সবাই শুয়ে পড় আর মাথাটা হাত দিয়ে ঢেকে নাও। এইভাবে…” বলে তীর্থঙ্কর মেঝেতে টানটান ভাবে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে হাত দুটো তুলে কনুই আর হাতের তালু দিয়ে মাথাটা ঢেকে নেয়। ওরা পাঁচ জন এখন পাশাপাশি শুয়ে আছে। দু-পাশে মহিমা আর তীর্থঙ্কর। ওদের দুজনের মধ্যে তিনটি বাচ্চা। ঘেষাঘষি করে, একসঙ্গে। প্রত্যেকে যেন প্রত্যেককে ছুঁয়ে রয়েছে। ঝরঝর করে দেওয়াল আর ছাদের সিলিং থেকে প্লাস্টারের টুকরো ঝরে পড়ছে ওদের চারপাশে। ওদের ওপরে।
অরিন ফিসফিস করে তীর্থঙ্করকে বলে, “কখন থামবে এটা?”
“এক্ষুনি” তীর্থঙ্কর জবাব দেয়।
“তখন আমরা ফিরে যাব?”
“হ্যাঁ। আমরা ফিরে যাব।”
পরের বিস্ফোরণটা সরাসরি ওদের ওপরে হল। এক সঙ্গে অনেকগুলো রম একই সময়ে বিস্ফোরিত হল ওদের বাড়িটাকে ঘিরে। তীর্থঙ্কর যেন টের পায় ওর শরীরের নীচে কংক্রিটের মেঝেটা ওকে নিয়ে উঠে পড়েছে। উঁচু হয়ে উঠছে। ফুলে উঠে বেড়ে যাচ্ছে বেলুনের মতো। ও আরও উপরে উঠে যাচ্ছে। ক্রমশ। ও চোখ বন্ধ করে রাখে। নিজেকে আরও চেপে নেয় মেঝের সঙ্গে। টের পায় তারপরও ও যেন ক্রমশ উঠে যাচ্ছে— ওপরে— আরও ওপরে। কংক্রিটের মেঝেটা যেন বেলুনের মতো ফুলেই চলেছে। ওর আশপাশের কংক্রিটের বীম আর কলামগুলো একের পর এক ফেটে যাচ্ছে। ভেঙে পড়ছে। দেওয়ালের প্লাস্টার আর সিমেন্টের চাঙড় বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ছে ওদের চারদিকে। ওদের শরীরের উপর। একবার যেন শুনতে পেল কোথাও কাচ ভেঙে পড়ার আওয়াজ। তারপর লেলিহান আগুনে সব কিছু পুড়ে যাওয়ার চড়বড় শব্দ ভেসে আসতে লাগল দূর থেকে।
“তীর্থ… ” মহিমার গলার আওয়াজ কানে আসে। আওয়াজটা চাপা। যেন লেপের তলা থেকে কথা বলছে।
তীর্থঙ্কর সাড়া দেয়। “হ্যাঁ, বল।”
“মনে হচ্ছে না যে আমরা— আমরা ফিরতে পারব।”
“আমি জানি না। সত্যিই জানি না।”
“হবে না গো। আমার মনে হচ্ছে আমরা ফিরে যেতে।”
“তাই-ই হয়তো। ফেরা আর হবে না আমাদের।”
ব্যথায় কাতরে ওঠে তীর্থঙ্কর। একটা বড় মতো চাঙড় সম্ভবত পিঠের ওপর এসে পড়ে। ক্রমশ আরও ভাঙা টুকরোটুকরা চাঙড় আর ইট-প্লাস্টারের বোঝা জমা হতে থাকে ওদের শরীরের উপড়ে। শিলাবৃষ্টির মতো ঢেকে দিচ্ছে ওদের। প্রশ্বাসের সঙ্গে বাতাসে ভেসে আসে কাঠ আর প্লাস্টিকের পোড়া গন্ধ। বেসমেন্টের ভেন্টিলেটরের প্লাইউডটা কোথায় ছিটকে গিয়েছে। এখন ওখান দিয়ে বিস্ফোরণে ফলে জ্বলে যাওয়া জিনিসপত্রের গন্ধ আর পোড়া ছাই উড়ে ঢুকে পড়েছে বেসমেন্টের ভিতরে।
“বাবা” সেই পোড়া গন্ধ আর ছাই ভরতি বাতাসে শ্বাস নিতে নিতে তীর্থঙ্কর হালকা ভেসে আসা জিনিয়ার গলার আওয়াজ শুনতে পায়। ও সাড়া দেয়।
“কী?”
“আমরা তো ফিরে যাচ্ছি, তাই না, বাবা?”
উত্তর দেওয়ার জন্য তীর্থঙ্কর সবে মুখ খুলতে যাচ্ছিল। একটা ভীষণ ভয়ংকর বিস্ফোরণের শব্দে চাপা পড়ে গেল সেই চেষ্টা। বিস্ফোরণের অভিঘাতে তীর্থঙ্করের মনে হল ও যেন ছিটকে গেল। শরীরটা যেন ভর শূন্য। পালকের মতো ভাসছে ও। চারপাশের সবকিছু যেন তীব্রগতিতে ঘুরপাক খেতে থাকল। ঝড়ের মতো ভেসে আসল এক গরম হাওয়ার স্রোত। যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল তীর্থঙ্করদের। যেন জ্বালিয়ে দিল শরীর। তীর্থঙ্কর চীৎকার করে ওঠে। মুখ হাত যেন জ্বলে যাচ্ছে। কোনওরকমে বলতে যায়, “মহিমা—”
তারপর চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে যায়। শুধুই অন্ধকার আর নিস্তবদ্ধতা।
(১১)
প্রথমে ভেসে আসে গাড়ির আওয়াজ।
কাছাকাছি কোথাও কয়েকটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। তারপর এল লোকজনের গলার আওয়াজ। এবার পায়ের শব্দ ভেসে আসছে। তীর্থঙ্কর পাশ ফিরতে চায়। পারে না। শরীরের উপর ইট-সিমেন্টের চাঙড়। একটা বড় কাঠের টুকরো। দু-হাত দিয়ে সব ঠেলে উঠে দাঁড়ায় তীর্থঙ্কর।
“মহিমা।” চারদিকে তাকিয়ে তীর্থঙ্কর খোঁজে সবাইকে। “দ্যাখো, আমরা ফিরে এসেছি।”
বেসমেন্টটা প্রায় পুরোটাই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। দেওয়ালগুলো ভেঙে পড়েছে। যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে সেখানে দেওয়ালের অংশ বেঁকে গিয়ে ঝুলছে। একদিকের ধ্বসে গিয়ে তৈরি হওয়া একটা বড় ফোকর দিয়ে ওপাশের ঘাসের সবুজ রং চোখে পড়ে। তার ওপাশেই একটা কংক্রিটের তৈরি পথ। একটা ছোট গোলাপ বাগান। তারপর পাশের বাড়ির সামনের সাদা দেওয়ালটা।
দূরে সারিবদ্ধ টেলিফোনের তারের খাম্বা। দূরের ঘর-বাড়ি। শহরটা। ওদের সুকনা। আরও দূরে জঙ্গল আর পাহাড়ের আভাস।
আনন্দে ঢীৎকার করে ওঠে তীর্থঙ্কর। “আমরা ফিরে আসতে পেরেছি।”
এতক্ষণে যেন হৃদয়ঙ্গম করে সম্পূর্ণ বাস্তবতা। সত্যিই ফিরে আসতে পেরেছে ওরা। এবং নিরাপদে। সাত বছরের ওপার থেকে। আবার সব ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু মহিমা কোথায়? অরিন? জিনিয়া? আর বিদিশা?
পাগলের মতো পড়ে থাকা ধ্বংসস্তূপ হাতড়ে সরাতে থাকে তীর্থঙ্কর। “মহিমা। কোথায় তোমরা? সবাই ঠিক আছো তো?”
“এই যে…” মহিমা ইট-পাথর সরিয়ে উঠে বসে। শরীর আর মাথা থেকে ঝরে পরে যত রাজ্যের নোংরা টুকরো টুকরো ইট সিমেন্টের অংশ। পুরো সাদা হয়ে গিয়েছে মহিমা সিমেন্টের ধুলোয়। মাথার চুল. মুখ চোখ, পোষাক— সব সাদা। মুখের বিভিন্ন জায়গায় কেটে গেছে দেখা যাচ্ছে। সমস্ত শরীর কেটেকুটে একসা। পোষাকের অবস্থাও ছিঁড়ে গিয়ে খুবই খারাপ। তীর্থঙ্করকে দেখে জিজ্ঞেস করে, “সত্যিই আমরা ফিরে এলাম?”
তীর্থঙ্কর উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই বাইরে থেকে কেউ আওয়াজ দেয়, “তীর্থঙ্করবাবু! আপনারা ঠিক আছেন তো?”
খাকি উর্দীপরা একজন পুলিশ পড়ে থাকা ইট-সিমেন্টের স্তূপ ডিঙিয়ে প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে এল বেসমেন্টে। পেছনে পেছনে আরও দুজন সাদা পোষাকের পুলিশ। বাইরে ততক্ষণে জড়ো হয়ে গিয়েছে প্রতিবেশীদের একটা দল। সবাই উঁকি মেরে দেখতে চাইছে।
“আমি ঠিক আছি,” তীর্থঙ্কর পুলিশদের বলল। জিনিয়া আর বিদিশা উঠে বসেছিল। তীর্থঙ্কর ওদের উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করতে করতে বলে, “মনে হয় আমরা সবাই ঠিক আছি।” জিনিয়া আর বিদিশার অবস্থাও একই রকম। ধুলোয় সাদা গোটা শরীর। এখানে ওখানে কেটে গেছে। মনে হচ্ছে বিদিশার ডান পা মচকেছে কিংবা ভেঙেছে। ওদিকে ততক্ষণে মহিমা অরিনকে উঠিয়ে বসিয়েছে। অরিনের অবস্থা তুলনামূলকভাবে একটূ ভালো মনে হল। ভেন্টিলেটরে লাগানো সেই প্লাইউডের টুকরোটা এসে প্রথমেই ওর শরীরের ওপর পড়ায় পরের দিকের ইট-কাঠ-সিমেন্টের টুকরো ওকে তেমন আঘাত করতে পারেনি। তবে থতমত হয়ে কেমন করে যেন তাকিয়ে রয়েছে। মহিমা ওকে কোলের কাছে টেনে নিলো।
“কী হয়েছিল?” খাকি পোষাকের পুলিশ সামনে থেকে একটা বড় চাঙড় সরিয়ে তীর্থঙ্করের দিকে এগিয়ে এল। “বোমা? কোনও বোমা-টোমা ফাটেনি তো?”
“বাড়িটা পুরো ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছে,” সাদা পোষাকের একজন বলে ওঠে। “আপনারা নিশ্চিত তো যে আপনাদের কোনও চোট লাগেনি?”
“আমরা নিচে ছিলাম। এই বেসমেন্টে।”
“তোমরা ঠিক আছো তো, মহিমা?” হাসিনা কাকী এর মধ্যেই নিচে নেমে এসেছেন। পেছনের গলিতে তিন নম্বর বাড়িতে থাকেন। ছেলের বিয়ে দেওয়ার পর থেকে সকাল-সন্ধ্যা পাড়ার দেখভাল করাটা উনি ওঁর জীবনের ব্রত করে নিয়েছেন। অন্যদিন হলে মহিমা বিরক্ত হত। আজ কিন্তু হাসিনা কাকীকে দেখে মনটা ভরে গেল। “হ্যাঁ, হাসিনা কাকী। তোমাদের আশীর্বাদে সবাই ঠিক আছি।”
শুধু হাসিনা কাকী কেন? ঠিক তার পেছনেই উঁকি মারলেন প্রাণকৃষ্ণদা। ওঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে চীৎকার করতে করতে নেমে এলেন এবং কোনওরকমে একটা হোঁচট খেয়ে সামলে নিয়েই শুরু করলেন, “রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ। কি অবস্থা! কী করে হল ভাই এমন?”
সাদা পোশাকের পুলিশ দুজন চারদিকে নজর ঘুরিয়ে এপাশ ওপাশ তদন্ত করছিলো। জমে থাকা ধ্বসে পড়া স্তূপগুলো পা দিয়ে নেড়েচেড়ে এই ভয়ানক ঘটনার কারণ খুঁজে বার কতে চাইছিল। একজন বলল, “আপনাদের ভাগ্য খুবই ভালো। ভাগ্যিস নিচে ছিলেন। ওপরের অংশটা পুরো ধ্বসে পড়েছে। কিন্তু আপনারা নিচেই বা ছিলেন কেন?”
প্রাণকৃষ্ণদা প্রায় ঝাঁপিয়ে তীর্থঙ্করের পাশে এসে দাঁড়ালেন। বাস্তবিক এবং আক্ষরিক— দুই অর্থেই। তীর্থঙ্কর সাদা পোশাকের পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলার আগেই উনি বলে উঠলেন, “রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ। দুচ্ছাই, আমি তোমাকে কতদিন থেকে বলছি বলো তো যে ছাদের ওই গরম জলের বয়লারটা সারাও, সারাও। তো গরীবের কথা কি তোমরা শুনবে! এখন হল তো? নাও এবার পুরো বাড়িটা সারাও। রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ।”
“কী?” তীর্থঙ্কর বিড়বিড় করে।
এটাও সেই রিটায়ার্ড ভূতত্ত্ববিদের আরেক খেয়ালের ফসল। ওঁর গবেষণার আর শীতের গরম জলের জন্য বাড়ির ছাদে একটা ছোট বয়লার-ও বসিয়ে ছিলেন। যেটার ইদানিং আর তেমন ব্যবহার ছিল না। বিশেষ করে বাথরুমে গিজার বসিয়ে নেওয়ার পর থেকে ওটা এমনই পড়ে ছিল।
প্রাণকৃষ্ণদা তখনও চুপ করেননি। “আরে তীর্থ, তুমি ভুলে গেলে? তোমাদের ছাদের বয়লারটা গো! রাধে কৃষ্ণ। আমি তো তোমাকে বলেছিলাম ক-দিন আগেই। ওটার ধার দিয়ে আমি ধোঁয়া বেরোতে দেখেছি। দ্যাখো, গরম হতে হতে ওটা ফেটে গিয়ে এই কাণ্ড হল কি না…”, বলতে বলতে তীর্থঙ্করের মুখ দেখে কি আন্দাজ করলেন উনিই জানেন আর জানেন ওঁর ইষ্টদেবতা, একটু চুপ করে গিয়ে আবার বললেন, “সে ঠিক আছে। তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো তীর্থ। আমি ইনসিওরেন্স কোম্পানিকে এসব কথা বলব না। রাধে কৃষ্ণ।”
তীর্থঙ্কর পুলিশের প্রশ্নের জবাবে কি বলতে যাচ্ছিল কে জানে। এখন মুখ খুলে বন্ধ করে নিলো। কিই বা ও বলতে পারে? না, ও ভালো করেই জানে এই ধ্বংসের কারণ কোনও খারাপ হয়ে যাওয়া বয়লারের বিস্ফোরণে নয়। যেটা ও সারাতে গড়িমসী করেছে। না, এটা কোনও গ্যাস সিলিন্ডারের বিস্ফোরণে-ও নয়। যেটা ও প্রথমে বলতে চেয়েছিল। এটা ও ধরনের কোনও ব্যাপারই নয়।
তাই চুপ করে গেল তীর্থঙ্কর। নির্বাক তীর্থঙ্কর তাকিয়ে রইল। ওর দৃষ্টি সামনের পুলিশ প্রতিবেশীদের ছাড়িয়ে যেন দূরে কোথাও হারিয়ে গেছে। গভীর ভাবনায় ডুবে গেলো ও।
সামনেই এগিয়ে আসছে একটা যুদ্ধ। একটা সর্বাত্মক যুদ্ধ। আর এটা আমার একার কোনও ব্যাপারই নয়। শুধু আমার পরিবারের ব্যাপারও নয়। শুধু আমাদের বাড়ির ব্যাপারও নয়।
এটা আপনাদেরও ব্যাপার। আমার, আপনার আর প্রত্যেকের ব্যাপার। এখানে, এই রাস্তার, তার পরের রাস্তার, তারপরের শহর বা গ্রাম, তার পাশের জেলা, গোটা দেশ আর গোটা উপমহাদেশ। গোটা পৃথিবী, এই রকম, আমাদের বাড়িটার মতো, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে চলেছে। সেদিন ধোঁয়াশায় ভরে যাবে চারদিক। মরচে পড়া ধ্বংসস্তূপের লোহার পাশ দিয়ে শুধু বেঁচে থাকবে কিছু আগাছা। আমাদের সবার জন্য সেই যুদ্ধ এই একই পরিণতি তৈরি করবে, ধ্বংসস্তূপের বেসমেন্টে আমরা কেউ কেউ দাঁড়িয়ে থাকব ধূলোময়, সাদাটে, ভয়ার্ত। বাকিরা নেই হয়ে যাবে হয়তো।
আর যখন ওই অবস্থার মুখোমুখি আমরা হব, হয়তো আজ থেকে পাঁচ বা সাত বছর পরে, তখন আর ফেরার পথ থাকবে না আমাদের। কোনও ফিরে আসা নয়, কোনও পেছনে আসা নয়, শুধুমাত্র তখন থাকবে এগিয়ে যাওয়া। আর তখন এটা সকলের জন্য হবে এবং চিরকালের জন্য হবে। কেউ আর পিছিয়ে ফেরত আসতে পারবে না। যেমন আজ আমরা আসতে পেরেছি।
মহিমা ওকে লক্ষ করছিল। তীর্থঙ্কর এখনও চুপ করে আছে। পুলিশের দলটা অপেক্ষা করছে তাদের প্রশ্নের উত্তরের জন্যে। প্রতিবেশীরা অপেক্ষা করছে তীর্থঙ্কর কী বলে তার জন্যে। সবাই অপেক্ষা করছে তার ব্যাখ্যার জন্যে।
তীর্থঙ্কর চুপ করে আছে এখনও।
হাসিনা কাকী উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করেন, “এটা কি সত্যিই বয়লারটা ফেটে হল?” তারপর উত্তর না পেয়ে নিজেই বলেন, “হ্যাঁ। এমন তো হতেই পারে। হয়েছেও বলে যেন শুনেছিলাম কোথাও…”
একজন প্রতিবেশী বলে ওঠেন, “গ্যাস সিলিন্ডারগুলো দ্যাখো। ওগুলো ফেটেও তো হতে পারে, না কি?”
তীর্থঙ্কর উত্তর দেয় না। কি উত্তর দেবে ও? প্রকৃত সত্য বলা যাবে না। সাত বছর পরের এক যুদ্ধ ওদের টেনে নিয়ে গিয়ে সেদিনের বাস্তব অবস্থাটা দেখিয়ে আবার ফেরত দিয়ে গেছে, এই গল্প কেউ বিশ্বাস করবে না। কাজেই সত্যিটা ও এদেরকে বলতে পারবে না। কেননা এরা কেউ বুঝতে পারবে না। এরা কেউই সত্যিটা জানতেও চায় না। এদেরকে একমাত্র তাদের মনের মতো উত্তর দিলে তবেই বিশ্বাস করবে এরা। ওদের মনের মতো উত্তর!
তীর্থঙ্কর এবার ওদের চোখে সেটা দেখতে পায়। সেই সঙ্গে ওদের চোখে একটা ভয়ের আভাস-ও দেখতে পায় তীর্থঙ্কর। ওরা যেন আন্দাজ করতে পারছে যে তীর্থঙ্কর আসলেই এক ভয়াবহ সত্য তাদের সামনে উন্মোচিত করতে পারে। তাই ওরা ভয় পাচ্ছে। ওর দিকে তাকিয়ে ওরা যেন মিনতি করছে। প্রকৃত সত্য নয়। বরং তীর্থঙ্কর যেন তাদের দেওয়া প্রস্তাবগুলোর মধ্যেই কোনও একটা মেনে নেয়।
স্থিত হয় তীর্থঙ্কর। দেখতে পায় সবাই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তীর্থঙ্করের উত্তর যেন সহনশীল হয়। তীর্থঙ্করের উত্তর যেন ওদের ভয়ের কারণ না হয়ে ওঠে।
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তীর্থঙ্কর বলে ওঠে, “ও, হ্যাঁ। এটা ওই বয়লারটার জন্যেই হয়েছে।”
প্রাণকৃষ্ণদা যেন দম চেপে বসেছিলেন এতক্ষণ। তীর্থঙ্কর উত্তরটা দিয়ে দিতে যেন হাঁফ ছাড়লেন। “আমি ঠিক ধরেছিলাম।“ বাকিরাও যেন মুক্তি পায় এই উত্তরে। সবার মধ্যেই একটা আনন্দের চাপা হিল্লোল যেন বয়ে গেল।
“আমার উচিত ছিল অনেক আগেই ওই বয়লারটার ক্রুটি সারিয়ে নেওয়া।” তীর্থঙ্কর বলে। “আরও অনেক আগেই ওটা লক্ষ করা উচিত ছিল আমার। পুরোপুরি খারাপ হয়ে এমন ধ্বংসের কারণ হয়ে ওঠার অনেক আগেই।”
ওর চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা উৎসুক লোকগুলোর মূখের দিকে একবার তাকিয়ে নিলো তীর্থঙ্কর। তারপর আবার বলল, “আমার আরও আগেই এ ব্যাপারে নজর দেওয়া উচিত ছিল। খুব দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই।”

মূল গল্প: ফিলিপ কে. ডিক রচিত কল্পবিজ্ঞান “ব্রেকফাস্ট অ্যাট ট্যুইলাইট” (১৯৫৪) গল্পটির ছায়া অবলম্বনে লিখিত।
Tags: অনুবাদ উপন্যাস, পঞ্চম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, ফিলিপ কে. ডিক, রুদ্র দেব বর্মন, সৌরভ ঘোষ